অমিতাভ সরকার
নতুন সূর্য আলো দাও
অবিস্মরণীয় রবীন চট্টোপাধ্যায়
‘নুপুরের গুঞ্জনে বনবীথি উতলা’, ‘ননদিনী বলো নাগরে’, ‘এ শুধু গানের দিন’, ’তুমি না হয় রহিতে কাছে’,’ঘুম ঘুম চাঁদ ঝিকিমিকি তারা’, ‘পলাশ আর কৃষ্ণচূড়া’ কিংবা ‘আর ডেকো না সেই মধু নামে’, ‘ওগো মোর গীতিময়’, ‘মনময়ূরী আবেশে দোলে’, ‘আজ এই তো প্রথম এমন করে আমার কাছে এলে’, ‘আঁধার ভাঙা আলোর গানে’, ‘আনমনা এই মন’ -গীতশ্রী সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে গানগুলো চারপাশে আজও কান পাতলেই শোনা যায়। এমন মন জাগানিয়া সুর – যে আজও তার এক অমোঘ আকর্ষণে যে কোনো সংগীতপিপাসু মানুষ মোহিত না হয়ে পারে না। কিন্তু গানগুলোর সুরকার কে, জিজ্ঞেস করলে অনেকেই তা বলতে পারবেন না।
উত্তরটি হলো -রবীন চট্টোপাধ্যায়। আজ অনেকে তাঁর নামটুকু না জানলেও বাংলা গানে তাঁর অবদান অনস্বীকার্য। সুরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষায়, চলচ্চিত্রের অর্কেস্ট্রেশনে, নেপথ্য সংগীতের ব্যবহারে অসাধারণ পারদর্শিতা সমকালের অন্যান্য সুরকারদের থেকে ওঁকে অনেকাংশে এগিয়ে রেখেছিল। চার-চারটি দশক উনি সুরকার হিসাবে নিজের একটা জায়গা তৈরি করে ফেলেন।
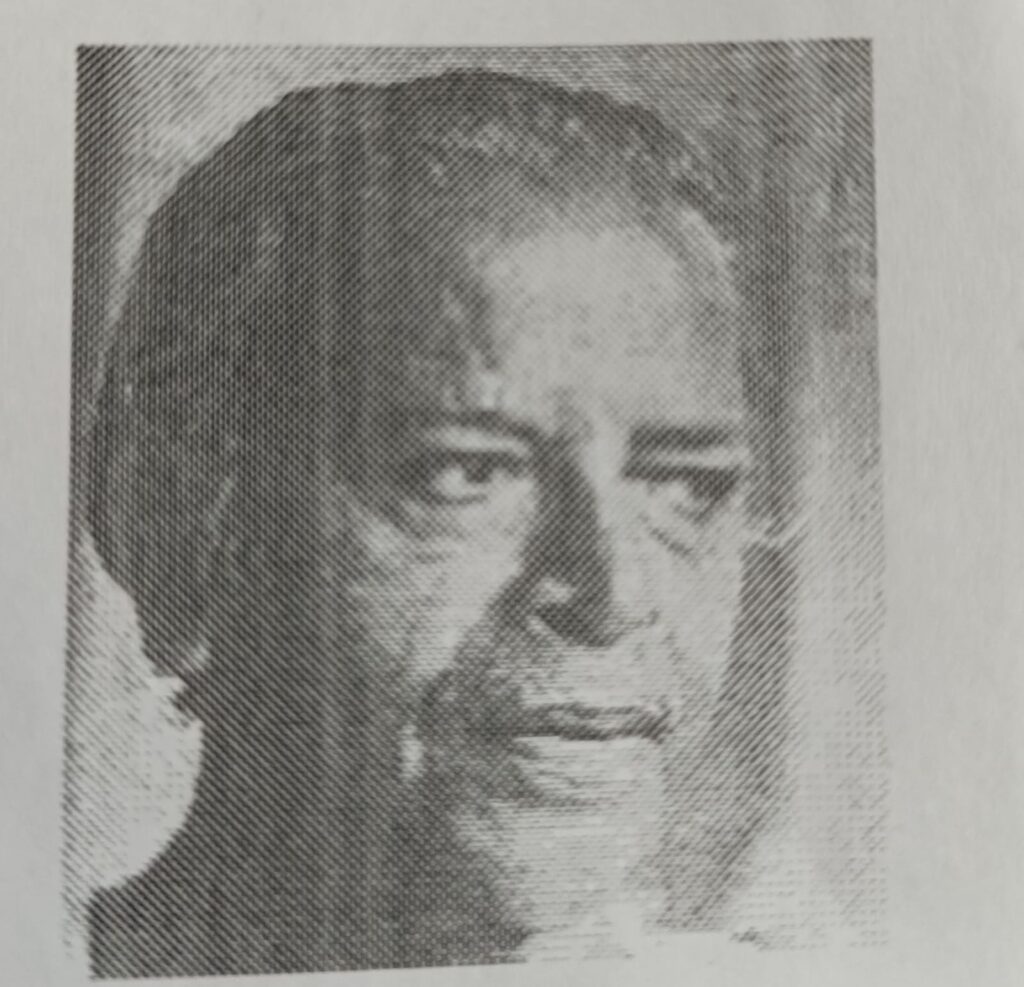
১৯৫০,১৯৬০-এর দশকে রবীন চট্টোপাধ্যায় সফলতম সংগীত পরিচালকদের মধ্যে একজন। প্রায় একশোর মতো চলচ্চিত্রে সঙ্গীত পরিচালক হিসাবে কাজ করেছেন, এক্ষেত্রে হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের পরেই ওঁর স্থান (হিন্দি-বাংলা মিলিয়ে হেমন্ত মুখোপাধ্যায় প্রায় ১৪২টি চলচ্চিত্রে সুরস্রষ্টা হিসেবে অসামান্য নজির রেখে গেছেন)। সেই সময় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের মতো এমন বহুমুখী প্রতিভার অধিকারী কেউ ছিলেন না। সুরকার হিসাবে হারমোনিয়াম, তবলা, স্যাক্সোফোন, ঢোল, কটেজ/গ্রান্ড পিয়ানো, ব্রাস ফ্রুট ইত্যাদি প্রায় সব রকম যন্ত্রবাদনে তিনি দক্ষ ছিলেন।
আড়বাঁশির জন্য পান্নালাল ঘোষ, সেতারে গোকুল নাগ, সরোদে তিমিরবরণ প্রভৃতি কিংবদন্তীরা ছিলেন তাঁর শিক্ষক। এছাড়াও বিভিন্ন মানুষের কাছে সংগীতের বিষয়ে খুঁটিনাটি অনেক কিছু শিখেছেন, এবং সেটা পুরোপুরি নিজেরই চেষ্টায়।
জন্ম ১৯১৮ সালের ৮ই জানুয়ারি। জন্মস্থান কালীঘাটের -২২/বি প্রতাপাদিত্য রোডের বাড়ি। বাবা নলিনীমোহন ছিলেন আইনজীবী, বংশপরিচয়ের দিক থেকে সরশুনার সম্ভ্রান্ত চট্টোপাধ্যায় পরিবারের একজন। মা চারুশীলা দেবী ভাগলপুরের জমিদারবংশের আইনজীবী গোপাল ব্যানার্জীর মেয়ে। রবীন্দ্রনাথ মা-বাবার তৃতীয় পুত্র, আর সন্তান হিসেবে ছিলেন পঞ্চম। মা-বাবার দেওয়া রবীন্দ্রনাথ নাম উনি নিজেই ছোট করে রবীন চট্টোপাধ্যায় লিখতেন(উল্লেখ্য একই ঘটনা সেই সময়ের বিখ্যাত নায়ক-গায়ক রবীন মজুমদারের ক্ষেত্রেও)। বড়দাদা অমরনাথ ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামী, অপর দাদা সত্যেন্দ্রনাথ অধ্যাপক, জ্যাঠতুতো দাদা বিখ্যাত পদার্থবিজ্ঞানী শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায় যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপনা করতেন।
বুঝতেই পারা যাচ্ছে, বাড়িতে গানবাজনার তেমন কোনো পরিবেশ ছিল না, বা সংগীত বিশারদও কেউ ছিল না। কিন্তু তা হলেও ছোটবেলা থেকেই গানের নেশা ওঁকে পেয়ে বসেছিল। নিজে ভালো গাইতেনও। অনেকের কাছে গান শিখেছেন। মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের কাকা সিদ্ধেশ্বর মত রত্নেশ্বর মুখোপাধ্যায় ছিলেন ওঁর প্রধান গুরু। এছাড়া রবীন্দ্রসংগীতে অনাদি ঘোষ দস্তিদার, ঠুমরীতে শ্রীমতী সিদ্ধেশ্বরী দেবী, পুরাতনী গানে তুলসী চক্রবর্তী -এঁরা তো ছিলেনই, এছাড়া বিদ্রোহী কবি কাজী নজরুল, রাধারানী দেবী, আঙুরবালা প্রভৃতিদের কাছেও অল্প সময়ের জন্য হলেও তালিম নিয়েছিলেন।
নিজের ব্যক্তিগত পছন্দের শিল্পী ছিলেন শচীনদেব বর্মন। ওঁর গান খুবই গাইতেন। ১৯৪০-৪৫ সালের সময়টাতে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের স্বকণ্ঠে গাওয়া বেশ কিছু গানের রেকর্ড বেরিয়েছিল বলে জানা যায়। বেসিক রেকর্ডের সেইসব গানগুলিতে সুরকার হিসাবে সুবোধ দত্তগুপ্ত, সুরসাগর হিমাংশু দত্ত, দুর্গা সেন -এঁদের নাম পাওয়া গেছে। এছাড়া বন্ধুবান্ধবের মধ্যে, ক্লাবের অনুষ্ঠানে গানও গেয়েছেন।
খেলাধুলাও খুব পছন্দ করতেন। নিজে ভালো ফুটবল খেলতেন। একসময় মোহনবাগানের জুনিয়র দলেও খেলেছেন। সে যুগে মোহনবাগান ক্লাব ছিল স্বদেশী আন্দোলনের আখড়া। ওঁর দেশপ্রেমের চেতনা, বিভিন্ন বিদগ্ধ মানুষের সঙ্গে পরিচিতি -সবকিছুই এখান থেকেই তৈরি হয়। খেলায় নাম করতে না পারলেও বন্ধুবান্ধব ছিল অনেক।
গান, খেলাধূলা করলেও উনি লেখাপড়াতে কিন্তু বেশ মনোযোগী ছিলেন। বাড়িতে লেখাপড়ার পরিবেশও ছিল। সাউথ সুবার্বন স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পাশ করে আশুতোষ কলেজে ভর্তি হন। সেখান থেকে ইন্টারমিডিয়েট পাশ করে ইংরেজিতে সাম্মানিক ডিগ্রিসহ বিএ উত্তীর্ণ হন।
ছাত্রজীবনেই গানের লাইনে প্রতিষ্ঠা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করতে করতে একদিন নীরেন লাহিড়ীর সঙ্গে ওঁর আলাপ হয়। তাঁরই অনুগ্রহে সুরকার অনুপম ঘটকের বাদ্যযন্ত্রী হিসাবে প্রথম কাজের সুযোগ পান। অর্কেস্ট্রার দলে, মধু বসু,সাধনা বসুর নাচের অনুষ্ঠানে এ ধরনের কাজের অভিজ্ঞতা আগে থেকেই ওঁর কিছুটা ছিল। অনুপম ঘটকের কাছ থেকে আরো কিছু সুযোগ নেই আরো কিছু শিখে নেওয়ার সুযোগ হয়ে গেল। অনুপম ঘটকও মনপ্রাণ ঢেলে দিলেন তাঁর এই আগ্রহী সহকারীটির জন্য। লেগে থাকতে থাকতে হঠাৎ করে প্রথম বছরেই প্রমথেশ বড়ুয়ার ‘শাপমুক্তি’ সিনেমায় সুযোগ এসে গেল সংগীত পরিচালনার। সুরকার অনুপম ঘটক অসুস্থ হয়ে পড়ায় ওই সিনেমার ‘একটা পয়সা দাও গো বাবু’ গানটি রবীন চট্টোপাধ্যায় নিজের সুরে শুক্রবার সরকারকে দিয়ে রেকর্ড করালেন। তবে সিনেমার টাইটেল কার্ডে সুরকার হিসাবে অনুপম ঘটকের নামটাই ছিল (তখন রবীন চট্টোপাধ্যায় সবে আনকোরা নতুন লে অনুপম ঘটক তাঁর নাম ব্যবহার করার অনুমতি দেননি)। কিন্তু এতে ধৈর্যশীল, মেধাবী গুণের অধিকারী তরুণ রবীন চট্টোপাধ্যায়ের খুব একটা অসুবিধা হয়নি। সুরসংযোজনা, আবহ সংগীতের ব্যবহার, বাদ্যযন্ত্রীদের সঠিক ভাবে ব্যবহার ও ম্যানেজ করা- এসবকিছুই উনি এত ভালোভাবে করতেন, যে সবাই রবীন চট্টোপাধ্যায়কে তখন থেকেই সমীহ করতো। তিমিরবরণের সঙ্গে কাজ করতে তিনি খুব ভালবাসতেন। তখন কলকাতায় প্রথম তিমিরবরণই অর্কেস্ট্রেশন পরিচালনা করতেন। রবীন চট্টোপাধ্যায় মিউজিক অ্যারেঞ্জ, মিউজিক ডাইরেকশন ইত্যাদির সামগ্রিক কাজে দক্ষ ছিলেন বলে তিমিরবরণও ওঁকে কাজে নিতে চাইতেন। তাছাড়া পরিশ্রমী, নিষ্ঠাবান, শৃঙ্খলাপরায়ণ দায়িত্বশীল একজন কর্মী হিসেবে সবাই ওঁর প্রশংসাও করতো। চেহারাও ছিল দারুণ। ছয় ফুট এক ইঞ্চি লম্বা, চুয়াল্লিশ ইঞ্চি ছাতির সুদেহী রবীন চট্টোপাধ্যায়কে সরু পাড়ের ধুতি, আর সাদা আরদির গিলে করা পাঞ্জাবিতে বেশ বড়োলোক দেখাতো। ওঁর ব্যক্তিত্ব ছিল চোখে পড়ার মতো। একদিন চিত্রপরিচালক পশুপতি চট্টোপাধ্যায় মোহনবাগান ক্লাবে তাঁর পরিচিত বিখ্যাত খেলোয়াড় অনিল দের সূত্রে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে পরিচিত হন এবং তাঁর ‘পরিণীতা’ ছবিতে ওঁকে সংগীত পরিচালক হিসেবে কাজ করার প্রস্তাব দেন। ওই বছরই অর্থাৎ ১৯৪২ সালে অভয়ের বিয়ে সিনেমায় সুরকার শচীন দেববর্মনের সহকারী হিসাবে রবীন চট্টোপাধ্যায় কাজ করে ফেলেছেন। কিন্তু স্বাধীন ভাবে সংগীত পরিচালকের দায়িত্ব পাওয়া গেল এই এমপি প্রোডাকশনের ‘পরিণীতা’ সিনেমাতেই। একে একে ‘সমাধান’ ‘কত দূর’, ‘পথ বেঁধে দিল’, ১৯৪৬-১৯৪৭ সালে ‘সাত নম্বর বাড়ি’(এই সিনেমাতেই বয়োকনিষ্ঠ হেমন্ত মুখোপাধ্যায় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে প্রথম কণ্ঠদান করেন। এছাড়া এই সিনেমায় রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরে তালাত মাহমুদের কণ্ঠে ‘কথা নয় আজি রাতে’ গানটি চিরস্মরণীয় হয়ে আছে।),’তুমি আর আমি’,’স্বপ্ন ও সাধনা’ ইত্যাদি চলচ্চিত্রে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুর ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় হয়। ১৯৪৮ সালে মুক্তি পেল ‘অনির্বাণ’,’বাঁকা লেখা’,’সাধারণ মেয়ে’ এবং ‘সমাপিকা’। ‘সমাপিকা’ চলচ্চিত্রের মাধ্যমে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের হাত ধরে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের আত্মপ্রকাশ ঘটলো। ওঁর সুরে চলচ্চিত্র ও রেকর্ডের বেসিক গান মিলিয়ে সব চেয়ে বেশি গান কিন্তু সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়েরই গাওয়া। এই ষাটখানা গানের সবই বহুল প্রচারিত ও আজও জনপ্রিয়। ‘সমাপিকা’ থেকেই অগ্রদূত পরিচালকগোষ্ঠীর সঙ্গে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগ। উক্ত সুরকার-পরিচালক জুটি পরবর্তীকালে বহু চলচ্চিত্র উপহার দিয়েছে। ১৯৪৯ সালে আভিজাত্য, নিরুদ্দেশ, সিংহদ্বার, সঙ্কল্প, বিদুষী ভার্যা- এই ছয়টি ছবি মুক্তি পায়, সবগুলোতেই সংগীত পরিচালনা রবীন চট্টোপাধ্যায়ের। মাত্র ত্রিশ বছর বয়সেই অপ্রতিরোধ্য সংগীত পরিচালক হিসেবে অসম্ভব বিখ্যাত হয়ে গেলেন। ১৯৫০ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘বিদ্যাসাগর’ খুব প্রশংসিত হলো। প্রথম পাঁচ বছরে পনেরোটি হিট ছবি দেওয়া কথার কথা নয়। ১৯৫০ সালে মায়ের পছন্দ করা পাত্রী অঞ্জলি দেবীকে বিবাহ করেন। অলকধন গঙ্গোপাধ্যায়ের কন্যা অঞ্জলি দেবী সাতক্ষীরার খুলনার সম্ভ্রান্ত আইনজীবী গঙ্গোপাধ্যায়ের পরিবারের কন্যা। এই দম্পতির দুই কন্যা শুক্লা, কৃষ্ণা এবং পুত্র সোমনাথকে নিয়ে ছিল সুখের সংসার। সুবিপুল কর্মজীবনের সঙ্গে পারিবারিক দায়িত্ব পালনেও কোনো খামতি থাকতো না। ওই সময় এক এক বছরে সাতটা থেকে পাঁচটা চলচ্চিত্রের সংগীত পরিচালকেরও কাজ করেছেন। ‘বাবলা’, ‘সহযাত্রী’ ইত্যাদি ছবি দর্শকদের মনে খুব দাগ কেটেছিল। প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়ের লেখা অবলম্বনে দেবকীকুমার বসুর ‘রত্নদীপ’ ছবিটি বাংলা তামিল হিন্দি তিন ভাষাতেই মুক্তি পায়।
এই সময় তিনি বোম্বে চলচ্চিত্রে সংগীত পরিচালনার জন্য প্রস্তাব পান। ‘মজবুরি’, ‘আফ্রিকা’, ’ফিরদৌস’, ‘পেহলি সাদি’,’চিমনি কা ধুঁয়া -হিন্দি চলচ্চিত্রে সুরকার হিসাবে রবীন চট্টোপাধ্যায় মীনা কাপুর, মনোরমা, তালাত মাহমুদ, এমনকি আশা ভোঁসলেকে দিয়েও গান গাইয়েছিলেন। তবে বোম্বেতে নাম করতে পারেননি। ফলে কলকাতা চলে আসতে হয়। বাংলা চলচ্চিত্রে তাঁর কাজ পাওয়া কিছুটা কম হয়ে গেছিল। মাঝের এই সময়টুকু বাদ দিয়ে ১৯৫৫ সালে ‘ভগবান শ্রী শ্রী রামকৃষ্ণ’ চলচ্চিত্রে জপমালা ঘোষ, শাস্ত্রীয় সংগীতশিল্পী প্রসূন ভট্টাচার্য, শ্যামল মিত্র প্রভৃতিদের দিয়ে গান গাওয়ালেন রবীন চট্টোপাধ্যায়। ‘দেবী মালিনী’ সিনেমায় আবারও অনুপম ঘটকের সঙ্গে যৌথভাবে সংগীত পরিচালনা করলেন। ‘শ্রীবৎস চিন্তা’ চলচ্চিত্রে ধনঞ্জয় ভট্টাচার্য, সুপ্রীতি ঘোষ, উৎপলা সেন প্রভৃতিদের সঙ্গে গান গাওয়ালেন নবাগতা আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়কে। ১৯৫৫ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ‘সবার উপরে’ আবারও হিট। উত্তম-সুচিত্রা জুটির এই সিনেমার গানে সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে এবারও অসাধারণ গান উপহার দিলেন সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়। তবে ১৯৬০ সালের পর থেকে তুলনামূলকভাবে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরকৃত চলচ্চিত্রের সংখ্যা কখনো কখনো একটু কমে গিয়েছে। এর কারণ, সুধীন দাশগুপ্ত, সলিল চৌধুরী, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, ভি বালসারার প্রভৃতিদের বিভিন্ন বাদ্যযন্ত্রের ব্যবহার, সময়ের আধুনিকতার সঙ্গে মানানসই সুরের প্রয়োগ ইত্যাদি নানান কারণ উল্লেখ করা যায়। তবে গায়ক-গায়িকাদের ব্যাপ্তিটাও বুঝতেন। সুরও করতেন সেভাবেই। ফলে সিনেমাগুলো বিশাল হিট না হলেও একেবারে ফ্লপ হতো না। রবীন চট্টোপাধ্যায়ও বিভিন্ন বিদেশি যন্ত্র ব্যবহার করতেন। তবে আড়ম্বরপূর্ণ সুররচনা বর্জন করে মূলত মেলোডিযুক্ত পরিশীলিত সুরের ব্যবহারই ওঁর পছন্দ ছিল। তবে সেটা অবশ্যই সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে। নিজেও মেজাজী মানুষ ছিলেন। কোনোরকম অন্যায়ের সঙ্গে, কিংবা যেটা মন থেকে ঠিক বলে মনে হতো না, সেসবের সঙ্গে আপোষ করাটা তাঁর একদমই স্বভাবে ছিল না। ফলে বাবার মৃত্যুর পর পৈত্রিক বাড়ি ছাড়তে হয়েছে- মুর এভিনিউ, রিজেন্ট পার্ক, লেক গার্ডেনস, যোধপুর পার্ক ইত্যাদি জায়গায় বারবার বাসা পরিবর্তন করতে হয়েছে, ভালো রোজগার করলেও ভাড়া বাড়িতেই থাকতে হয়েছে, নিজের বাড়ি করা আর হয়ে ওঠেনি। শেষের দিকে যাদবপুরের রাইপুর রোডে সপরিবারে থাকতেন। বড়ো মনের মানুষ ছিলেন। দানধ্যানও করেছেন। সৌখিনতাও ছিল প্রচুর। অনেক নতুন শিল্পীকে সুযোগ করে দিয়েছেন। তবে সংসারে বেশি সময় দিতে পারতেন না। স্ত্রী অঞ্জলি দেবীকেই সব সামলাতে হয়েছে। ১৯৫৫ সালে আবার ছয়টি, ১৯৫৬ সালে সাতটি ছবি উপহার দিলেন। এরমধ্যে ‘সাগরিকা’ সিনেমার সব গানগুলোই জনপ্রিয় হয়। শ্যামল মিত্রের গাওয়া ‘আমার স্বপ্নে দেখা রাজকন্যা’, সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের কণ্ঠে ‘এই মধু রাত শুধু’,’এই তো আমার প্রথম ফাগুনবেলা’, কিংবা সমবেত কণ্ঠে ‘আমরা মেডিকেল কলেজে পড়ি’ গানগুলো কালজয়ী হয়ে গেছে। ‘সাহেব বিবি গোলাম’ সিনেমার রাগাশ্রয়ী গানগুলো অনবদ্য। ‘গোধূলি’,‘পথে হলো দেরি’,’লালু ভুলু’,’শুনো বরনারী’,’ইন্দ্রধনু’,’শহরের ইতিকথা’,’বিপাশা’,’অগ্নিশিখা’, ‘অভিসারিকা’, ’আকাশ প্রদীপ’,’দ্বীপের নাম টিয়ারঙ’,’সূর্যশিখা’, ‘উত্তর ফাল্গুনী’, ’মোমের আলো’,’রাজা রামমোহন’,’জয়া’,’শুধু একটি বছর’,’দত্তা’ ইত্যাদি চলচ্চিত্রে রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুমধুর সঙ্গীত উপহারের অনিবার্য ধারা অব্যাহত ছিল। ১৮৬৪ সালে ‘সঁইয়া সে ভইলে মিলনবা’ নামের একটি ভোজপুরি চলচ্চিত্রে সুরকারী হিসেবে সুমন কল্যাণপুর এবং মোহাম্মদ রফিকে প্লে ব্যাক করিয়েছিলেন। ১৯৫৬ থেকে ১৯৬৪ সাল পর্যন্ত এই সময়কালটি সুরকার রবীন চট্টোপাধ্যায়ের স্বর্ণযুগ। এই সময়টায় উনি চল্লিশটি ছবিতে সুরসৃষ্টি করেছিলেন। ১৯৬৯ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত চারটি ছবি ‘আধার সূর্য’,’আরোগ্য নিকেতন’,’অপরিচিত’ এবং ‘কমললতা’। ‘কমললতা’ সিনেমার গানগুলো সঙ্গীতপ্রেমী মানুষেরা আজও মনে রেখেছেন। হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের কন্ঠে সাতটি কীর্তনাঙ্গের গান, শ্যামল মিত্র-সন্ধ্যা মুখার্জী দ্বৈতকণ্ঠে ‘সে বিনে আর জানে না’,’ও মন কখন শুরু কখন যে শেষ’-আজও মনকে আলোড়িত করে। ১৯৭২ সালে ‘নায়িকার ভূমিকায়’ সিনেমায় অনুপ ঘোষালের কণ্ঠে ‘এক যে আছে কন্যা’ খুব জনপ্রিয়। এছাড়া শেষদিকের সুর করা ছবিগুলির মধ্যে ‘অপর্ণা’,’দুরন্ত জয়’ এবং ‘চাঁদের কাছাকাছি’-র নাম উল্লেখ করা যায়। সর্বশেষ ছবি ‘চাঁদের কাছাকাছি’ চলচ্চিত্রের সাফল্য দেখে যাওয়া ওঁর পক্ষে আর সম্ভব হয়নি, কারণ তার আগেই উনি ইহলোক ছেড়ে ‘চাঁদের কাছাকাছি’ পাড়ি দেন। মৃত্যুর তিন দিন আগে সকালে হঠাৎ পুজো করতে গিয়ে পড়ে গেলে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় রবীন চট্টোপাধ্যায়কে পিজি হাসপাতালে ভর্তি করলে ডাক্তাররাও অনেক চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু উনি আর ফিরে আসেননি। দিনটা ছিল ১৯৭৬ সালের ২রা এপ্রিল। তিন সন্তান, স্ত্রীকে রেখে যাওয়া এই সঙ্গীতকারের মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল মাত্র আটান্ন।
রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সুরের মূল্যায়ন করা সহজ নয়। একজন শিল্পীর শিল্পভাবনার বিচার সমকাল তো বটেই, উত্তর কালেও বেশ কঠিন। গৌরীপ্রসন্ন, শৈলেন রায়, শ্যামল গুপ্ত, পুলক বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রণব রায়, পবিত্র মিত্র, হীরেন রায়, বিমল ঘোষ, শিবদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি গীতিকারদের গানে যেমন সুর বসিয়েছেন, তেমনি সন্ধ্যা হেমন্তকে বাদ দিয়ে শ্যামল মিত্র, প্রতিমা বন্দ্যোপাধ্যায়, তরুণ বন্দোপাধ্যায়, কানন দেবী, যূথিকা রায়, গায়ত্রী বসু, রবীন মজুমদার, সতীনাথ মুখোপাধ্যায়, বনশ্রী সেনগুপ্ত, ইলা বসু, মানবেন্দ্র মুখোপাধ্যায়, আলপনা বন্দ্যোপাধ্যায়, মিন্টু দাশগুপ্ত, নির্মলা মিশ্র, অনুপ ঘোষাল, শিপ্রা বসু ইত্যাদি প্রচুর শিল্পী ওঁর সুরে গেয়েছেন। আরতি মুখোপাধ্যায়ও রবীন চট্টোপাধ্যায়েরই আবিষ্কার। রবীন চট্টোপাধ্যায় একটি সঙ্গীতানুষ্ঠানে বিচারক হয়ে উপস্থিত ছিলেন, সেই প্রতিযোগীতার শিল্পী হিসাবে আরতি মুখোপাধ্যায়ের গান শুনে তাঁকে বাংলা সিনেমা গাওয়ার সুযোগ করে দেন। এছাড়া মনোহারী সিং, বাসু চক্রবর্তীকে বোম্বে পাঠালে ওঁরা বোম্বেতে প্রতিষ্ঠা পান। ‘কমললতা’ চলচ্চিত্রে সাফল্যের পর বলিউডের ডাক পাওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছিল। তবে শেষের দিকে ওঁর শরীর স্বাস্থ্য, বা মানসিক চিন্তাভাবনা ঠিক কী অবস্থায় ছিল সেটা বলা মুশকিল। ওঁর স্ত্রী অঞ্জলি দেবীও ২০১৫ সালে গত হয়েছেন। সেদিক থেকেও তথ্য পাওয়াটা খুব মুশকিল। তবে শেষদিকে উনি কথাবার্তা বলা কমিয়ে দিয়েছিলেন। যাদবপুরের ওখানে বাড়ি করার চিন্তাভাবনাও করছিলেন। কিন্তু সব আশায় জলাঞ্জলি হয়ে যায় ওঁর ওই অকস্মাৎ চলে যাওয়ায়।
রবীন চট্টোপাধ্যায়ের সম্বন্ধে অনেককিছুই জানা যায় না। সমকালের শিল্পীরাও কেউ ওঁর সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখে যাননি।
কিছুটা রাশভারী মানুষও ছিলেন, আশেপাশের মানুষজনকে বেশি কাছে ঘেঁসতে চাইতেন না। তাছাড়া উনি কাজ ছাড়া কিছু ভাবেননি। সুর তৈরিই ছিল ওঁর একমাত্র ধ্যানজ্ঞান। কাজের মধ্যে থাকতে থাকতেই চলে গেছেন। অন্য কোনোকিছুর সুযোগ দেননি।
বঙ্গদর্শন ব্লগের ওয়েবপেজ থেকে প্রাপ্ত তথ্য, এবং বিভিন্ন অন্যান্য লেখা, গুগল প্রভৃতির ভিত্তিতে এই নিবন্ধ রচনা সম্ভব হলো। বঙ্গদর্শন থেকে শিল্পীর পুত্র সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়ের যোগাযোগের সূত্র ধরে এবং সুশান্ত চট্টোপাধ্যায়ের গ্রন্থন সহায়তায় যতটুকু জানা, এতেই খুশী থাকতে হলো। আগ্রহী গবেষকদের কাছে অনুরোধ রইলো বাকিটা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার। বরেণ্য এই সুরস্রষ্টাকে নিয়ে সঙ্গীতানুরাগী মানুষের আগ্রহ বাড়ানোই এই রচনার উদ্দেশ্য।
এই ক্ষণজন্মা সুরকারের মৃত্যুর এত বছর পরেও তাঁকে নিয়ে কিছু জানার, বা শ্রদ্ধাপ্রকাশের কোনো আগ্রহ আমাদের আত্মবিস্মৃত বাঙালি জাতির মধ্যে দেখা যায়নি, তা সে নিজেদের যতই সংগীতপ্রেমী বলে আখ্যায়িত করি না কেন। রবীন চট্টোপাধ্যায় জীবদ্দশায় মাত্র দুটো পুরস্কার পেয়েছিলেন- ১৯৫৬ সালে ‘সাহেব বিবি গোলাম’ ছবির জন্য সংগীত নাটক একাডেমী পুরস্কার, আর ১৯৬২ সালে বিএফজেএ থেকে শ্রেষ্ঠ সংগীত পরিচালকের পুরস্কার। ব্যস, এর বেশি কিছু নয়।
‘আশা নদীর দুই ধারে শুধু ভাঙা গড়া শুধু সার’, ‘আলোকে ছায়াতে দিনগুলি ভরে রয়’,’আমার চেতনা চৈতন্য করে'(শ্যামাসংগীত),’কেন বন কোয়েলা ডাকে’,’কাঁটার আঘাতে ছিন্ন চরণে রক্ত ঝরে’,’কাকলি কূজন আর ভ্রমরে মধু গুঞ্জনে’, ‘রিমিঝিমি রিমিঝিমি শ্রাবণে কি সুর’, ‘গান ফুরানো জলসাঘরে’, ‘স্বপ্ন জাগানো রাত’, ‘নবমী নিশি রে’,’নিখিল নিরঞ্জন নিখিল কারণ’, ‘আমি প্রিয়া হব ছিল সাধ’,’যদি কোনোদিন ঝরা বকুলের’, ’আমি যারে স্বপন দেখি’,’মাগো তুমি অমন করে ডেকো না’, ’আমি চান্দের সাম্পান যদি পাই’,’প্রাণ ঝরনা জাগলো’, ’মাটির ঘরে আজ নেমেছে চাঁদ রে’,’মধু মালতী ডাকে আয়’, ‘এ শুধু গানের দিন’(উল্লেখ্য, যে এই গানে পিয়ানো অ্যাকোর্ডিয়ান যন্ত্রের এফেক্ট সুন্দরভাবে এনেছিলেন। যা সেইসময়ের একটা আলাদা দৃষ্টান্ত।), কিংবা ‘শ্রীরাধার মানভঞ্জন’(১৯৬৯), রামকৃষ্ণের জীবনবৃত্তান্তের অ্যালবাম(১৯৭৪)-এর মতো অসাধারণ সব কাজ করে গেছেন, সেই মানুষটির কী আমাদের কাছে আরও অনেকখানি সম্মান পাওয়া উচিত ছিল না! এটা আমাদের বিবেকের কাছে একটুও কী ভেবে দেখার নয়!
সম্ভাবনা কম। বিজ্ঞান, প্রযুক্তির যুগে এসেও এ ব্যাপারে ইচ্ছেটাই যে কম। তবু আশা হারালে যে চলবে না।
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়ের গানের লাইন দিয়ে এই নিবন্ধ শুরু করেছিলাম, তাঁরই গানের কথা দিয়ে এই রচনার ইতি টানলাম- ’জানি না ফুরাবে কবে এই পথ চাওয়া’…।
প্রতিভাস ম্যাগাজিন | Prativas Magazine
