অরিত্রী দে
পর্ব – ১
মাটির স্বাস্থ্যরক্ষা ও কৃষি-সংস্কৃতি: মিথোজীবীতার আখ্যান
‘পরিবেশ’ (Environment) শব্দটার তুলনায় ‘প্রকৃতি’ (Nature) শব্দ ও অনুষঙ্গের সঙ্গে আমরা বেশি পরিচিত। প্রকৃতি সেই সমগ্র তথা অখন্ড’র ধারণাকে বহন করে যেখানে তার অন্তর্গত সমস্ত জৈব ও অজৈব উপাদানগুলি অত্যাধুনিক মানব সভ্যতার রাক্ষুসে প্রযুক্তির ক্ষতিকর প্রভাব মুক্ত। আর পরিবেশ বলতে বাহ্য উপাদানগুলির সমন্বয়গত সেই পরিস্থিতিকে বোঝায় যা কোনো জীব বা প্রজাতির প্রাণ ধারণ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। আমাদের সংস্কৃতি মূলত: প্রকৃতি লগ্নতার সংস্কৃতি ছিল। সে কারণে আমাদের উৎপাদনও জলবায়ু, মৃত্তিকা, জল, উদ্ভিদ, গবাদি পশু নিয়ে একটা গোটা (Whole) সংস্কৃতি হিসেবে পরিচিত ছিল। আমরা কৃষি উৎপাদন বলতাম না, বলতাম ‘কৃষি সংস্কৃতি’। প্রতিটি ঋতুর বিভিন্ন উৎসব, খাদ্য-অখাদ্যের সময় মানার নিয়ম, নদী বা জল নিয়ে নিয়ম-সংস্কার, বিশেষ গাছের বা তিথির পবিত্রতা, উৎসব কিংবা শোকের মন্ডনসজ্জা ইত্যাদি সব কিছুতেই প্রকৃতিমুখীনতা ও প্রকৃতির নিয়মানুবর্তিতা ছিল৷ তখন উৎপাদনেও বৈচিত্র্য ছিল। তাই আষাঢ়, পৌষ মাসে সারাদেশে ফসল বোনা আর তোলার উৎসব পালিত হতো বিভিন্ন নামে। মাঠে যে ফসল ফলত, মানুষ ছাড়াও গবাদি পশুরা, এমনকি মেঠো ইঁদুর, কেঁচো প্রভৃতি প্রাণীরা বাঁচত। হাঁস-মুরগি প্রতিপালনের জন্য তখন বাজার থেকে আলাদা করে খাবার কিনতে হত না। খুদ, ভুট্টার দানা, ফসলের খোসা খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হত। ধানক্ষেত ও তার নিকটস্থ অগভীর জলে জন্মানো অ্যাজোলা (জলজ ফার্ন) জমির উর্বরতা বৃদ্ধিতে ও একইসঙ্গে পশুখাদ্য হিসেবে এখনও ব্যবহৃত হয়। ক্ষেতে কৃষিজাত বড় গাছের নিচে ব্রাহ্মী, থানকুনি, ভৃঙ্গরাজ, কেশুত, শুশনি আমরুলের মত অকৃষিজাত বেশ কিছু ভেষজ উদ্ভিদ প্রকৃতির নিয়মেই ভালো হয়। আমরা সকলেই জানি যে ধানজমির নিজস্ব প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্র আছে। জৈব সার প্রয়োগ, প্ল্যাঙ্কটন উৎপাদন, অবশ্যম্ভাবী রূপে প্ল্যাঙ্কটন খাদক পোকার আগমন ও মাংশাসী পোকার আনাগোনা (পূর্বোক্ত ছোট পোকা ভক্ষণ করে) – সব মিলিয়ে এক স্বাস্থ্যসম্মত কৃষি বাস্তুতন্ত্র গড়ে ওঠে। এই ধান বোনার জমিতে আলের জলে মাছও চাষ হত। সেই মাছ যেমন প্রোটিন আহার জোগায় তেমনি মৃত মাছের দেহাবশেষ মাটিতে মিশে উর্বরতাও বাড়ায়। কোনো সপ্তাহে বাজার না হলেও দিদা, ঠাম্মা, মায়েরা শাক পাতা তুলে এনে ঠিক খিদে মেটাতেন। তাঁরা জানতেন কোথায় খাদ্যযোগ্য উদ্ভিজ্জ মিলবে। ছোট রকমের রোগপাতিও সারিয়ে দিতে পারতেন প্রকৃতি সংলগ্নতার জ্ঞান থেকেই। এই প্রকৃতিমুখীনতা, প্রাকৃতিক নিয়মানুবর্তিতা, উৎপাদন বৈচিত্র্য গ্রামীণ মানুষ সহ বাস্তুতন্ত্রের অন্তর্গত অন্যান্য প্রাণীদের খিদে তখনও মিটিয়েছে যখন ধান-গমের অভাব দেখা দিত। বিংশ শতকের গোড়া থেকেই প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্ক হোঁচট খেতে শুরু করে। ঔপনিবেশিক শাসন ও দুই বিশ্বযুদ্ধ ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের প্রাকৃতিক ধনসম্বলকে (এমন কিছু, যা কিছুতেই খরচ করতে চাওয়া হয়না) শেষ করে। বিশ্বযুদ্ধ পরবর্তীতে আমাদের প্রকৃতিলগ্ন উৎপাদন নীতি প্রতিস্থাপিত হয় উন্নয়ন ভাবনা প্রভাবিত নতুন উৎপাদন নীতির দ্বারা। উৎপাদন ক্রমে আগ্রাসন ও লোভজড়িত উন্নতির অন্তর্ভুক্ত হল। এই যুগকে আমরা পরিবেশ বিপন্নতার যুগ বলতে চাইব। প্রকৃতির প্রক্রিয়াকরণ (Processing) শুরু হয় এই পর্ব থেকেই, জন্ম নেয় প্রাকৃতিক উপাদানের (উপাদান মানেই খন্ডিত) ধারণা।
আধুনিক জেনেটিক মডিফায়েড বীজ, কৃষক ও কর্পোরেট সম্পর্ক (যেমন- আদানি গ্রুপ) প্রভৃতি এই লোভ আর মুনাফা প্রশ্নেরই অন্তর্গত। ফলে আধুনিক কৃষি যত ফলন বাড়িয়েছে, তার চেয়ে অনেক বেশি চাতুর্যে গরিব করেছে গ্রামকে। কীভাবে, তার অবতারণা করার আগে একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক নিয়ে আলোচনার প্রয়োজন আছে। বিশ্ব উষ্ণায়ন, অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে ওজোন স্তরের বে-আব্রু হয়ে পড়া ইত্যাদির কালে ‘ক্লাইমেট সলিউশন’ হিসেবে আজকাল ‘সয়েল কার্বন ফার্মিং’ প্রায় দেবদূতের মতো উপস্থিত হয়েছে। এর তত্ত্ব বুঝতে গেলে প্রকৃতির নিজস্ব নিয়মে মনোনিবেশ করতে হবে। সালোকসংশ্লেষ বা ‘ফটোসিন্থেসিস’ এর মাধ্যমে প্রকৃতি থেকে উদ্ভিদ নিজের মধ্যে কার্বন-ডাই-অক্সাইড শোষণ করে। এর ফলে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় কার্বন ( C) ও অক্সিজেনে (O2) ভেঙে পাতার মধ্যে দিয়ে কার্বন অণু পরিবাহিত হয় আর অক্সিজেন পরিবেশে গিয়ে মেশে। কার্বন উদ্ভিদের মূলে চলে যায় ও জারিত হয়ে চিনি এবং অন্যান্য কার্বন যৌগে পরিণত হয়৷ মূলের মধ্যে দিয়েই সেগুলি মাটিতে ছড়িয়ে পড়ে, যা মাইক্রোঅর্গানিজমের খাদ্যে পরিণত হয়। এরপর জৈব পদার্থে ভেঙে গিয়ে (Organic substance) তা যথেষ্ট পরিমাণে পরিপোষক পদার্থের (Nutrients) যোগান দেয়। এগুলি উদ্ভিদ শোষণ করে নেয়। আবার পোকামাকড়ের দেহাবশেষ, জীবাণু মাটির সমস্ত অণু শক্ত করে ধরে রাখতে সাহায্য করে। এর ফলে মাটিতে জল, বায়ু পর্যাপ্ত পরিমাণে চলাচল করতে পারে এবং মূলের বৃদ্ধি ঘটে। এভাবে ‘ইকো সিস্টেমে’র সঙ্গে মাটির সম্পর্ক যত দৃঢ় হয়, মাটি তত স্বাস্থ্যবান হয়। ২০১৯ সালের র্যাচেল কার্সন পুরস্কার প্রাপ্ত বেথ ব্রেকেট (Beth Brockett) তাঁর গবেষণায় দেখিয়েছেন- মাটিতে কার্বনের পরিমাণ বাড়িয়ে আমরা বায়ুমণ্ডলে কার্বনের পরিমাণ হ্রাস করার সঙ্গে সঙ্গে উষ্ণায়নও হ্রাস করতে পারি, এমনকি তাতে মাটির স্বাস্থ্যেরও উন্নতি হবে। তিনিই মূলতঃ কার্বন ফার্মিংয়ের (Soil Carbon farming) উদ্যোক্তা।
চিত্র-১ চিত্র-২
এটি আসলে চাষবাসের এক প্রকার পদ্ধতি যা পরিবেশে উপস্থিত কার্বনকে মাটিতে, ফসলে, গাছের পাতা ও কাঠে আবদ্ধ করে। ‘নেচার ইংল্যান্ডে’ (Nature England) কাজ করতে করতেই বুঝেছিলেন প্রকৃতির সংরক্ষণ ও পরিবেশকেন্দ্রিক যেকোনো সমস্যা সূচনায় ও সমাধানে মানুষকে রাখতেই হবে-” people as individuals, People ar communities, as voters, users of technolog consumers, people in organizations & organized into systems.” তিনি জলবায়ু পরিবর্তনের প্রতিনিধি হিসেবে মানুষকে চিহ্নিত করে তার কার্যাবলিকে বুঝতে চেয়েছেন। মানুষকে কর্মসূচীর অন্তর্গত না করলে যথার্থ অর্থে পরিবেশবিদই হয়ে ওঠা হবে না -“Without understanding people, as the agents of change, we were always going to be frustrated environmentalists.” গ্যাব ব্রাউন মৃত্তিকা-স্বাস্থ্য আন্দোলনের (Soil health movement) একজন পথপ্রদর্শক এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পঁচিশজন প্রভাবশালী কৃষি নেতাদের একজনের। তিনি ‘নো ড্রিল ফার্মিং’ এর কথা বলেন, যাতে ভূ-গর্ভস্থ বাস্তুতন্ত্র (Under ground eco-system) খুবই ভালো থাকে। ‘ড্রিলিং ফার্মিং’ মাটির জন্য প্রয়োজনীয় জীবাণু, অসংখ্য প্রাণী, কার্বন ও অন্যান্য পৌষ্টিক উপাদান গুলি নষ্ট হয়ে উর্বরতা কমে যায়। ‘সয়েল কার্বন ফার্মিং’ এর মাটি কালো ও পরিষ্কার হয়, কারণ এই মাটিতে কার্বন প্রচুর পরিমাণে থাকে। জলবায়ু সঙ্কটের সাথে লড়াই করতে এই ধরনের চাষ আদর্শ কেননা জলবায়ুতে মিশে থাকা কার্বনকে মাটিতে নিয়ে নেওয়া হয়। বায়ুতে প্রায় ৭৫০ বিলিয়ন টন কার্বন আছে। মাটিতে প্রায় ১৫০০ বিলিয়ন টন কার্বন। না বুঝে ক্ষতিকর পদ্ধতিতে চাষ করে করে প্রায় ৫০০ বিলিয়ন টনের বেশি কার্বন মাটি থেকে হারিয়েছি। ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্রিকালচার’ এই বিষয়টিকে দ্রুততর করেছে। ‘ইন্ডাস্ট্রিয়াল এগ্রিকালচার’ বলতে বুঝি শস্য ও প্রাণীর বৃহৎ রকমের নিবিড় উৎপাদন, যেখানে দৈনন্দিন হারে ফসলে রাসায়নিক সার ও প্রাণী শরীরে অ্যান্টিবায়োটিকের ক্ষতিকর ব্যবহার হয়। ‘কার্বন ফার্মিং’ বা ‘রিজেনারেটিভ এগ্রিকালচারে’র মাধ্যমে ভূ-সম্পদের সহনশীলতা, স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা সম্ভব। এই ধরনের চাষে মাটিতে ভালোভাবে জল অনুপ্রবিষ্ট হয়, ফলে জলের বেশিরভাগটাই বেরিয়ে যেতে পারে না।
ভারতের বৃহৎ এবং বৈচিত্র্যময় ভূমি এলাকায় মাটির কার্বন অপসারণের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। মোট ৩২৯ মিলিয়ন হেক্টর (মি হেক্টর) ভূমি এলাকার মধ্যে ১৬২ মিটার হেক্টর আবাদযোগ্য জমি, ৬৯ মিটার হেক্টর অরণ্য ও অরণ্যভূমি, ১১ মিটার হেক্টর স্থায়ী চারণভূমি, ৮ মিটার হেক্টর স্থায়ী ফসলের জন্য ভূমি এলাকা রয়েছে। এবং অন্যান্য ব্যবহারের জন্য ৫৮ মি হেক্টর ভূমি এলাকা। এখন জলবায়ুর নিজস্ব ব্যবস্থায় কার্বন সঞ্চয় ও মুক্ত করার ক্ষমতা, পদ্ধতি আছে যা ‘কার্বন পুল’ (Carbon pool) নামে পরিচিত। অনুমান করা যায় যে ভূমির ৩০ সেন্টিমিটার গভীরতায় ২১ পিজি (পেটাগ্রাম, পিজি ১ x ১০ গ্রাম = বিলিয়ন টন) এবং ১৫০ সেন্টিমিটার গভীরতায় ৬৩ পিজি কার্বন সঞ্চয় করার ক্ষমতা থাকে। ভারতের মাটিতে এই কার্বন জমা ও প্রয়োজন মত খরচ করার ক্ষমতা ১ মিটার গভীরতায় বিশ্বের ‘কার্বন পুলে’র ২.২% এবং ২ মিটার গভীরতায় ২.৬%। বিশ শতকের ছয়ের দশক থেকে অবিচ্ছিন্ন বাস্তুতন্ত্রের পূর্ববর্তী স্তরের তুলনায় চাষকৃত মাটির জৈব কার্বন (SOC) ঘনত্ব ৩০-৬০% হ্রাস পেয়েছে। মাটিতে কার্বনের নিম্ন ঘনত্বের জন্য দায়ী যেমন তেমন ভাবে লাঙ্গল চাষ, ফসলের অবশিষ্টাংশ অপসারণ এবং বারবার খননের ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হওয়া। অতিরিক্ত চাষের মাধ্যমে, সার ব্যবহারের ভারসাম্যহীনতায় তা আরো তরান্বিত হয়। এমনকি জলবায়ু (তাপমাত্রা এবং বৃষ্টিপাত) এবং মাটিতে থাকা কার্বন ঘনত্বের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত কোনো সম্পর্ক বিদ্যমান নেই। ভাবলে অবাক লাগে আগে এই মাটিই কত লক্ষ লক্ষ বছর ধরে অগণিত জনসংখ্যার খিদে মিটিয়েছে, উৎপাদন হয়েছে অথচ এত বছর তার ভান্ডার কিন্তু অপরিবর্তিত থেকেছে। মাটি এমন এক জটিল প্রাকৃতিক আধার যেখানে উদ্ভিদের খাদ্য নানা অবস্থায় জমা থাকে (প্রাপ্য, আংশিক প্রাপ্য ও অপ্রাপ্য অবস্থায়)। ফসল মাটি থেকে তার প্রয়োজনীয় উপাদান ধীরে ধীরে শোষণ করে নেয়, অন্যদিকে মাটির মধ্যে প্রাকৃতিক জটিল প্রক্রিয়ার ফলে সেই ঘাটতি পূরণ হয়। মাটির এই পদ্ধতির প্রকৃতিগত একটি সুনির্দিষ্ট গতি বর্তমান। নাইট্রোজেন, কার্বন, জল সুনির্দিষ্ট প্রাকৃতিক চক্রের আবর্তনের মাধ্যমে মাটিতে আসে। সাবেকি কৃষি ব্যবস্থায় এই নাইট্রোজেন, কার্বন ও জলচক্র’কে কাজে লাগিয়ে ফসল উৎপাদন করা হতো। এতে ফসলের প্রতিটি জাতই ছিল প্রকৃতি সৃষ্ট। বংশানুক্রমিক ভাবে প্রাপ্ত আবহাওয়া ও কৃষিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে মানুষ উৎপাদন করেছে উন্নত জাতের ফসল। কাজে লাগিয়েছে জৈব সার ও কেঁচোর উপযোগিতাকে, দেশীয় সেচ ব্যবস্থা আর সবুজ সারের ব্যবহারে। কিন্তু মানুষ প্রয়োজনের তুলনায় আরো বেশি পরিমাণে ফলন চাইলে এবং একই সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধির কারণে কৃত্রিম সংকরায়ন ঘটিয়ে উচ্চ ফলনশীল ফসল তৈরি হল। এতে দেশীয় জাতের ফসলের চেয়ে কয়েক গুণ বেশি খাদ্য দরকার হল। এখন ব্যাপার হল এই দরকার টা একবার না, বারবার হল কিন্তু মাটির পক্ষে সেই বিপুল অভাব পূরণ করা সম্ভব হল না। অন্তর্ভুক্তি ঘটলো নানা কৃত্রিম জাতের রাসায়নিক সার ও কৃষি বিষের৷ রাজ্যের মাটিতে ক্রমে কমে আসছে গন্ধক, দস্তা, বোরন, মলিবডেনামের মত জৈব কার্বনের পরিমাণও। কোচবিহার, জলপাইগুড়ি, পশ্চিম মেদিনীপুর, বাঁকুড়া, পূর্ব মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও নদীয়ায় মাটিতে এই ঘাটতি দৃশ্যমান। লক্ষণীয় হারে মাটির পরিমাণও কমছে ক্রমশ। মাটি অর্থাৎ ভূমি মাতার আচ্ছাদন ও বৃষ্টিপাতের বৃদ্ধির সাথে পাল্লা দিয়ে জৈব কার্বনের ঘনত্ব বৃদ্ধি পায়। আবার গড় বার্ষিক তাপমাত্রা বৃদ্ধির সাথে হ্রাস পায়। ফসলের অবশিষ্টাংশ, পড়ে থাকা গোবর ও অন্যান্য জৈব পদার্থ মাটিকে স্বাস্থ্যবান করে তুলত। এর অপসারণ মাটিতে ‘ফার্ম ইনপুট’ কমিয়েছে।
চিত্র-৩
সুস্থায়ী কৃষি ও স্বক্ষমতা: সম্পদরঞ্জন পাত্র, ২০১৪ সালের তথ্য অনুযায়ী
মাটিতে কার্বন অভিস্রবণ বাড়ানো এবং নির্গমন কমাতে ব্যবস্থাপনা অনুশীলন-
ক. খামারি ব্যবস্থাপনায় সুষম পুষ্টি, একটি চাষের সঙ্গে আরেকটি চাষের মধ্যবর্তীকালীন বিরতি বাড়ানো, মিশ্র চাষ দরকার। বহুবর্ষজীবী ফসল চাষের জন্য বর্ধিত এলাকা ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও ‘ফার্ম ফরেস্ট ম্যানেজমেন্টে’ কৃষি বনায়ন জরুরি। আগেই জেনেছি যে টার্গেট ফসল ছাড়াও সঙ্গে আরো কিছু গাছ-গাছালি বা যাকে আগাছা বলে জানি, তারও প্রয়োজনীয় ভূমিকা আছে। অত্যাধুনিক কৃষি যন্ত্রপাতি থেকে যে সমস্ত বর্জ্য নির্গমন হয়, তা নিয়ন্ত্রণ করা জরুরি। এবং তাল মিলিয়ে জৈব বর্জ্য অপসারণ বন্ধ করতে হবে।
খ. ‘ল্যান্ডস্কেপ লেভেল ম্যানেজমেন্টে’র মাধ্যমে বনায়ন, বৃক্ষ ও অরণ্যের প্রাকৃতিক পুনর্জন্মকে উৎসাহিত করতে হবে। অবশ্যই অনতিবিলম্বে বন্ধ করতে হবে গাছ কাটা আর তার বিভিন্ন অংশ পোড়ানোর অভ্যাস। সঙ্গে উন্নত পশুসম্পদ ও উন্নত পিট মাটি ব্যবস্থাপনাকে অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।
২.
ভারতীয় লেখিকা কমলা মার্কণ্ড্য রচিত ‘Nectar in Sieve’ উপন্যাসে ভূমিকেন্দ্রিক কৃষিজীবী এক পরিবারের কাহিনী আছে, যা ভারতের আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনের সময়ে চিত্রিত। গ্রামীণ ব্যবস্থার ভাঙন আর বিদেশি উৎপাদন প্রকল্পের মডেল অনুসারে নগরায়ণ ও শিল্পের অনুপ্রবেশের সন্ধিক্ষণ। রুক্মিনীর স্বামী জমিতে চাষ করে, ভূমি যা দেয়- তার ওপরেই ওদের জীবন অতিবাহিত হয়। গ্রামে চামড়া (Tannery) প্রক্রিয়াকরণ শিল্প ও কারখানা তৈরি হয়। লক্ষণীয়-এই কারখানার দায়িত্বে কিন্তু একজন শ্বেতাঙ্গ। গ্রামের অনেকে শ্রমিক হিসেবে কাজ করা শুরু করে এবং মনে করে যে এতে গ্রামের আর্থিক উন্নয়ন হবে। চর্ম শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার সময়কার আওয়াজ- যা শব্দদূষণের সৃষ্টি করে, প্রকৃতিকে ক্ষতিগ্রস্ত করতে থাকে। গ্রামের পশুপাখির ওপর ‘ট্রমাটিক এফেক্ট’ ফেলে। আবার বৃষ্টি, বন্যা, খরার দ্বারাও রুক্মিনীদের ভূমি (মৃত্তিকা, চাষ) কেন্দ্রিক জীবন নিয়ন্ত্রিত হত। রুক্মিনীকে বলতে শুনি “Nature is like a wild animal that you have trained to work for you.” আমরা খেয়াল করব ‘trained’ তথা ‘প্রশিক্ষণ’ শব্দটিকে। প্রকৃতিকে নিজের কাজে লাগানোর প্রয়োজনে প্রশিক্ষিত যন্ত্রপাতি আসছে ও মানুষের ক্ষমতার কাছে গায়ের জোরে আত্মসমর্পণ করানোর তাগিদ স্পষ্ট।
উপন্যাসটিকে যদি ভারতীয় অর্থনীতি ও সমাজগত পরিবর্তনের প্রেক্ষাপটে রুক্মিনীর সুখ অন্বেষণের আখ্যান হিসেবে ধরা হয়, তবে বলতেই হবে যে তার দুর্ভাগ্য আর সুখহীনতার কারণ কোনো শিল্প-কারখানা এককভাবে না, বরং প্রকৃতি সচেতনতা ও বিপন্নতার মুখে প্রকৃতি সংরক্ষণের জন্য প্রয়োজনীয় যথাযথ শিক্ষার অভাবে। রুক্মিনী এবং তার স্বামী নাথন প্রায়ই জমি থেকে গোবর তুলে নিয়ে যায়; এই গোবর জমিতে জৈব সার প্রদান করে। আবার গোবরের ঘুটে ভালো দামে বিক্রি করে তাকে পণ্য করে তোলে কিন্তু জমির উর্বরতা বৃদ্ধির কাজে লাগায় না। আমাদের মনে পড়বে বিবাহ পরবর্তীতে এক সন্তান জন্মানোর পর রুক্মনীর বন্ধ্যাত্বের কথা, ডাক্তার তাঁকে ‘ফার্টিলিটি ট্রিটমেন্টে’র পরামর্শ দেয়। ব্যঞ্জনার্থে তার সত্যিই ঐ উর্বরতা বৃদ্ধিজনিত শিক্ষার দরকার ছিল। আবার ধান বোনার জমিতে আলের জলে মাছ উঠে আসলে নিঃশেষে সমস্ত মাছ জাল দিয়ে তুলে নেয় রুক্মিনীরা, তারা তামি থেকে সার ও পাখিদের খাবার নিয়ে নিয়েছিল। মৃত মাছ ও গোবর থেকে প্রাপ্ত পুষ্টি ধানচারীকে ও জমিতে উর্বর করতে পারত। এই স্বাস্থ্যকর গর্ভাধান আরো ভালো ধান সরবরাহ করতে পারত। রুক্মিনী ধানচাষের জীবনকে রোমান্টিক করে তোলে যখন প্রচুর পরিমাণে ফসল পায়। তার মনে হয় – বীজবপন শরীরকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে এবং বীজ ফোটানো আত্মাকে উন্নত করে। উৎপাদিত ধান দেখা ও ধরে রাখা তার কাছে সবচেয়ে সন্তোষজনক অনুভূতি। ভবিষ্যতের জন্য ধান গোলাজাত করা, যা বিশেষত নারীর সঞ্চয়ী ভাবনা। কিন্তু উৎপাদনের কৌশল যথাযথভাবে তাদের জানা না থাকায় চাষের অবৈজ্ঞানিক ও নিষ্ঠুর কৌশল জমির ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই করে না। যেহেতু ধান কোনো প্রাকৃতিক জলায় জন্মায় না, তাকে তৈরি করতে হয়। জলের তলায় মাটিকে এমনভাবে রাখা হয় যাতে কাদামাটি মিশে আঠালো পদার্থ তৈরি করে, এটিই ক্রাস্ট (Crust) গঠন করে মাটির ওপর (layer, ভূ-ত্বক)। এতে মাটির ক্ষতি হয়, ফলে মাটিতে একই ফসল না ফালিয়ে নানারকম ফসল ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চাষ করাতে হয়। ধান চাষ করতে ধান জমির উপযুক্ত বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে লাগে। বন্যার সময়ে জমিতে জৈব পদার্থ ভেসে জমে- পচে যে মিথেন গ্যাসের জন্ম দেয়, সেই কৃষিজাত রাসায়নিক বিষয়টি ক্ষতিকারক হয়। রয়েছে জলের যথাযথ ব্যবহার সংক্রান্ত শিক্ষা এবং খননকার্যের মাধ্যমে (খনিজ সম্পদ উত্তোলন) জমির ক্ষতি করার প্রসঙ্গ।
ফসলি জমির অনুর্বরতাকে ব্যক্তিগত জীবনের অনুর্বরতার অনুষঙ্গে মিলিয়ে রুক্মিণীদের শিখতে হয় প্রকৃতি সহনশীল উপায়ে উর্বরতা বৃদ্ধির কৌশল, সুস্থায়ী কৃষির ‘জিও-ইঞ্জিনিয়ারিং’। তবেই আয়ত্ত হবে স্ব-ক্ষমতা, আমাদের চরাচরের ক্ষতি না করেই ৷
পর্ব – ২
ধানী সংস্কৃতির প্রতিবেদন
“গোলাভরা ধান গোয়ালভরা গরু পুকুরভরা মাছ / তোর কোথায় গেল ওরে বাঙালী!”
কৃষিই নৃ-গোষ্ঠীর প্রত্নস্মৃতি। বিশ্বব্যাপী কৌম কৃষিপ্রধান গোষ্ঠীর সমাজে গোলার বাইরে এক ছড়া ধান ঝোলানোর রীতি আজও বহালতবিয়তে আছে। আমাদের সমাজ, সংস্কৃতি যার এক্তিয়ারভুক্ত, তাকে ‘বাংলা’ বলি। ভাত আর মাছ বিনে বাঙালী হয়না, তার রক্তেই আছে ‘আয় বৃষ্টি ঝেপে ধান দেব মেপে’র হিসেববোধ। বৃষ্টি থেকে ধরণী গর্ভবতী হবে, উৎপাদিত হবে ধান আর তাতে ঋণ শোধ হবে। স্পষ্টতই এটি একটি মাঙ্গলিক এষণা, তাই এর সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায় লক্ষ্মীদেবীর শ্রী অনুষঙ্গ। ঘরে ঘরে বৃহস্পতিবারের পুজোয় গীত হয়-
“লক্ষ্মীর ভান্ডার যেবা স্থাপি নিজঘরে।
রাখিবে তন্ডুল তাহে এক মুঠা করে।।”
গৃহস্থের সঞ্চয়ের পথ নিশ্চিত করাই এর একমাত্র লক্ষ্য ছিল। সামাজিক এই মঙ্গল কারক- তন্ডুল তথা চাল। শতপথ ব্রাক্ষ্মণে বলা হয়েছে- স যো হ বা অন্নং সমষ্টি যজুরিতি বেদাব হান্নং রুন্ধে যৎ কিঞ্চনান্নেন জয্যং সর্বং হৈব তজ্জয়তি। অন্নকে যে সমষ্টিযজু বলে জানে সে অন্নকে বাঁধে ও অন্নকে দিয়ে যা কিছু জয় করা যায়, যেমন- ক্ষুধা, অভাব দারিদ্র্য, মৃত্যু, রোগ ব্যাধি, অযশকে জয় করে। ঐতরেয় ব্রাক্ষ্মণেও স্বীকার করা হয়েছে যার প্রচুর অন্ন আছে, সে’ই দেশে সম্মানিত। এভাবে অন্নের সঙ্গে সমৃদ্ধি, সামাজিক প্রতিপত্তি আর শ্রী’র তাৎপর্য জুড়ে গেছে। আবার গোব্রাক্ষ্মণের উত্তরভাগে অন্নাদ্বীর্যম বলা হচ্ছে। সুতরাং যথেষ্ট পরিমাণে অন্ন ভক্ষণে বল, বীর্য পাওয়া যাবে- এই ব্যাখ্যা বিশেষ খাদ্যশস্যটির পুষ্টিগুণ সম্পর্কেও অবহিত করে। এতে মূলতঃ থাকে কার্বোহাইড্রেট, যা শক্তি অর্জনে সহায়ক। প্রতি একশো গ্রাম ভাত থেকে ২.৯ গ্রাম প্রোটিন, ২৬ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট ও ০.৪ গ্রাম ফ্যাট পাওয়া যায়৷
ধান অর্থাৎ Oryza Sativa বাংলার তো বটেই, গোটা পূর্ব এশিয়ার প্রধান খাদ্যশস্য। ফলে চাষও হয় ব্যাপকভাবে। ধানের পূর্ব প্রজাতি Oryza Rufipogon বা বুনো ধানের এর বীজ নিয়ে চীনা কৃষকেরা চারাযোগ্য ধান রোপণ করেছিল। কার্যত ধানের দুটি উৎপত্তিস্থল- চীন ও ভারত। চীন ও জাপানে রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বহু বছর আগে ধান চাষ শুরু হয়েছিল। কিন্তু ভারতীয় ধানই গোটা বিশ্বে সভ্যতার মুখপাত্র হিসেবে প্রথম ছড়িয়েছিল ইউরোপের মাধ্যমে। এই যে ধান থেকে অন্ন অর্থে চাল বা ভাতকে বোঝায়, তাতে সুস্পষ্ট অর্থগত এক কালানুক্রমিক সরণ আছে। বৈদিক অর্থে অন্ন বলতে খাদ্য বোঝাত, তৈত্তিরীয় উপনিষদে বলা হয়েছে- অন্নাদ্বৈ প্রজা: প্রজায়ন্তে যা কাশ্চ পৃথিবীং শ্রিতা:, অন্ন থেকেই বিশ্বের সব জীব জন্মায় তথা খাদ্যই জীবনের কারণ। পরাশর মুনির ‘কৃষি সংহিতা’য় যব, বাজরা, মারোয়া প্রভৃতি খাদ্যশস্যের কথা পাই। কৃষ্ণযজুর্বেদের তৈত্তীরীয় সংহিতায় প্রথম ‘বোনা ধান’ অর্থে ‘ব্রীহি’ শব্দটির ব্যবহার মেলে। ক্রমে সংস্কৃত ও পালি সাহিত্যে সরাসরি ধানের কথা আসে। শাক্যমুনি বুদ্ধ সম্বোধি লাভের পর মধু আর বার্লি দিয়ে তৈরি কেক খেয়েছিলেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুর খাদ্য তালিকায় যে কটি শস্যের কথা উল্লেখিত আছে, তার প্রথমটিই হল ‘ওদন’ (Odana)। এর অর্থ ঘি, মাংস ও বিভিন্ন ফলমূল মিশ্রিত সেদ্ধ ভাত। এইভাবে ভাতই হয়ে উঠল প্রধান খাদ্যশস্য। রামায়ণে যে সীতা বাঙালির মন জয় করে নিয়েছিল, মিথ অনুযায়ী সেই সীতাকে আমরা পেয়েছিলাম লাঙলের ফলাগ্রে। ‘সীতা’ অর্থ হলরেখা তথা লাঙ্গল দিয়ে মাটি কর্ষণ করার ফলে মাটিতে যে দাগ পরে। বন্য মানুষের কৃষিকেন্দ্রিক হয়ে এক জায়গায় স্থিত হওয়া আর সভ্যতার সূচনা করার আখ্যানই সীতার আখ্যান। আনুমানিক খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতকের আগে বহু পরিশ্রমে কাঠের ফাল যুক্ত লাঙল দিয়ে বহু পরিশ্রমে স্বল্প জমিতে অগভীর ‘সীতা’ রেখাপাত করা যেত। পরে লোহার ফালে বেশি জমি অল্প সময়ে চষা সম্ভব হল, ক্ষুন্নিবৃত্তির নিবারণ সহজ হল। একারণে ঐ সময়ে উত্তর ভারতে উৎপাদন ব্যবস্থায় গভীর পরিবর্তনের কথা জানা যায়। একইসঙ্গে হালের বলদের প্রয়োজন হওয়ায় বিধান দিয়ে (যেমন শতপথ ব্রাক্ষ্মণে) যজ্ঞে পশুনিধন (ধেনু ও ষাঁড়) বন্ধ করা হল। ফালের কল্যাণে চাষে কম মানুষ নিযুক্ত হওয়ায় যে উদ্বৃত্ত শ্রমিক হল, তাদের কুটির শিল্পে আনা হল। কাঠ, ধাতু, চামড়া, পাথর, মাটি ইত্যাদি দিয়ে ঘরের ও প্রতিদিনের ব্যবহারের প্রয়োজনীয় সামগ্রী নির্মাণের কলাকৌশল শিখল তারা। বলা যায় ধান ও অন্যান্য অপ্রধান খাদ্যশস্য চষাকে কেন্দ্র করে যে কৃষ্টি গড়ে উঠল, এই আনুষঙ্গিক প্রকৌশলগত চর্চা তারই অঙ্গ। মানুষ খেতের পাশেই মড়াইশিল্প শিখল, আলপনা দিল, গরু-ছাগল-হাঁস-মুরগি প্রভৃতি পশুকে গৃহপালিত করে তুলল। মনে পড়বে সীতার দুই সন্তানের একজন কুশ, যা তীক্ষ্ণাগ্র তৃণবিশেষের অপর নাম। ঘরের ছাউনি দিতে ও ধর্মানুষ্ঠানের কাজে এই ঘাস ব্যবহৃত হয়। এইভাবে সীতা তার সঙ্গে খামারি জ্ঞানভাণ্ডার বহন করে কৃষ্টিগত সামগ্রিক রূপের অনুষঙ্গ ধারণ করে থাকে।

বাংলাদেশে মূলত তিন রকম ধানের প্রচলন ছিল- আউশ, আমন, বোরো। আউশ মূলত উচ্চ ফলনশীল আষাঢ়ী ধান। কুমারী, কটকতারা, আটলাই প্রভৃতি এর রূপবৈচিত্র্য। আর হৈমন্তী বা আগুনী ধান আমন যথাক্রমে রোপা, বোনা ও বাওয়া- এই তিন রকমের হয়। আগে বাংলার ধান বলতে আউশ ধানকেই বোঝাত। ভাদ্র মাসে রোয়া ধানগাছের চারপাশে নিড়েন পড়তো রোষণা, চেঁচকো, পাতি, ওকরা, কালেয়া কানছিঁড়ে, কুলপো প্রভৃতি ঘাস টেনে উপড়ে ফেলার জন্য। পৌষে কাটা হয় মুড়ির ধান। বাংলায় মরশুমের সাথে মিলিয়ে যে ধান হত, কিছুকাল পরে সেচ নির্ভরতায় সেই প্রাকৃতিক খেয়ালও কাটিয়ে ওঠা গেল; কার্তিকী ধান বোরো চাষ শুরু হয়। যেমন- পশুশাইল, বানাজিরা, খৈয়াবোরো। এতক্ষণে বোঝা গেছে দেশি ধানের জাতের নামকরণ হত লোকায়ত মনস্তত্ত্ব থেকে। শিষে দানার বুনট অনুযায়ী খেজুরছড়ি, নারকেলছড়ি, বাঁশফুল, তুলসীমঞ্জরী; ধান কাটার মাস অনুযায়ী আশ্বিন ঝরিয়া, পশু পাখির নামে ঘোড়াশাল, বাঘ ঝাপটা, হাতিপাঁজর; আদুরে জামাই আর বউয়ের নাম অনুযায়ী জামাই নাড়ু, বৌ- ভোগ প্রভৃতি। এমনকি মহাকাব্যিক চরিত্রের নাম দিয়েও বাংলার ধানের নাম অজস্র- ভীমশাল, রামসাল, রাধা তিলক। আবার চৈতন্য দেবের ঐতিহাসিকতার প্রভাবে ধানের ‘গৌরনিতাই’ নামকরণও হয়েছে। মনে পড়ে স্যার ড্যানিয়েল হ্যামিলটনের কথা যিনি সুন্দরবনের জনবসতি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। খাদ্য সুরক্ষার অনেক মৌলিক ব্যবস্থাপনার জন্য তার স্মরণে সুন্দরবনের একটি লবণ সহনশীল জাতের ধান ‘হ্যামিলটন’ নামে খ্যাত হয়। সংবাদ প্রভাকরে ১২৫৭ সালের একটি সম্পাদকীয়তে আষাঢ়ী ধান আর তাকে কেন্দ্র করে কৃষকের ওপর হওয়া অত্যাচারের কথা বলা আছে- কৃষকেরা কর্ষণের সময়ে অর্থাৎ আষাঢ় শ্রাবণ মাসে যত পরিমাণে ধান নিয়ে খত লিখে দিত, পৌষ ও মাঘ মাসে তার দেড়া দিতে হত। কিন্তু দৈবত: কারোর জমিতে পর্যাপ্ত ফসল না জন্মালে সর্বনাশ ঘটতো, খতের লিখিত ধান উক্ত নিয়মে পরিশোধ করতে না পারলে ওই দেড়া ধানের খেত লিখে নেওয়া হতো। মৃত্যু ছাড়া চাষীদের সেই ঋণ থেকে উদ্ধার হওয়ার কোনো উপায়ই ছিল না। সেলিনা হোসেনের ‘নীল ময়ূরের যৌবন’ উপন্যাসে দেখি কাহ্ন পাদের গোষ্ঠীর মানুষজন কেউ চাঙ্গারি বুনে, শিকার করে, দুধ ও মদ বিক্রি করে, মুদির দোকান চালিয়ে দিনাতিপাত করে। খিদের জ্বালা তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। নগর থেকে দূরে বসবাসকারী নিম্নবর্গের মেয়ে বিশাখা ধানখেতের স্যাঁতসেঁতে মাটিতে শামুক খোঁজে। পাহাড়ের গায়ে গজিয়ে ওঠা কচি ধানের চারা হাওয়ায় দোলে অথচ সেই ফসলে অধিকার নেই ওদের কারোর। দেশাখ স্বপ্ন দেখে একদিন আর পশুশিকারের অপেক্ষায় তাকে থাকতে হবে না, রাজা নিজে এসে তাকে জমি দেবে, সোনার ফসল ফলবে তাতে। কিন্তু অন্নের প্রাচুর্যে আত্মপ্রতিষ্ঠার লড়াই এত সহজ হয়না, তাদের কল্পনায় সৃজন করতে হয় মাছ-ভাতের উৎসব। আসলে তো অন্নময়তাতেই মনের জন্ম, খিদের নিবৃত্তি না হলে জ্ঞানলাভের ইচ্ছেই আসত না, সভ্যতাও এগোত না। অন্নে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করে যারা, সেই কৃষক আর মজুরেরা চিরকাল পরান্নজীবীদের দ্বারা শোষিত।
চাষীদের মূল কেন্দ্রীয় অন্নকেন্দ্রিক উৎসব বলতে ‘নবান্ন’। মাঠে ধান কাটা শেষ হলে গৃহস্থে শেষ বিড়া বয়ে আনা হয়, তা থেকে অঘ্রাণে চাল তৈরি করে পায়েস হয়। অবশ্যই এই অন্ন লক্ষ্মী দেবীকে উৎসর্গ করা হয়। আর খামার আলপনা দিয়ে সাজিয়ে তোলা হয়। অকৃষি এলাকা বাঁকুড়ায় ‘জিউড় উৎসব’ পালিত হয়। এখানে মূলত জনার অর্থাৎ ভুট্টা হওয়ার প্রবণতা বেশি বলে নতুন ভুট্টা উঠলে তা দিয়েই নবান্ন পালিত হয়। আবার উত্তরবঙ্গের নবান্ন কে বলা হয় ‘নামান’। দীনেন্দ্রকুমার রায়ের ‘পল্লী বৈচিত্র্য’ প্রবন্ধে নবান্ন’র পরিবেশগত বিবরণ চিত্তগ্রাহী। বলাই বাহুল্য নবান্নের আয়োজনের সঙ্গে বাড়ির মহিলারাই যুক্ত থাকেন। এখানে বলা প্রয়োজন ধান কাটা ইত্যাদিতে মহিলা শ্রমিকদের জুড়ি মেলা ভার। ধান কাটার মরশুমে মহিলা শ্রমিক যোগানের জন্য একরকম বিশেষ বিবাহ প্রথা বাংলাদেশে প্রচলিত আছে। ফলন্ত ধানগাছকে নারী শরীরের সৌন্দর্যের সঙ্গে মিলিয়ে দেখার সংস্কৃতি আমাদের আছে-
“চারিদিকে নুয়ে প’ড়ে ফলেছে ফসল,
তাদের স্তনের থেকে ফোঁটা-ফোঁটা পড়িতেছে শিশিরের জল;…আমি সেই সুন্দরীরে দেখে লই—নুয়ে আছে নদীর এ-পারে
বিয়োবার দেরি নাই—রূপ ঝ’রে পড়ে তার—”
(অবসরের গান, জীবনানন্দ দাশ)
এখানেই আসে জিহুড় পার্বণ বা ধানের সাধভক্ষণের কথা। আশ্বিন সংক্রান্তির সময় বহাল জমিতে লাগানো ধান গাছের শস্যে সাদা দুধ জমাট বেঁধে থোড় হয়ে যায়, একেই বলে ধানের গর্ভাবস্থা। বাঙালীর জীবনের বিভিন্ন লগ্নাচারে শিশুর জন্ম থেকে শুরু করে মৃত্যু পর্যন্ত আশীর্বাদে, লাজ বর্ষণে, বধূবরণে, কনকাঞ্জলিতে, অতিথি সৎকারে, এমনকি শ্মশান যাত্রায় তন্ডুলের ব্যবহার বর্তমান।
আগে চাষীরাই ধান বীজ তৈরি করতেন, সংরক্ষণও করতেন। তাদের কাছেই থাকত ‘বীজ রেজিস্টার’। ভারতে সাতের দশকে তথাকথিত সবুজ বিপ্লব ঘটে পাঞ্জাব, হরিয়ানা, মহারাষ্ট্র সহ বিভিন্ন রাজ্যের হাত ধরে। এই বিপ্লবের পরপরই introduced হয়েছে রাসায়নিক সার-বীজ প্যাকেজ, অগণিত জনসংখ্যার পেট ভরাতে হবে। ফলে জৈবসার প্রয়োগ, ক্যানেলসেচ পদ্ধতি বন্ধ হয়ে শ্যালো, ডিপ ও মিনিডিপ টিউবকলের ব্যবহার বাড়ল। এতে ভূমি গর্ভের জলস্তর যেমন নামতে থাকলো, তেমনি অগভীর জলস্তর থেকে আর্সেনিক দূষণের প্রকোপ বাড়ল। আটের দশকের চাষের কাজে যন্ত্রের ব্যবহার আরো বাড়ে। ক্রমে কৃষির পুরোটা না হলেও অন্তত কিছুটায় কর্পোরেট স্থায়ী আসন লাভ করল, উচ্চ ফলনশীল টার্মিনেটর বীজ তৈরি হলো ও বাণিজ্য দায়িত্ব একচেটিয়া পুঁজিবাদী সংস্থার হাতে তুলে দেওয়া হল। অন্য দিকে ১৯৯৪ তে GATT (General Agreement on Tariffs and Trade) চুক্তির ফলে Monsanto জাতীয় কৃষি বহুজাতিক সংস্থার মাধ্যমে জেনেটিক মডিফায়েড বীজ ব্যবহার শুরু হল। প্রচুর দেশি প্রজাতির ধান চলে গেল। এই ধরনের বীজ প্রসঙ্গে বলা হলো যে এতে পোকা লাগেনা। ধান উৎপাদনে জ্ঞানী চাষীভাইরা জানেন পোকা ধানী বাস্তুতন্ত্রের অঙ্গ। যে পোকাকে রাসায়নিক সার দিয়েও পুরোপুরি সরানো যায় না, নতুন রকমের বীজে সেই পোকা একেবারে না লাগা বীজটির জিনগত কৃত্রিম ও ক্ষতিকর পরিবর্তন বিষয়েই আমাদের সচেতন করে তোলে। মানুষের খাদ্য শৃঙ্খলে ঢুকে পড়েছে প্রাকৃতিক এই ছন্দপতনের প্রভাব। স্পষ্টতই কর্পোরেট সংস্থাগুলির আয়ত্তে চলে এসেছে বীজ সংরক্ষণের অধিকার। তারাই কৃষককে তারই জমিতে নির্দিষ্ট কিছু ফসলই ফলানোর বায়না দিচ্ছে নগদ টাকার বিনিময়ে। ফলে ধানের সঙ্গে যে মিশ্র চাষ হতো সেটাও চলে গেল। আগে কৃষকেরা স্বতন্ত্রভাবে নিজের খেয়াল খুশি মতো সারাদিন ধরে খেতে চাষ করত, ‘টোকা’ ব্যবহার করত- তালপাতায় তৈরি ত্রিকোণাকার একরকম ঠান্ডা টুপি। সারাদিনের ক্লান্তি অপনোদনের জন্য ছিল ধেনো-মদও। এসব এখন আর নেই, আমাদের নাগরিকদের ঘর সাজানোর লোকসংস্কৃতির দৃষ্টি আকর্ষণকারী উপকরণে পরিণত হয়েছে। লেখক আনসারউদ্দিনের ‘গো রাখালের কথকতা’য় এই কৃষিকেন্দ্রিক গোষ্ঠী-সংস্কৃতিকে আগলে রাখার প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়। আরেকটি পৃথক বৈঠকি আলাপে তা নতুন করে স্বপ্ন দেখানোর দাবি জানাতে থাকে প্রসব যন্ত্রণার মত। ‘ধান ভানতে শিবের গান’ করে সেখানে নয়া আসর বসানো হবে।
পর্ব – ৩
পরিবেশের অর্থনীতি, কৃষিনির্ভরতা ও
আধুনিক সাহিত্যের কথকতা
১
জোনুই এ নেজনা জুড়্যা বুড়্যা রাখে আল।
ঈষ ধর্যা পাশি সষ্যা পরাইল কাল।।
বাঁট দিয়া কোদালে জুয়ানে দিয়া মলি।
পুরস্কার পায়্যা চলে লৈয়া পদধূলি।।
-কবি রামেশ্বর কৃষিকাজের বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছিলেন শিবকে কেন্দ্র করে। মধ্যযুগের মঙ্গলকাব্যগুলিতে দেবখণ্ডে শিব-পার্বতীর কোন্দলের মূল বিষয় হয়েছে অন্নাভাব৷ ‘শিব সংকীর্তন’ কাব্যে শিবকে সাংসারিক অভাব দূরীকরণে চাষ করতে দেখা যায়। আমাদের অর্থনীতি যে কৃষিপ্রধান, সেই বাস্তবতাই রুদ্র শিবের মিথকে শস্যের সঙ্গে জুড়েছে। কুবেরের কাছে বীজধান সংগ্রহ করে দেবীচক দ্বীপে শিব কৃষিকার্যের সূচনা করেন, সঙ্গে ভীম। চাষের পদ্ধতি বর্ণনা ছাড়াও বিভিন্ন রকমের চালের কথা পাই। অনুমিত হয় কবির উদ্দেশ্য ছিল চাষের গৌরব বৃদ্ধি। ‘অন্নদামঙ্গল’ কাব্যে দেবী অন্নদাকে দেখি শিবের সঙ্গে ঝগড়া করে শিবকে বিপদে ফেলার জন্য দেশে দুর্ভিক্ষ তৈরি করায়। আবার তিনিই পাত পেরে সবাইকে চর্ব্য-চোষ্য-লেহ্য-পেয় খাইয়ে শান্ত করেন। বিজয়াতে দশমীর সকালে দুচোখ ভরে যারা মাঠের ধান দেখে তারা জানতে পারে মায়ের সর্বব্যাপী অন্নপূর্ণা রূপ। দেবী আরাধনায় যে নবপত্রিকা বরণ রয়েছে, তা দেবী দুর্গার শাকম্ভরী রূপটিকে পরিস্ফুট করে। রম্ভা, কচ্চী, হরিদ্রা, জয়ন্তী, বিল্ব, দাড়িমৌ, অশোক, ধান প্রভৃতি নবপত্রিকার কথা আছে। পরিবেশের অর্থনীতি যে কৃষিনির্ভর, তার পরিবর্তনে পল্লীপ্রকৃতির সুষম চেহারা ধসে যেতে পারে- এই সাবধান বাণী কথাসাহিত্যের বিবিধ ক্ষেত্রে চর্চিত হয়ে চলেছে। অনিতা অগ্নিহোত্রীর ‘সুখবাসী’ উপন্যাস বন পাহাড় মালভূমির সঙ্গে মিশে থাকা জনপদ, হাট, গঞ্জ, চষা মাঠ, রোদে পোড়া ধান আর অঙ্কুরে বিনষ্ট শস্যের এক অভিনব বারোমাস্যা। এখানকার আদিবাসী মিথ অনুযায়ী শিব আর ভীমই তাদের মাটিতে বীজ বুনতে বা কৃষিকাজ করার প্রত্ন-জ্ঞান শিখিয়েছে। বিশ্বদরবারে অর্থের লোভে এই কৃষিজ্ঞান, প্রাসঙ্গিক লোকগান বিক্রি করতে চায় কুচক্রী দালালেরা। গ্রামের কেউ কেউও কাঁচা টাকার ফাঁদে পা দিয়ে ফেলে। তবু গোষ্ঠীস্মৃতির চলমান প্রক্রিয়া থেমে থাকেনা।
‘মা মেয়ের ঘর’ আখ্যানে লেখিকা বিশ্বেশ্বরী পঞ্চাধ্যায়ী ১৯৮৩ সালে তাঁর মায়ের মৃত্যুর পরে যে স্মৃতিকথা লিখছেন, তাতে গ্রামকে পরিবেশ প্রকৃতি আর পরিচর্যায় ‘সমগ্র’ হয়ে থাকতে দেখি। পূর্ব মেদিনীপুরের কোনো এক গ্রামে জন্মানো লেখিকার মায়ের শিক্ষাগত দৌড় দ্বিতীয় শ্রেণি অবধি। সেই মেয়ে স্বামীর মৃত্যুর পর কেবল সংসার আগলায়নি, মেয়েকে লেখাপড়া শিখিয়েছেন, সতীনকে আর তার ছেলেকে খাইয়েছেন-পরিয়েছেন। বলতে গেলে জীবনযুদ্ধে একাই আত্মশক্তিতে টিকে থেকেছেন। কিন্তু এই শক্তিই বা কিসের জোরে? বিশ্বেশ্বরীর মায়ের বিয়ে হয়েছিল গ্রামের জমিদারের সঙ্গে। দু বিঘে জমির উপরে বাড়ি আর ছিল আশি বিঘে জমি, তিনশো নারকেল গাছ, আম গাছ, গ্রামের পুকুর৷ পুকুরে মাছ, কাঁকড়ার অভাব ছিল না। তখন জমিদারির প্রাচুর্য বলতে এই সম্পদকেই বোঝানো হত। অর্থাৎ ঘর-মাঠ-ক্ষেত-গরু-চাকর পরিবৃত সমৃদ্ধ সংসার। আখ্যানের ঘটনাকাল যে সময়পর্বকে চিহ্নিত করে, তাতে প্রেক্ষাপটে ছিল ভারত ছাড়ো আন্দোলন (১৯৪২), দুর্ভিক্ষ (১৯৪৩), আইন অমান্য আন্দোলনের মতো রাষ্ট্রীয় ঘটনা। ব্রিটিশ সরকারের রোষে গ্রামের অনেকের সঙ্গে জমিদারবাবুও তাঁর জায়গা জমি হারান। সেই বছরেই ভয়াবহ বন্যায় সমুদ্রে এসে পড়ে গোটা সংসার। কেবল চার বিঘে জমি বেঁচে ছিল, জমিদারবাবুর ছোট গিন্নি তথা বিশ্বেশ্বরীর মা সেই জমির কিয়দংশে পেট ভরানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। কোনোমতে একচালা ঘর বেঁধে একটুও সময় নষ্ট না করে মাঠে যাওয়া, ফসল রোয়া, গরু-বাছুর প্রতিপালন করা, আনুষঙ্গিক দ্রব্য উৎপাদন করে বাজারে বিক্রি করা প্রভৃতি নিয়ম করে করেছেন। লেখিকার কথায়, গরু-ঘাস-হাট-দোকান -কাঠকুটো জ্বালন। কৃষি আর ঘর-গেরস্তির যে সংস্কার বিশ্বেশ্বরী, তার মা আর আরো আগে পূর্বমাতৃকারা অর্জন করেছিলেন সেসবের জ্ঞানই টিকে থাকতে শিখিয়েছে। এক বিঘে মত জমিতে জৈষ্ঠ্য মাসের বৃষ্টিতে ধানের বীজ বুনে দিতেন মা, আষাঢ়ে তার কল বেরিয়ে যেত। বৃষ্টিতে গাছ বেড়ে যেত বহুগুণ, তারপর জল দাঁড়ানো জমিতে কাদা করে ধানচারা তুলে বসাতেন। আগাছা তুলতে নিড়ানি দিতে ভুলতেন না। আশ্বিনে নল সংক্রান্তি, ভোরে পুকুরে ডুব দিয়ে বালিতে বানানো মাঙ্গলিক পুতুল ব্রত কিংবা তুলসিবেদীর উপরে স্বর্গদীপ দেওয়ার উপাচার- প্রভৃতি ব্রত’র প্রতিটি পালন করতেন। গ্রামে কার্তিক-অঘ্রাণে ধান কাটা হতো, তখন শুরু হতো ভিন গ্রাম থেকে মজুর আসার পালা। মজুর পেলে ধান তোলার পর রোদ খাইয়ে আঁটি বাধা আর ধান ঝাড়ার পর্ব চলত।

ধান থেকে চাল বের করার নিয়মনীতি বিশেষ করে জানত মেয়েরাই। আঁটিগুলো ঝাড়া হতো। উঠোনের চারদিক ঝাড়ানো আঁটি দিয়ে ঘিরে দেওয়া হতো। নাহলে ‘হেস’ মানে ভালো খড় দিয়ে হাতে বানানো মাদুরের মতো দেখতে জিনিস দিয়ে খুঁটি পুঁতে তা দিয়ে উঠোনের চারিদিক ঘিরে নিতো যেন ধানগুলো চারিদিকে ছড়িয়ে না যায়। আঁটিগুলো পিটিয়ে ঝাড়ানো হয়ে গেলে দু চারটে কুলো দিয়ে বাতাস করে তার থেকে খড়কুচি ধুলো উড়িয়ে দিয়ে পরিষ্কার করতে হয়, পরে সেই পরিষ্কার ধান ধামায় ভরে ভরে মরাইতে তুলে দেওয়া হতো। এসব তো দীর্ঘদিনের চর্যায় পূর্বনারীরাই জেনে এসেছেন। খাওয়ার জন্য মাঝে মাঝে দু-চার মণ ধান বের করে চাল তৈরি করা হতো। এই প্রক্রিয়াকরণের কোনো একটি ধাপেও কিচ্ছুটি অপচয় হত না। যেমন কুলোয় বাছার সময় চাল হয়নি এমন আগড়া ধান বের করে জ্বালানি, তেল তৈরির কাজে লাগানো হয়। খড়ের আঁটি গরু দিয়ে ভালো করে মাড়িয়ে কিছুটা বিচালি করা হয় আর ভালো খড় মানুষের ঘরে ছাউনি দেওয়ার কাজে লাগানো হয়। ধান মরাই থেকে বার করে তাকে বড়ো বড়ো মেচলায় জল দিয়ে ভেজাতে হতো। তারপর কাঠের উনুনে ধান সেদ্ধ করা থেকে শুরু করে আবার জল ঢেলে একদিন ভিজিয়ে রেখে পরের দিন সেদ্ধ করা পর্যন্ত আরো এক ধাপ চলতো। ধানকে ভালো করে রোদ্দুর লাগিয়ে শুকিয়ে ঠিকমতো তৈরি করা হয়েছে কিনা সেটা মা-মাসিমারা পরীক্ষা করে দেখতেন, তারপরে ঢেঁকিতে দিয়ে ভাঙা হতো। তখন তো কোথাও ধানভাঙা কল বসেনি। এই কাজের জন্য বাড়ির শাশুড়ি বৌমা-রা থাকতই, তাছাড়া পাড়ার মেয়েদের কাউকে ডেকে আনা হতো যারা কাজটা খুব ভালো জানে। বেঁচে ছিল ধান কাটার গান, ঢেঁকিতে পাড় দেওয়ার গান। কুলোয় করে ঝাড়তে গিয়ে চাল আর চালের খুদ মানে ভাঙা দানাগুলো আলাদা করে রাখা হতো। দেখতে গেলে কৃষিকাজের কৃষ্টি শীতের সময়কার আচরণীয় কাজকে অবলম্বন করে থাকে। শীতের সকালে গ্রামবাসীদের প্রায়ই খুদের জাউ খেতে দেখা যায়। ওই সময়েই বাগানে নতুন আলুও উঠত। ছোট ছোট আলু মাঠ থেকে তুলে ধুয়ে ঝাঁটার কাঠিতে গেঁথে জাউয়ের মধ্যে ফেলে দেওয়া হতো। নারকেল কোরাও দিত, অল্প লবণও। এরপর ওই খুদ সেদ্ধ হয়ে গেলে যে ফেণাভাতের মতো তৈরি হতো, তা খেয়েই কাজের লোকজন মাঠে যেত ধান কাটতে বা ঝাড়তে। বিশ্বেশ্বরীর মা জানতেন মাঠ থেকে সদ্য তোলা শাক-সব্জির কোনটা কেমনভাবে কতটুকু মশলায় রান্না করলে, এমনকি কতটা আঁচে ফোড়ন দিলে রান্না ভালো অথচ সুপাচ্য হয়। তিনি বুঝতেন গ্রামের ঘরে ঘরে দুধের অভাব নেই, সুতরাং মাখন-ঘি-দই তৈরি করলেই একমাত্র দুধের সদ্ব্যবহার করা যাবে আর ঘরে অর্থও আসবে। এই নারীরা বাস্তববাদীও তো ছিলেন। নারকেল গাছ থেকে তেল বানিয়ে রান্না করার পাশাপাশি বাড়তি তেলের বিনিময়ে হয়তো খানিক সর্ষের তেল বা অন্য কিছু কিনে কাঁচা টাকার বাজারি ব্যবস্থার উল্টোদিকে নিজের মত করে সুস্থিত বিনিময় ব্যবস্থা বানিয়ে নিতেন। তেলের অভাবে খড়, খোসা দিয়ে লম্ফো জ্বালিয়ে বিশ্বেশ্বরীদের পড়ার ব্যবস্থাও করতেন। তিনি জানতেন মাঠ থেকে ধান ওঠার পর জমির সাদাটে মোলায়েম মাটিই ঘর লেপার উপযুক্ত। পিতৃতন্ত্র বা পুরুষের শাসন ব্যবস্থাকে আমরা নারী-পুরুষ মিলেই শক্ত করেছি দীর্ঘদিন ধরে। স্বামীর আশ্রয়ে, অধীনে থাকা মেয়েরা সৌভাগ্যবতী বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সাবেক সমাজে খেটে খাওয়া বিধবা মেয়ে ‘বেচারা’ অভিধা প্রাপ্ত আজও। বিশ্বেশ্বরীর ছেলেবেলা আর তার মায়ের জীবনচর্যা কোনোদিক থেকেই পাঠকের মনে তাদের সম্পর্কে কোনোরকম অসহায়তার বোধ জাগায় না, আমরা পাঠচর্বণায় জিভ চুক চুক করে ‘আহা রে’ও বলতে পারিনা। বরং পেছনে এক মেরুদন্ডের উপস্থিতি টের পাই, যা আমাদের বাংলার নিজস্ব পরিবেশের সংস্কৃতি তৈরি করে দেয়।
২
বিশ্বায়ন-উত্তর যুগ যত পুঁজি আর পণ্যকেন্দ্রিক হয়ে পড়ছে মেয়েদের জ্ঞান তত অকাজের বলে পরিগণিত হয়েছে। শাক-সব্জি উৎপাদন করা, ফসল তোলা, মুরগি প্রতিপালন, খই-চিঁড়ে-মুড়ি ভাজা প্রভৃতি কাজ নারীরা করলেও হাতে হাতে বিক্রি করে মূলধন পুরুষ জোগাড় করে আনে বলে সে হয় ‘কর্মী’। অথচ যুগ-যগান্ত ধরে আমাদের ঠাম্মা, দিদিমা, জেঠিমা, মায়েরা জানেন কি করে ছোটখাটো অসুখ গাছগাছড়া মশলা দিয়েই সারিয়ে দেওয়া যায়। কিভাবে বাজার না করেও কটা দিন চালিয়ে নেওয়া যায় শাকপাতায়। সাহিত্যিক ও সমাজকর্মী জয়া মিত্র এই সনাতনী জ্ঞানকে ব্যাখ্যা করেছেন ‘উত্তরকন্যা’র ধারায়। পূর্বপুরুষ থেকে উত্তর-পুরুষ পর্যন্ত যে ইতিহাস রক্ষিত হয়, নারী সেখানে ‘অপর’ হয়ে থাকে। নারীর নিজের জ্ঞানের ইতিহাস নথিবদ্ধ হওয়ার প্রয়োজন। ‘অকাজের বউ’ গল্পের উদ্দিষ্ট নারী চরিত্র শহরে বাড়ি-বাড়ি কাজ করে পেট চালাতে গিয়ে একমাত্র বুঝেছিল- পাকা বাড়ি আর কাঁচা টাকার লোভে পুকুরের মাছ, উর্বর জমি, নিজের গ্রাম ছাড়লে কি ক্ষতি হতে পারে। নিজের ঘরের আম-কাঁঠাল, পেয়ারা, লেবু, ফসল থাকতে শহরে কাঁচালঙ্কাটুকুও কেন কিনে খেতে হবে তার যৌক্তিকতা সে বোঝেনি। নারীকে তার পরিবারের কথা ভাবতে হয়। স্বামী, সন্তানকে বাঁচিয়ে রাখতে এক-আধটা মাছ চুরির জন্য অসহায়তা প্রকাশ করে- “এখনও তো ভয়ে ভয়ে চুপি চুপি নিইছি, কেড়ে নিইনি। মাথায় পা দিয়ে আরও বেশি চেপে দিলে শেষে হয়তো একদিন সেও করব। মরতে আর কে চায় বলো মা।” ক্ষমতার আধিপত্য আর তার পাল্টা বয়ান এভাবেই সাহিত্যে হয়ে উঠতে চায় পল্লীপ্রকৃতিকে কেন্দ্র করে।
ঊষালতাও জানে ভাত, জমি, নিজের একটা গ্রাম থাকার মর্ম (‘উন্নয়ন ও গ্রামের লক্ষ্মী’ গল্প)। সে তার পরিবারসহ উদ্বাস্তু হয়েছে পরপর দু’বার। প্রথমবার তথাকথিত উন্নয়নের স্বার্থে গরমেন্টের রাস্তা তৈরির জন্য জমি দখলের কারণে, দ্বিতীয়বারে বিদ্যুৎ বিভাগের হাইটেনশন তার তৈরির কারণে। স্পষ্টতই তথাকথিত উন্নয়নের মডেলে জায়গা হয়নি ঊষালতা, অকাজের বউ-এর পরিবারের মত বহু পরিবারের। ঊষা যখন তেরো বছরের, তখন মহাজনের জমিতে মা ধান রোয়ানোর কাজ করত। সাপে কাটলে মেয়েকে এসে সেই খবর না দিয়ে প্রথমে সজনে শাক আর কুচো মাছ দিয়ে ভাত খেয়ে নিতে বলেছিল। দুমুঠো ভাতের মূল্য বুঝেছিল বলেই। সেই গ্রামেই ঊষার বিয়ে হয়, সে দেখেছে কিভাবে গ্রামগুলো আর গ্রাম থাকে না, গ্রামের গোটা অর্থনীতি পাল্টে যায় তার পরিবেশের চরিত্র বদলে। বদলে যাচ্ছিল গ্রাম, পুকুর-ডোবার তলা ফেটে চাকলা মাটি উঠে আসে, শামুকের চিহ্ন থাকে না, মাঠে একগাছা শাক মেলে না। তার শাশুড়ি না খেতে পেয়ে মরে। প্রথমবারে তারা ভেবে পায়নি বসত বাড়ির পাশে এত বড় মাঠ থাকার সত্ত্বেও রাস্তা কেন তাদেরই বাড়ি উঠিয়ে যাবে। বর্ধমান না দুর্গাপুর থেকে যেন সব গাড়ি-ট্রাক সাঁই সাঁই করে বিহারে দিল্লিতে পৌঁছে যাওয়ানোর জন্য এই রাস্তা হচ্ছিল। ঊষালতাদের দলিল ছিলনা বটে কিন্তু বাড়ি-ঘর সেই কবে করেছে বাপ-ঠাকুরদারা। বুড়াবাটি, জোড়গাছা, বালিডি সহ ছয় গাঁয়ের লোকজনের বসতজমি খেয়েছিল গরমেন্টের উন্নয়ন। নতুন গ্রাম জোড়বাড়িতে ভালো লাগেনা। রাস্তার ধারে চাপাচাপি, মাটি প্রায় নেই বললেই চলে, সোজা রাস্তা, সারাদিন গাড়ি চলে। যাদের বাড়ি ভর্তি গাছ ছিল, জমির ফসল ছিল, আজ অন্যের বাড়ির আগাছা কাটতে হয়। ঊষালতার স্বামী এই করে, মাসের এক দু’দিন বাদ দিয়ে বাকি দিন বেকার থাকে। ঊষালতারা মাঠ পেরিয়ে কাজে যেত, সেই মাঠেও নতুন খুপরি কোয়ার্টার তৈরি হয়েছে। বোঝেনা সে- ইট, কাঠ কি খাওয়া যাবে? ধান চাল লাগবে যে! নতুন গ্রামকে আর গ্রাম বলা যায়না, কারখানা-ফ্যাক্টরি হয়, গায়ে লেপ্টে থাকা ঘরবাড়ি হয়। তবু সুবালা, আশা, শিবানী, উষালতা ২০০ টাকা করে গ্রাম প্রধানকে দিয়ে একফালি জমিতে নিজেদের ফসলটুকু ফলানোর ব্যবস্থা করেছিল। ধান কাটার মরশুমে ফসল কেটে নেওয়ার আর তিন দিন বাকি- এমন সময়ে গরমেন্টের ট্রাকে আসা ‘স্টোনচিপস’ ক্ষেত ঢেকে দেয়। ধানলক্ষ্মীর বুকে পাথর চাপাতে নেই, কিন্তু সরকারি বাবুর স্পষ্ট কথা- “তোমাদের মত লোকেদের বেআইনি কাজের জন্য দেশের উন্নতির কাজ আটকে থাকবে?” পেট পুরে দুটো ভাত, ছেলেপিলের সামনে ভাতের থালা ধরা- এর চেয়ে বেশি সুখ চায়নি ওরা। তবু পরিবেশ, কৃষি আর উন্নয়ন পরস্পর বিরোধী হয়ে যায়। নব্য প্রযুক্তি আসার আগে সেই কোন ভুলে যাওয়া কাল থেকে বাঙালি নারী ধানের সঙ্গে সবচেয়ে বেশি যুক্ত পরিশ্রমসাধ্য প্রক্রিয়ায়। শস্যের সঙ্গে নারীর সম্পর্ক যে অনেক পুরনো, তার খবর মায়েদের কাছ থেকে পরবর্তী প্রজন্মের কাছে পৌঁছয়৷
‘সূর্যের নিজের গ্রাম’ (জয়া মিত্র) কেবল সুরজের ত নয়, আমাদের ভেতরেও ‘নিজের একটা গ্রাম, নিজের একটা নদী’র জন্য আকুতি জাগিয়ে তোলে। এই ‘নিজের গ্রাম’ নিছক শব্দবন্ধ মাত্র নয়, বরং এমন কিছু যাকে আঁকড়ে থাকা যায়। এ হল এমন এক আশ্রয় যেখানে সকলেই ‘হড়’ (মানুষ), সকলের মধ্যে ‘কথাকথি’ আছে, আছে প্রচুর ‘কাঁদর’ আর ‘বতর’ হওয়া মাটি, খেজুরগাছ অবধি কানকো দিয়ে হেঁটে যাওয়া কৈ মাছ আর কাদা থেকে মাছ ধরার জন্য ফাঁদ বানানোর সংস্কৃতি। সেখানে নিয়ম করে পুকুর কাটা হয়, মাটি লেপে কাঠ দিয়ে ঘষে সুন্দর ছবি-নকশা করা হয়, সে জীবনে থাকে কৃষিসংক্রান্ত ডাকের বচন- ছড়াকাটা- গোলা থেকে ধান ঝরার কোমল দৃশ্য, কৃষি আর গো সংস্কার, এমনকি গৃহপালিত পশুগুলির খুঁটিনাটি জানার সপ্রেম আগ্রহ। কিন্তু ঘন জঙ্গল থেকে ক্ষেতজমি, ক্রমে খাদান হল। অথচ কথা তো ছিল মাটির নীচে পাথর থাকবে, মাটির ওপরে থাকবে ক্ষেত-গাছপালা-গ্রাম-নদী-পুকুর; এইরকম থাকাটাই তো নিয়ম। এরপর বহুকাল হল গাঁদাপাতা, কালমেঘের গুণ কিংবা লেবুকাঁটার গাছ তুলে তার শেকড় থেঁতো কাটা জায়গায় লাগানোর জ্ঞান মান্যতা হারিয়েছে। এযাবৎ আমাদের অভ্যাসের বদল ঘটেছে বিপুল, চাষের খরচ বেড়ে গেছে, জমিতে আর লাভ নেই। তবু আকলা, মিলিন্দ, সুরজ, তার দীনুদা আর সৈকতদা’রা জানে এমন আকালে আধশুকনো পুকুর, খেত, ঐ কাঁদর, বাঁধাঘাট, হাওয়া দেওয়া বাঁশঝাড় হারিয়ে ফেলতে নেই। সুরজ দিব্যি শুনতে পায় তার গাঁয়ের সেই ডাক ” ও সুরজ, দোতলায় কাপড়গুলো তুলে নে বাবা, ঝড় আসছে।” এই সমস্ত আখ্যান আমাদের স্মৃতি খুঁড়ে তোলা মাটির ঢিপি আর বিরাট বিরাট গর্ত ভরানোর গল্প।
স্বয়ং সাহিত্যিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও সংস্কৃতির এই গর্ত ভরানোর আকুতি বুঝেছিলেন। পল্লীপ্রকৃতি নিয়ে তাই তাঁর বাস্তবসম্মত চিন্তা-ভাবনা কর্মকুশলতার দিকে এগিয়েছিল।
পর্ব – ৪
রবীন্দ্রনাথের পল্লী উন্নয়ন ও পরিবেশ ভাবনা : প্রসঙ্গে ‘পল্লীপ্রকৃতি’
ক.
শুরুর কথা:
চতুর্দিকে ঘন জঙ্গল এবং অন্ধকারের মধ্যে জল প্রবেশ করে সমস্ত পাতা লতা পচতে থাকে, গোয়ালঘর এবং মানব গৃহের আবর্জনা সমস্ত চারদিকে ভাসতে থাকে, পাট পচা দুর্গন্ধ, জলের রঙ নীল হয়ে ওঠে, উলঙ্গ পেট মোটা পা সরু ছেলে মেয়েরা যেখানে সেখানে জল কাদায় মাখামাখি ঝাপাঝাপি করতে থাকে, মশার ঝাঁক স্থির পচা জলের উপর একটি বাষ্প স্তরের মতো ঝাঁক বেঁধে ভন ভন করতে থাকে— এ অঞ্চলের বর্ষার গ্রামগুলি এমন অস্বাস্থ্যকর আরামহীন আকার ধারণ করে যে তার পাশ দিয়ে যেতে ভয় হয়।
— ২০ সেপ্টেম্বর, ১৮৯৪ সালে কবি ‘দিঘাপাতিয়া জলপথ’ থেকে ইন্দিরা দেবীকে এক গ্রামের দুরবস্থা প্রসঙ্গে এমন কথা লিখেছিলেন। এই পরিবেশের মধ্যে গৃহস্থের মেয়েরা একখানা ভিজে শাড়ি গায়ে জড়িয়ে বাদলার ঠাণ্ডা হাওয়ায় বৃষ্টির জলে ভিজতে ভিজতে হাঁটুর উপর কাপড় তুলে জল ঠেলে সহিষ্ণু জন্তুর মতো ঘরকন্যার নিত্যকর্ম করে। প্রতি ঘরে ঘরে বাতে ধরছে, পা ফুলছে, সর্দি হচ্ছে, জ্বর হচ্ছে, পিলেওয়ালা ছেলেগুলো অবিশ্রাম ঘ্যান ঘ্যান করে কাঁদছে- মানুষের আবাসস্থলে এই অবহেলা, অস্বাস্থ্য অসৌন্দর্য, দারিদ্র্য, বর্বরতা কবিকে চিন্তিত করেছিল। বছর দশেকের রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রচলিতের তুলনায় চলাফেরার ভৌগোলিক পরিধিগত দিক থেকে অনেকটাই সীমাবদ্ধতা অনুভব করতেন। জোড়াসাঁকোর অবরুদ্ধ গতানুগতিক জীবনের অভ্যস্ত ধারা থেকে মুক্তি পেয়ে যেদিন পেনেটিতে ছাতুবাবুর বাগানে সপরিবারে আশ্রয় নিতে হয়েছিল (ডেঙ্গু জ্বরের ভয়ে), সেটি তাঁর স্মরণীয় দিন হয়ে থেকেছে। পেনেটির বাগানে এসেও চলাফেরার নিষেধ শিথিল হলো না, কাছেই বাংলার পল্লীগ্রাম অথচ সেখানে প্রবেশের অনুমতি নেই। পল্লীজীবনকে নিতান্ত কাছ থেকে দেখা বা জানার অবকাশ তখনও সেভাবে আসেনি। আরো বেশ কয়েক বছর পরে তা আসে যখন মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের বড়জামাতা সারদাপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে ও স্ত্রী-বিয়োগ পরবর্তী সাংসারিক কাজকর্মে বীতস্পৃহ জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুরকে পেরিয়ে জমিদারি তত্ত্বাবধানের ভার দ্বিজেন্দ্রনাথ এবং কনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর বর্তায়। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর আবার দার্শনিক ও কবি, তাঁর পক্ষে বৈষয়িক কাজকর্ম দেখাশোনা করা প্রায় অসম্ভব। সুতরাং পরিচালনার যাবতীয় রবীন্দ্রনাথের উপর এসে পড়ল। ১৮৮৯ সাল থেকে ১৯২০ সাল পর্যন্ত সুদীর্ঘ একত্রিশ বছর রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এস্টেটের বেতনভোগী হিসাবে জমিদারি দেখেছেন। এই জমিদারির সঙ্গে তার সম্পর্ক ছিল সর্বমোট পঞ্চাশ বছরের। পদ্মা সংলগ্ন জনপদে পরবর্তী সময়ে যখন রবীন্দ্রনাথ স্থায়ী বাসা বাঁধেন, তখন পল্লীর প্রাণস্পন্দনকে নিতান্ত কাছ থেকে অনুভব করেছেন।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কার্যতই তাঁর ‘জমিদার’ পরিচয়কে অতিক্রম করে পল্লীগ্রামকে তন্ন তন্ন করে জানার চেষ্টা করেছিলেন। জমিদারির কাজকর্ম, হিসাবপত্র, খাজনা আদায়, জমা-ওয়াশীল— এতে কোনোকালেই অভ্যস্ত ছিলেন না…কিন্তু কাজের মধ্যে যখন প্রবেশ করেন, কাজ তাঁকে পেয়ে বসে। এমনকি পার্শ্ববর্তী জমিদারেরাও তাঁর কাছে কর্মচারী পাঠিয়ে দিতেন, কী প্রণালীতে তিনি কাজ করেন তাই জানার জন্যে। এখন প্রশ্ন- যে কাজ কবিকে পেয়ে বসল, তা ঠিক কি? এই কাজ পল্লী-উন্নয়নের কাজ, বলা ভালো পল্লী পুনর্গঠন ও তার প্রকৃতি পরিবেশের আনুকূল্য ফিরিয়ে আনার কাজ; প্রসঙ্গক্রমে কবির ‘দেশ’ সম্পর্কিত চিন্তাভাবনার সুপরিকল্পিত প্রয়োগ প্রচেষ্টা। মৃত্যুর মাত্র এক বছর আগে কবি বাঁকুড়ায় যান (১ মার্চ ১৯৪০) বাঁকুড়ার ম্যাজিস্ট্রেট সুধীন্দ্রকুমার হালদার (আই.সি.এস) ও তাঁর পত্নী কবির স্নেহাস্পদা উষাদেবীর আগ্রহ ও ব্যবস্থাপনায়। পৌঁছনোর পরদিন কবি ‘বাঁকুড়া- প্রদর্শনী’র দ্বার উদ্ঘাটন করেন। এর আগে মণ্ডপে নানা প্রতিষ্ঠান তাঁর প্রশস্তি পাঠ করে। সকল অভিনন্দনের উত্তরে কবি একটি ভাষণ দেন, যেখানে প্রতিবাদ করে বললেন- ধনীবাড়ির সন্তান হওয়া সত্ত্বেও পল্লীগ্রামকে নিরন্তর ভালোবাসার যে দৃষ্টি দিয়ে দেখেছেন তাতেই তাঁর হৃদয়ের দ্বার খুলে গেছে। বৈশাখ ১৩৪৭ সংখ্যা প্রবাসীতে মুদ্রিত হয় ভাষণটি। কবির মৃত্যুর পর, তাঁর জন্ম শতবর্ষে প্রকাশিত ‘পল্লী প্রকৃতি’ গ্রন্থের সর্বশেষ রচনা এই অভিভাষণ। ‘পল্লী প্রকৃতি’ গ্রন্থে সংকলিত রচনার সংখ্যা উনিশ। এর মধ্যে পল্লীর উন্নতি, ভূমিলক্ষী, শ্রীনিকেতন, পল্লীপ্রকৃতি, দেশের কাজ, উপেক্ষিতা পল্লী, অরণ্যদেবতা, হলকর্ষণ, পল্লীসেবা, সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ, বাঙালির কাপড়ের কারখানা ও হাতের তাঁত, জলোৎসর্গ প্রভৃতি কয়েকটি রচনা খেয়াল করলেই পল্লী গ্রামের সার্বিক উন্নয়ন বিষয়ে ভাবিত রবীন্দ্রনাথের মনোভাব স্পষ্ট হবে। ১৯১৫ সাল থেকে ১৯৪০ সালের মধ্যে লেখা প্রবন্ধগুলি থেকে মনে হয় যেন দক্ষ পরিবেশবিদ সূত্রাকারে রচনা করছেন রুটিন। এই সময়পর্বেই আসলে পল্লী গ্রামের সঙ্গে কবির অন্তরের যোগ আক্ষরিক অর্থেই নির্মিত হয়েছিল। এইখানে বলে রাখার যে বিংশ শতাব্দীর গোড়া থেকে ‘কালচার’ শব্দটি নিয়ে বিদ্বজ্জনেরা বিবিধ চিন্তাভাবনা করছিলেন (আচার্য যোগেশচন্দ্র রায়, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ)। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ‘কালচার’কে সবিশেষ ব্যাখ্যা করা ও নির্মাণ করার প্রয়োজনীয়তা বোধ হতে থাকল। এর আভিধানিক অর্থ ঠিক হল ‘রিফাইনমেন্ট’ (Refinement), ‘কাল্টিভেশন'(Cultivation), ‘ডেভলপমেন্ট’ (Development)। ঐ শতকের তিনের দশক জুড়ে রবীন্দ্রনাথ বিব্রত ছিলেন কালচারের সমার্থক ‘কৃষ্টি’ শব্দটি নিয়ে। এটি একটি বৈদিক শব্দ, তথা কর্ষিত ক্ষেত্র বা ভূমি। সেই অর্থে কালচারের সঙ্গে দেশ বা দেশের মানুষ, জাতি- বলা ভালো যে জাতি কৃষিকর্ম জানে, তার সম্পর্ককে বোঝাল। কৃষি ক্ষেত্রে যেমন বীজ বপনের মাধ্যমে এক থেকে বহুর সৃষ্টি হয়, ভূমিক্ষেত্রের কর্ষণ হয়, তেমনি মানুষের সমাজবদ্ধতার সজ্ঞান প্রচেষ্টায় তার বেঁচে থাকার যাবতীয় কিছুর সংস্কার সাধন ও গুণগত মান বৃদ্ধি ঘটে; এও ‘কর্ষণ’। প্রাকৃতিক নিয়মশাসিত জীবনকে সজ্ঞান সচেতন চেষ্টায় বিচিত্র কর্মের বিচিত্রতর নিয়ম সংযমের শাসনে ক্রমশ সংস্কৃত করে তোলাটাই সংস্কার সাধন করা। কবির কাছে কালচার বলতে এই কর্ষণ ও সংস্কার (to improve), সেখান থেকে ‘সংস্কৃতি’। শান্তিনিকেতন-শ্রীনিকেতন পর্বে ‘পল্লীপ্রকৃতি’র প্রতিটি প্রবন্ধেই, গ্রামের স্বাস্থ্য-শিক্ষা-পরিবেশ-রাজনীতি বা স্বদেশী ব্রত প্রসঙ্গে এই কালচারে’র কথা এসেছে।
খ.
সাংস্কৃতিক পুনরুজ্জীবন ও গ্রাম–শহরের প্রভেদ দূরীকরণ:
পল্লীপ্রকৃতির প্রথম প্রবন্ধ ‘পল্লীর উন্নতি’তে কবি পল্লীকেই ‘দেশ’ বলতে চেয়েছেন। কেননা অন্নকে কেন্দ্র করে অন্নসংস্থান করার সুযোগে একত্রিত হওয়ার সামাজিক মনোবৃত্তি থেকেই জনপদ ‘পল্লী’র জন্ম। পল্লীর অন্নভান্ডার ও অন্ন-সংস্কৃতির প্রাঙ্গণে বাঁধা হয়েছিল গ্রাম। এখানে সেই অন্নব্রহ্মের তত্ত্ব (প্রবন্ধ: পল্লীপ্রকৃতি), যার আশ্রয়ে নবান্ন, ধানের সাধ ভক্ষণ, স্বর্গদীপ প্রভৃতি পার্বণ পিড়ি পেতে দেয়। নেপথ্যে বাঙলার নিজস্ব সংস্কৃতিটি চিরবিরাজমান। একে কেন্দ্র করে আস্তে আস্তে সঙ্গীত, শিল্পকলা, সাহিত্য, ধর্মনীতি ইত্যাদি বিচিত্র আয়োজনপূর্ণ আচার-অনুষ্ঠান হয়ে উঠেছে। এহেন পল্লীর অন্ন-জল-চিকিৎসাব্যবস্থা-শিক্ষা ও অর্থনৈতিক সুষ্ঠু কাঠামো গড়ে তুলতে হাত লাগাতে হবে সকলকেই, এই ত ‘দেশের কাজ’। ‘পল্লী’ই আসলে সমাজ, বৃহদর্থে দেশের জনসাধারণ, যারা একইসঙ্গে ধনের উৎপাদক ছিল, ভাগীও ছিল আর পরস্পরের প্রতি সামাজিক কর্তব্য সাধনে একটা সমগ্র (Total) ব্যাপার। কবি খেয়াল করেছেন শিক্ষিত মানুষ ব্যক্তিস্বাতন্ত্রের লোভে, অতিরিক্ত অর্থের লোভে অস্বীকার করে গ্রাম আর তার পরিবেশকে। ঔপনিবেশিক পর্যায়ে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রয়োজনে যখন শহর গড়ে উঠতে থাকল, অর্ধেকের বেশি মানুষ গ্রাম ছাড়ল কাঁচা টাকা হাতে হাতে পাওয়ার জন্য। শুরু হল চাকরি জীবন, তৈরি হল কলকারখানা, বন্দর, কলোনি; ক্রমাগত বেড়ে চলল শহর। অন্যদিকে গ্রামের পরিসর কমতে থাকল, কর্ষণযোগ্য জমিও তাই। অর্থাৎ শহুরে জনসংখ্যা নাগাড়ে বৃদ্ধি পেলেও বরাদ্দ ভূমিলক্ষ্মী তথৈবচ। আবার ফলানো ফসল বাইরে যায় বিদেশীদের খিদে মেটাতে। পুরনো চাষপদ্ধতি ও চিরাচরিত প্রচলিত জ্ঞান খাদ্যশস্য জন্মানোর হার বাড়াতে অক্ষম। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে বিশ্বায়ন- নগরায়ণের যে জোয়ার সবকিছুকে ভাসিয়ে নিয়ে যাবে, ‘আধুনিক যুগ’ বলে যে সময়কাল চিহ্নিত হবে, তার প্রাক্কালে দাঁড়িয়ে কবি বুঝেছিলেন গ্রাম যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষের সামূহিক অবস্থিতি আর অন্ন-জল-বায়ুর সরাসরি সংযোগ নষ্ট হচ্ছে। গ্রাম উৎপাদন করছে আর শহর নির্বিশেষে ভোগ করছে। গ্রাম থেকে যা একবার শহরে যাচ্ছে তা আর গ্রামে ফিরে আসছে না, পূর্ণ হচ্ছে না সুষ্ঠু বিপাকীয় চক্র (প্রবন্ধ: ভূমিলক্ষ্মী)। ‘উপেক্ষিতা পল্লী’তে এটাই আরো স্পষ্ট করে বলছেন, শহর যেন চাঁদের একপিঠের আলো আর আর গ্রাম অন্য পিঠের অন্ধকার। মনে রাখতে হবে কবি কিন্তু শহর বিরোধী নন, শুধু যান্ত্রিক শহর ও গ্রামের মধ্যে পারস্পরিক সেতুবন্ধনের যে অভাব, তার বোধ থেকেই পল্লী পুনর্গঠনের কথা বলেন, মনে করান সমাজ-স্বার্থের কথা। স্পষ্টতই বলছেন- “দায়ে পড়ে নিজের সকলপ্রকার অযোগ্যতা সত্ত্বেও কাজে নামতে হল। যাতে কয়েকটি গ্রাম নিজের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, আর্থিক উন্নতি প্রভৃতির ভার সমবেত চেষ্টায় নিজেরা গ্রহণ করে আমি সেই চেষ্টায় প্রবৃত্ত হলুম। দুই-একটি শিক্ষিত ভদ্রলোককে ডেকে বললুম, তোমাদের কোনো দুঃসাহসিক কাজ করতে হবে না—একটি গ্রামকে বিনা যুদ্ধে দখল করো।” এক একটা গ্রামের দায়িত্ব অবস্থাপন্ন ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকে যেন নেন। পরে যদিও এই ভাবনা থেকে সরে আসবেন ‘শ্রীনিকেতনের ইতিহাস ও আদর্শ’ প্রবন্ধে। তাঁর শান্তিনিকেতন আত্মশক্তি, সাহস, ভিত্তি স্তরে কাজ করার প্রবণতা দিয়ে নির্মিত হয়েছিল। ১৯২২ সালের ৬ ফেব্রুয়ারিতে পল্লী উন্নয়ন বিভাগের কেন্দ্র সুরুল স্থাপিত হয় শান্তিনিকেতন কুঠিতে। ১৯২৩ সালে শান্তিনিকেতনে বৃক্ষাবাস স্থাপিত হয়। এরও পাঁচ বছর পরে ১৯২৮ এ বৃক্ষরোপণ ও হলকর্ষণ অনুষ্ঠিত হয় শান্তিনিকেতনে। ১৫ জুলাইতে নন্দলাল বসু প্রাচীরগাত্রে হলকর্ষণ উৎসবের ফ্রেসকো রচনা করেন। ১৩৩৬ বঙ্গাব্দের শ্রাবণ মাসের এই উৎসব ‘সীতাযজ্ঞ’ নামে পরিচিত হয়েছিল।
গ.
স্বায়ত্তশাসিত গ্রাম পরিকল্পনায় সমবায়নীতি প্রণোদিত এক অর্থনৈতিক বন্ধন:
ধনীদের কল্যাণে গ্রাম ভালো ছিল- এই ব্যবস্থা স্বীকার করলেও তা কার্যকর হোক, কিছু পরে নিজেই আর চাননি কবি। পরিবর্তে তিনি সমবায়িক শক্তির কথা বললেন। সকলের যা সম্বল আছে সামর্থ্য আছে তা একত্র করলে অনায়াসে ট্রাক্টর দিয়ে সকলের জমি চাষ করা চলবে। সকলে একসঙ্গে কাজ করলে জমির সামান্য তারতম্যে কিছু যায় আসে না। এতে করে লভ্যাংশ যেমন ভাগ করে নেওয়া যাবে তেমনি সমস্ত ফসল গ্রামের একটি জায়গাতেই রাখা সম্ভব হবে এবং সেখান থেকে মহাজনেরা প্রয়োজনে উপযুক্ত মূল্য দিয়ে কিনে নিয়ে যেতে পারবে। এধরনের সমবায়িক বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতির সাহায্যে অর্থনীতিতেও স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তুলতে প্রকৃতির দান আর মানুষের জ্ঞান- এই দুইকেই সহযোগী রূপে চেয়েছেন। একসময়ে মাড়াই কল আর তার যন্ত্রের মাধ্যমে গ্রাম দেশ দেশান্তরকে চিনি আর কাপড় জুগিয়েছে। কবির কথায়- “তখন শ্রী ছিল তার ঘরে, কল্যাণ ছিল গ্রামে গ্রামে।” যেখানে অন্ন আর ধন পরস্পর হাত ধরাধরি করে আছে, তাকেই গ্রহণ করতে পরামর্শ দিয়েছেন। এমনকি শহরের যন্ত্রদানব এই সুসম্পর্কের দিকে রক্তচক্ষু পাকালে দেশের মানুষকে নিজেদের উদ্যোগে নিজের অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা বজায় রাখতে হবে। ‘অর্থনৈতিক স্বনির্ভরতা’ অর্থে কিন্তু সংস্কৃতিকে ধারণ করেই খাওয়া-পরার যে স্বচ্ছলতা, সেই বিশেষ সামঞ্জস্যপূর্ণ অবস্থান। যারা বিলাতের আমদানি কোন কল চালিয়ে কাপড় না বুনে নিজেদের হাতের শ্রম ও কৌশলকে প্রধান অবলম্বন করে তাঁত বোনে, সেই দেশি তাঁত শিল্পকে বাঁচিয়ে রাখতে উদ্বুদ্ধ করেছেন। বোঝাতে চেয়েছেন যে বাংলার শিল্প আপনাকে তুলে ধরতে অপর কোনো দেশের প্রাকৃতিক সম্পদ ছিনিয়ে নিয়ে ব্যবহার করেনা। যেমনটা ঔপনিবেশিক ভারতবর্ষে বোম্বাইয়ের কারখানায় দক্ষিণ আফ্রিকার কয়লায় কল চালিয়ে কাপড় তৈরি হয়। কুটির শিল্পের উন্নতি চিন্তাও তাঁর মাথায় ছিল। বয়নশিল্প শেখাতে শ্রীরামপুরে নিয়ে যান একজন তাঁতিকে, স্থানীয় একজন মুসলমান জোলাকে পাঠানো হয় শান্তিনিকেতনে তাঁতের কাজ শিখতে। তিনি এসে খোলেন তাঁতের স্কুল। পুত্র রথীন্দ্রনাথকে লিখছেন- বোলপুরের ধান-ভাঙা কলের মত একটা কল পতিসরে আনতে পারলে বিশেষ কাজে লাগবে। এখানকার চাষীদের কোন ইন্ডাস্ট্রি শেখানো যেতে পারে সেই কথা ভাবছিলেন। ভাবছেন পটারি শিল্প গ্রামে তৈরি করা যায় কিনা, ছাতা তৈরির শিল্প চাষীদের শেখানো যায় কিনা অথবা টালি বা খোলা তৈরির কারখানা। দেশের কাজের কথা বলতে গিয়েও পল্লী কেন্দ্রিক উন্নয়নকে লক্ষ্যে রেখে নানান কর্মসূচি নির্দেশ করেছেন। দেশব্যাপী মানুষের নিজেদের মধ্যে আত্মীয়তা বাড়ানোর স্বার্থে কবি দেশের উৎপাদিত পদার্থই ব্যবহার করতে বলেন৷ ১৯০৬ সালে কৃষিবিদ্যা ও গোষ্ঠ বিদ্যা শেখাতে পুত্র রথীন্দ্রনাথ ও বন্ধু সন্তোষ চন্দ্র মজুমদারকে আমেরিকা পাঠান, উদ্দেশ্য গোপালন ও দুগ্ধ শিল্পকে মজবুত করে গড়ে তোলা। পরের বছর মীরাকে বিয়ে দিয়ে জামাতা নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলীকেও কৃষিবিদ্যা পড়ার জন্য পাঠান। ১৯০৯ সালে রথীন্দ্রনাথরা বিদেশ থেকে ফিরে কবির তত্ত্বাবধানে শুরু করেন বৈজ্ঞানিক প্রথায় চাষ, সার, পাম্প ইত্যাদির ব্যবহার। কৃষি বাড়ি সংলগ্ন আশি বিঘা খাস জমিতে চালু হয় সুদূর ভবিষ্যৎ মুখী কৃষি গবেষণাগার। ভাবলে বিস্মিত হতে হয় যে জমিদারী এস্টেটকে ওয়েলফেয়ার এস্টেটে রূপান্তরিত করতে পেরেছিলেন কর্মযোগীর মত। কবিবন্ধু এলমহার্স্ট কৃষি বিষয়ক বহু গ্রন্থ, যন্ত্র-সরঞ্জাম ও অর্থ নিয়ে শ্রীনিকেতনে এসে পল্লী উন্নয়ন পরিকল্পনাকে গতি দেন। সুরুল গ্রাম পুনর্গঠন কেন্দ্রের নাম হয় ‘স্কুল অফ এগ্রিকালচার’। রবীন্দ্রনাথকে চ্যান্সেলর করে এলমহার্স্ট, সন্তোষচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও গৌর গোপালকে নিয়ে কর্ম সমিতি তৈরি হয়। ঐসময়ে নতুন ‘ইন্ডিয়ান অ্যাক্ট’ অনুযায়ী গ্রামে যে পঞ্চায়েত গঠিত হয়েছে তার দ্বারা গ্রামের কতটা উন্নতি হবে এ বিষয়ে সন্দিহান ছিলেন কবি। তাই ঐ পঞ্চায়েত শিক্ষা, স্বাস্থ্য, শান্তি রক্ষা ও কর আদায়ের দায়িত্ব পেলেও রবীন্দ্রনাথ নিজেদের নির্দিষ্ট এলাকার প্রায় স্বয়ম্ভর গ্রাম পরিকল্পনার কাজে আত্মনিয়োগ করেন, গড়ে তোলেন পল্লি সমিতি। পল্লীর মানুষের নানা অর্থনৈতিক প্রয়োজন পূরণকল্পে সমবায় ব্যাঙ্ক এবং বিপর্যয় কিংবা প্রয়োজন ভিত্তিতে তাদের কৃষিঋণ দেওয়ার জন্য কো-অপারেটিভ লোন সোসাইটি স্থাপন করেন। ইতিমধ্যে মিতব্যয়িতা, সংঘকর্ম ও সঞ্চয় অভ্যাস শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেছিলেন। টাকায়, মনে, শিক্ষায় একজোট হয়ে জীবন ও জীবিকানির্বাহ করার যে উপায় ‘কো-অপারেটিভ’ প্রণালী বলে পরিচিত, ‘সমবায়’ শক্তি বলতে কবি তা’ই বুঝিয়েছেন।
ঘ.
স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও পরিবেশ সচেতনতা:দেশের অন্যতম প্রধান কাজ গ্রামে গ্রামে স্বাস্থ্য ফিরিয়ে আনা, তা করতে গিয়েও সমষ্টিগত প্রচেষ্টায় সেই মিলিত হবার আনন্দকে বৃত্তের কেন্দ্র করছেন। প্রসঙ্গক্রমে ‘সমবায়ে ম্যালেরিয়া নিবারণ’ প্রবন্ধে ডাক্তার গোপাল চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সহযোগিতায় বঙ্গে যে রোগের প্রাদুর্ভাবে একসময়ে গ্রামকে গ্রাম উজাড় হয়ে যেত, তা নির্মূল করার কথা উল্লেখ করেন- “গোপালবাবু যে ব্যবস্থা করেছেন, যাকে পল্লীসেবা বলা হয়েছে, তার অর্থ তোমরা একত্র সমবেত হয়ে তোমাদের নিজের চেষ্টায় তোমাদের দুঃখ দূর করো।” লক্ষণীয়, ম্যালেরিয়া নিবারণী কর্মদ্যোগ গ্রহণে আহ্বান জানিয়ে আসলে বিদ্বান মূর্খ সকলের মিলিত হওয়ার এক সহজ ক্ষেত্র তৈরি করতে চেয়েছেন। ইউরোপ ঘুরে দেখেছিলেন সেখানকার গ্রাম আর শহরের মধ্যে শিক্ষাগত অদ্ভুত ও প্রকট প্রভেদ নেই। সেখানে গ্রামবাসীরা নিজেদের মনের স্বাস্থ্যকর পুষ্টি সম্পর্কে সচেতন থাকে; যোগ্যতা থাকলে তাদের কর্মসংস্থানের অভাব হয়না। কিন্তু নিজের দেশের পল্লী আর শহরে জ্ঞানের পার্থক্য দেখে ব্যথিত হয়েছিলেন কবি। দরকার গণশিক্ষা, এর কানটি ধরে টানলেই পিছে পিছে আসে স্বাস্থ্যসচেতনতা, সাংস্কৃতিক ও আর্থিক স্বনির্ভরতা। এই শিক্ষা যেন ‘দান’ না হয়, বরং গ্রামবাসী আর শহুরে সবজান্তা শিক্ষকের মধ্যে যে যোজন দূরত্ব, তাকে নির্মূল করতেই এক সার্বিক মিলনক্ষেত্রের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। তিনি বাংলার জলকষ্ট বিষয়ে বিশেষত মেয়েদের যন্ত্রণা অনুভব করেছিলেন, যেহেতু ঘর-গেরস্থালি, রান্না, খাবার খাওয়ানো মেয়েদের দায়িত্বে। গ্রামবাংলা ভোগে হয় জলের অভাবে নয় বাহুল্যে। তার প্রধান কারণ পলি ও পাঁকে নদীগর্ভ আর জলাশয়তল বহু কাল থেকে অবরুদ্ধ আর অগভীর হয়ে পড়ে থাকে। বিশ্বভারতীর সেবাব্রতী গণের মধ্যে প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখ করে বলেছেন যে তিনি পাঁক তুলে বহু জলাশয় পুনরুদ্ধার করেছিলেন। কার্যত গ্রামবাসীদের মধ্যে কৃষিপ্রধান ও রোগমুক্ত পল্লী পুনর্গঠনে পরিষ্কার জলের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করতে কম চেষ্টা চালাননি কবি নিজে ও তাঁর সহকারীবৃন্দ। কূপ খনন, নলকূপ স্থাপন, নতুন পুকুর খনন ও পুরনো পুকুর সংস্কার করে গেছেন বিভিন্ন সময়ে। শ্রীনিকেতনে ছাত্রদের খাবার ঘর ও রান্নাঘরে বর্জ্য দূষণ আর জল দূষণ নিয়ন্ত্রণ করতে পাকা ড্রেনের নকশা নিয়ে রবীন্দ্রনাথ এন্ড্রুজের সঙ্গে বিজ্ঞানসম্মত পর্যালোচনা চালিয়েছিলেন। স্নানের জল নষ্ট না করে আশ্রমের সব্জির বাগানে পাইপলাইনে নিয়ে আসা হতো। বলা বাহুল্য এই বাগান থেকেই আশ্রমের রান্নাঘরের খাদ্য আসত। জলের এই ‘রি-সাইকেলিং’ পদ্ধতি গুরুত্বপূর্ণ। নিজে হোমিওপ্যাথি ও আয়ুর্বেদিক চিকিৎসা রীতিমতো অভ্যাস করেছেন। এও বলছেন যে কৃষি থেকে প্রকৃতির সঙ্গে সখ্যতা, সেখান থেকে জনসমবায় এবং ধর্ম ও ঐক্যবন্ধনে বাঁধা যে পল্লীপ্রকৃতি, সময়ের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তাকেও শিখতে হবে যন্ত্রবিদ্যা। তবে হয়ে উঠবেনা যন্ত্রসর্বস্ব, বরং সনাতন জ্ঞানের সঙ্গে আধুনিক যন্ত্রের (মানবকল্যাণের অনুকূল যন্ত্র) জ্ঞানও এসে মিশবে, ছুটবে উন্নয়নের রাজরথ- এমন স্বপ্নই ছিল কবির। নববাবুদের নাগরিক উন্নাসিকতা দিয়ে যে গ্রামের তথা দেশের উন্নতি হবে না একথা মানতেন রবীন্দ্রনাথ। ‘হলকর্ষণ’ ও ‘অরণ্যদেবতা’ প্রবন্ধে বলছেন সুস্থ প্রতিবেশ, বাস্তুতন্ত্র নির্মাণের কথা। নিজেদের খিদে মেটাতে বসুধার প্রাণরস সিঞ্চন করে মাটিতে হলকর্ষণ করে যে ফসল আদায় করি, তার বিনিময়ে বৃক্ষরোপণ করে মাটিকেও যেন কিছু ফিরিয়ে দিই- এ শিক্ষা চিরন্তনী। কার্যত পল্লীর উন্নয়নপন্থায় কল্যাণকারী অরণ্যের ক্ষতি না করে তার সঙ্গে সহনশীল পারস্পরিক সহাবস্থানের কথা সর্বত্র ব্যক্ত হয়েছে। সমাজ-অর্থনীতি কেন্দ্রিক পরিবেশভাবনা এখানে গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হয়ে থেকেছে। এমনকি কথকতা, কীর্তন, যাত্রাপালা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে পল্লীর যে নিজস্ব সংস্কৃতির ধারাটি প্রবাহিত, ইউরোসেন্ট্রিক কালচারের দুনিয়ায় তাকে বাংলার নিজস্ব মেরুদন্ড হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন কবি। বহুজাতিক সংস্থা ও বিশ্ব বাণিজ্যের ব্যবস্থার দ্বারা যখন আমাদের বাণিজ্য ও কৃষি, নগর ও গ্রাম সার্বিকভাবে আক্রান্ত তখন এই পল্লী উন্নয়ন চিন্তার চর্চা আমাদের নতুন এক পথ দেখাতে পারে বলে মনে হয়। কৃষি-সমবায়, শিক্ষা-সমবায়, স্বাস্থ্য-সমবায় ও শিল্প-সমবায়ের আন্দোলনকে পরিব্যাপ্ত রূপ দিয়ে তার প্রধান অবলম্বন রূপে গ্রাম-মন্ডলী গঠনের যে মডেল তিনি উপস্থাপিত করেছিলেন, তা আজও শিক্ষণীয়। যে শ্রেষ্ঠত্বের দিকে লক্ষ্য রেখে চর্যার সামূহিক উত্তরোত্তর কর্ষণে সকল মানুষের জন্মগত অধিকার, সেই অধিকার যে পল্লীবাসীর উপরেও বর্তায়, এই বার্তাটি প্রায়োগিক ভাবেই ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এক অর্থে এই আলোচনা পল্লী আর পরিবেশ-প্রকৃতির স্বাধিকারের স্বার্থও ঘোষণা করে।
পর্ব – ৫
পরিবেশ- পুরানো সেই দিনের কথায়
Nature is pure, supporting all forms of life and abundant resources while environment is shaped by human activities and more man-made, triggering scarcity and corruption of resources.
অর্থাৎ পরিবেশ বলতে বাহ্য উপাদানগুলির সমন্বয়গত সেই পরিস্থতিকে বোঝায়, যা কোনো জীব বা প্রজাতির প্রাণধারণ ও বিকাশকে প্রভাবিত করে। যখন থেকে ধনতন্ত্র নিজের উন্নয়নের স্বার্থে প্রকৃতিকে পণ্য করলো, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির সমন্বয় তাকে গতি দান করলো, তখন থেকেই প্রকৃতির স্বাভাবিক আশ্রয় থেকে বিচ্যুত হয়েছি আমরা। মনে রাখার যে অষ্টাদশ শতকে শিল্পবিপ্লবের (১৭৫০ সাল) পর ক্রমপ্রসারিত শিল্পাঞ্চলগুলিতে স্থানীয় ও পারিপার্শ্বিক বায়ুমণ্ডল, জলবায়ুর উপর কারখানা থেকে নির্গত অ্যাসিড, ধোঁয়া, তাপপ্রবাহের প্রভাব সম্পর্কে তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়েই গোয়েথ কার্লাইল (Goethe Carlyle) প্রথম ‘এনভায়রনমেন্ট’ শব্দটি প্রয়োগ করেন ১৮২৮ খ্রিস্টাব্দে।
ভারতের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে ঔপনিবেশিক শাসন ও পরপর দুই বিশ্বযুদ্ধের পর দেশীয় প্রকৃতিলগ্ন উৎপাদন নীতিটি হ্যারি ট্রুম্যান কথিত নতুন উৎপাদন নীতির দ্বারা (‘To develop produce more’) প্রতিস্থাপিত হলে এমন এক যুগের সূচনা হয়, যখন চেয়ে বা না চেয়ে পরিবেশ (environment) ও প্রতিবেশের (ecology) চিন্তা আমাদের দৈনন্দিন জীবন-ভাবনায় ঢুকে পড়েছে; দীপেশ চক্রবর্তীর মতে এ এক বিশেষ ‘গ্রহের যুগ’ (planetary age), পরিবেশ বিপন্নতা এই যুগের নিজস্ব সমস্যা। বাধ্যত এই সময়ে আমাদের অর্জন করতে হয়েছে পরিবেশ-চর্চার শিক্ষা, গত তিন দশকের বেশি সময় ধরে ‘এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স’ আমাদের পাঠ্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত। চরাচরের আলো, জল, বায়ু, গ্যাস, তেল, মৃত্তিকা, পাথর, উদ্ভিদসহ সমস্ত জৈব ও অজৈব উপাদানের গুরুত্ব বুঝে তার ব্যবহারিক (use value) ও অস্তিত্বের মূল্য (existence value) নির্ধারণের দায় হঠাৎ একদিনে বিশ শতকের শেষভাগে এসে উপস্থিত হয়নি। ধনতন্ত্রের বিকাশ ও নগরায়ণের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি বিশ্বজনীন চরিত্র অর্জন করলেও তার ক্রমিক রূপান্তরের সঙ্গে তাল মিলিয়ে সংরক্ষণের যথাযথ বন্দোবস্ত গৃহীত হয়নি। পরিবেশবিজ্ঞান অনুযায়ী পরিবেশ-চেতনার বিজ্ঞানসম্মত ভিত্তি হলো ভৌত পরিবেশ (physical environment)।

ঔপনিবেশিক আমলে পরিবেশের সঙ্গে কেবল বসতিভিত্তিক পন্থায় স্থাপিত সম্পর্ককে অর্থাৎ স্থায়ী বসতির কৃষিভিত্তিক জীবনকে স্বীকার করা হত। কেননা তাতে ভূমি রাজস্বের জোগান তো হতই, সঙ্গে কৃষিপণ্যের রপ্তানি বাড়ত, যার গুরুত্ব উনিশ শতকীয় ঔপনিবেশিক শাসন ও শোষণের মৌলিক কাঠামোয় অপরিসীম ছিল। রপ্তানি উদ্বৃত্ত বজায় থাকলে মুনাফার মাধ্যমে পুঁজিবাদী স্বার্থও বজায় থাকত। এই সময়ে কয়েকজন ব্রিটিশ প্রকৃতিচর্চাকারী, মূলত কোম্পানির কাজে নিযুক্ত শল্যচিকিৎসকেরা অরণ্য সংরক্ষণের দাবি তোলেন। আমাদের মনে পড়বে রানাল্ড মার্টিনকে, যিনি চাকরিসূত্রে কলকাতায় এসে ১৮২০ সালের বার্মা যুদ্ধ-পর্বে ইউরোপীয় সেনাদের নানা অসুখে ভুগতে দেখে কলকাতার প্রাকৃতিক পরিবেশ, সেখানকার মাটির বিবর্তন, জলবায়ুর ধরন নিয়ে পরীক্ষা চালান। তিনিই প্রথম বাংলার জলবায়ু, স্বাস্থ্য ও উন্নয়নের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ককে জনসমক্ষে আনেন এবং বনবিভাগ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতে বন সংরক্ষণ কার্যক্রমকে প্রাতিষ্ঠানিক করে তোলেন। তিনি কলকাতায় যে ‘ফিবার হাসপাতাল’ (fever hospital) তৈরি করেছিলেন, সেখানে বাংলায় চিকিৎসা-ব্যবস্থার উন্নতি বিধানের পদ্ধতি-প্রকরণ নিয়ে একটি কমিটি তৈরি হয় ১৮৩৫ সালে। উক্ত কমিটিতে ডাক্তার মধুসূদন গুপ্ত (১৮০০-১৮৫৬) কলকাতার সংকীর্ণ রাস্তা, নোংরা জল ও জঞ্জাল ভর্তি পয়ঃপ্রণালীকে রোগের আঁতুড়ঘর হিসেবে ব্যাখ্যা করেন। এমনকি তিনি কলকাতার অধিকাংশ উচ্চবিত্ত কর্তৃক ব্যবহৃত গঙ্গার জলকেও পানযোগ্য বলে মনে করেননি। তখন নেটিভ কলকাতার পুকুরের জলও পানের উপযুক্ত ছিলো না, ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যা অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি করত। ড. মধুসূদনের মতে- যথাযথ বায়ু চলাচল, জল নিষ্কাশন ও সেই সঙ্গে পানীয় জলের উপযুক্ত ব্যবস্থা করলে কলকাতাকে একটি স্বাস্থ্যকর স্থান হিসেবে গড়ে তোলা সম্ভব। তিনি তাঁর আলোচনায় ধুলোর ক্ষতিকর দিকের কথাও বলেন, অর্থাৎ ধুলো সংক্রান্ত দূষণের কথা (dust pollution) তুলে ধরেন। মধুসূদন গুপ্তর এই বিবৃতি থেকে কলকাতা ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলের জনস্বাস্থ্যের এবং পরিবেশের বিস্তারিত, পুঙ্খানুপুঙ্খ চিত্ররূপ মেলে। শতাব্দীর গোড়া থেকে শহর কলকাতায় পানীয় জল সংক্রান্ত সমস্যা ছিলো। উত্তর কলকাতায় বাড়ির ভিতর পুষ্করিণীর জল ততোটা ভালো ছিল না। সাহেবরা বর্ষার জল ধরে রেখে ব্যবহার করতেন আর ১৮০৫ থেকে ১৮৩৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হেদো, পটলডাঙার গোলদিঘি, বহুবাজারের গোলদিঘি, মাদ্রাসার দিঘি, চাঁপাতলার তালাও, সুরতিবাগান পুকুর প্রভৃতি খনন করা হয় বিশুদ্ধ পানীয় জলের জন্য। ১৮২০ সালে পাকা জলপ্রণালী (aquaduct) প্রস্তুত হলে চাঁদপাল ঘাটে দমকলের সাহায্যে গঙ্গাজল তুলে ধর্মতলা, চৌরঙ্গি, লালবাজার, বহুবাজার, কলেজ স্ট্রিটে ব্যবহার করা হত।
উনিশ শতকের ষাটের কোঠায় ড. গুডিব চক্রবর্তী কলকাতার পানীয় জল সম্বন্ধে বক্তৃতা করেন। ১৮৬৫ সালে জল-কল প্রতিষ্ঠার সূচনা হল এবং অব্যবহিত পরেই শহরে ওলাইচণ্ডী রোগের হ্রাস বোঝা গেল। জ্যোতিরিন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর জন্ম ১৮৪৯ সালের ৪ মে। তাঁর শৈশবকে ষাটের দশক পর্যন্ত টেনে নিয়ে গেলে তা থেকে জানা যায় (শ্রী বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রণীত জ্যোতিরিন্দ্রনাথের জীবনস্মৃতি থেকে) যে তখন কলকাতায় খোলা নর্দমা ছিলো, চারিদিকেই দুর্গন্ধ আর তখন শহরের যতো ময়লা সব গঙ্গায় ফেলা হত। গঙ্গার জলে সবসময় ময়লা ভাসতো কিন্তু অভ্যাস ও সংস্কারের মাহাত্ম্যে গঙ্গাস্নানের সময় ময়লা বা তজ্জনিত দুর্গন্ধ সত্ত্বেও মানুষজনের তেমন অসুবিধাই মনে হত না। তাদের বাড়িতে লালদিঘি থেকে পানীয় জল আসতো, বাড়ির পুকুরের সঙ্গে গঙ্গার যোগ ছিলো, পুকুর শুকোলে লহর দিয়ে গঙ্গার জল আনা হত।
বোঝা যায় মধুসূদন গুপ্তর বিবৃতিদানের দুই দশক পরেও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হয়নি, বরং উত্তরোত্তর জনসংখ্যা বৃদ্ধিতে পরিবেশে আরো প্রতিকূলতার সৃষ্টি হয়। বীরেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়-এর বাংলাদেশের সপ্ত প্রসঙ্গে গ্রন্থে এই সময়ের কলকাতা প্রসঙ্গে বলা আছে যে শহরের বেশিরভাগ রাস্তা তৈরি হত খাল ভরাট করে। এমনকি খালগুলি ভরে বসতি নির্মাণও হত। যেমন প্রাচীন কলকাতার একটি খাল ওয়েলিংটন স্কোয়ার, বেন্টিঙ্ক স্ট্রিট ও হেস্টিংস স্ট্রিট দিয়ে এসে গঙ্গায় পড়ত; ওই খালটি ভরাট করেই ‘ক্রিক রো’ সড়কটি নির্মিত হয়।’ আবার উনিশ শতকের কলকাতায় উপযুক্ত পয়ঃপ্রণালীহীন কসাইখানায় ছাগল বলি দিয়ে মাংস বিক্রির মাধ্যমে নিত্য যে দূষণ ছড়াতো ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ তৈরি হত, তার জন্য পৌর কর্তৃপক্ষের আইনি পদক্ষেপ গ্রহণের কথাও জানা যায়। কলকাতায় মিউনিসিপ্যালিটির কমিশনাররা ১৮৮০ থেকে ১৮৮৪ সালের মধ্যে দূষণ নিয়ন্ত্রণ আইনের একাধিক উপধারায় স্বাস্থ্য বিভাগের কর্মকর্তাদের নিযুক্ত করে নিয়মিত পরিদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন।
ফেলে আসা কালের যবনিকা উত্তোলন করলে দেখব- সপ্তদশ শতকে জোব চার্নক কলকাতায় কুঠি প্রতিষ্ঠা করলে তাঁর পূর্বপরিচিত বাঙালি, হিন্দুস্থানি, আর্মেনীয় হিন্দু-মুসলমান-খ্রিস্টান নির্বিশেষে সহযোগী ব্যবসায়ী, দালাল, গোমস্তা, পেয়াদা, দাদন দেওয়ার লোক— সবাই এসে উপস্থিত হয়। কোম্পানির ব্যবসা ফুলে-ফেঁপে উঠল, ফলে মানুষজনের সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ল। অনেকে পাকাপাকিভাবে পরিবার নিয়ে এসে ভিড় করল কাঁচা টাকার লোভে। ফলে দরকার পড়ল জমির। এই সময়ে অনেক পতিত জমিকে স্থায়ী বসতির আওতায় আনার সিদ্ধান্ত গৃহীত হল এবং প্রয়োজনে নিচু জমিকে উঁচু করে ঘর-বাড়ি বানানো শুরু হয়। শহর তো গড়ে উঠল কিন্তু নিকাশি ব্যবস্থা ঠিকঠাক হল না। জমা জল বেরিয়ে যাওয়ার রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছিল, জলে বিবিধ প্রকারের জঞ্জাল পচত। অসুখের কবলে পড়ে নবগঠিত শহর। ১৭০৪ সালে আদেশ এল, আবর্জনাতে ভরা সব দিঘি আর পুকুর বুজিয়ে দেওয়ার। এরপর নিকাশিব্যবস্থাকে যেভাবে শহর আর বসবাসকারী মানুষের উপযোগী প্রযুক্তিতে বানিয়ে তোলা হল, তা আরেক সচেতনতার ইতিহাস।
পর্ব – ৬
ঔপনিবেশিক কলকাতার নিকাশি পরিবেশ
১
The drains were unpaved and coolies had to be continually employed in digging out the black mud and filth.
-নিকাশি নালার এই চেহারার বর্ণনায় ঔপনিবেশিক সমাজেতিহাসের কিছু গুরুত্বপূর্ণ কারবার আছে। ১৬৯০ সালে কলকাতার ভূখণ্ডে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির আগমনের পর কুঠিয়াল জব চার্নক হুগলি নদীর তীরে জলাভূমি বেষ্টিত সুতানুটি নির্বাচন করেছিলেন কোম্পানির কুঠি স্থাপনের জন্য। তখন জায়গিরদার সাবর্ণ রায়চৌধুরী সসম্মানে বর্তমান। ১৬৯৮ সালের ১০ নভেম্বর নাগাদ কোম্পানি তাঁর কাছ থেকে সুতানুটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুর গ্রামের প্রজাস্বত্ব ইজারা নেয়। পরে ১৭১৭ সালে ফারুকশিয়রের ফরমানে গ্রামের জমিদারিসত্ত্ব কেনার অধিকার অর্জন করেছিল। পরবর্তী চল্লিশ বছরের মধ্যে পলাশির যুদ্ধ আর ‘নবাব’ শব্দ জাত ভাবভঙ্গির জনপ্রিয়তা ইংরেজদের পেয়ে বসে। ক্রমে মীরজাফরের দৌলতে চব্বিশ পরগনার জায়গির লাভ, বক্সারের যুদ্ধে জয়লাভ, শাহ আলমের থেকে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার রাজস্ব আদায়ের অধিকার অর্জন নতুন নবাব-শাসক তৈরি করল। এই নতুন নবাব-শাসকদের জন্যই কলকাতা হয়ে উঠছিল অন্তত উনিশ শতক পর্যন্ত। বলা যায় সিপাহী বিদ্রোহের কাল অবধি কলকাতার শৈশব দশা কাটছিল, অনেক কিছুর সঙ্গে তৈরি হচ্ছিল শ্রেণি বৈচিত্র্যও। কার্যত ভারতের পূর্ব সীমান্তে ইস্ট ইন্ডিয়ান কোম্পানির শাখা স্থাপন করে তাকে নিজের শর্তে নিয়ন্ত্রণ করতে পারার প্রতি চার্নকের উচ্চাকাঙখা বর্তমান কলকাতা শহর তৈরিতে ভূমিকা পালন করেছিল। ১৭৫৭ সালে শহরকে নতুন করে সাজানোর কথা ভাবেন হলওয়েল সাহেব। হুগলি নদী বরাবর তিনটি গ্রাম- সুতানুটি, কলিকাতা আর গোবিন্দপুরের একদিকে নদী আর তিনদিকে জলা ও জঙ্গল। কেবল উঁচু ফাঁকা ডাঙা এলাকায় ঘর বসতি ছড়িয়ে ছিল। ইতিমধ্যে কর্ণওয়ালিশের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের (১৭৯৩) মাধ্যমে জঙ্গল কেটে প্রচুর অনাবাদি জমিকে আবাদযোগ্য করে তোলা হয় আর তাকে কেন্দ্র করে স্থায়ী বসতি গড়ে ওঠে। ১৮০৯-১৮৩৬ সালের মধ্যে লর্ড ওয়েলেসলির উদ্যোগে লটারি কমিটির মাধ্যমে রাস্তাঘাট তৈরি হতে থাকে। যদিও সাতের দশকের পর রাস্তা পরিসর ও পরিমাপগত দিক থেকে বাড়ে। এসব অবশ্যই নগর উন্নয়ন প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত, যার স্বার্থে কাজ করেছিল উক্ত কমিটি।
২
কোম্পানির বাণিজ্যের শুরুতে গঙ্গা নদী থেকে গোয়ালন্দের কাছে ব্রহ্মপুত্র ও চাঁদপুরের কাছে মেঘনা নদী দিয়ে পূর্ব ও উত্তর-পূর্ব অঞ্চলের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষিত হত। আবার উত্তর-পশ্চিম থেকে যাত্রী ও পণ্য নদীয়া হয়ে গঙ্গার শাখা ভাগিরথী, জলঙ্গি ও মাথাভাঙ্গা দিয়ে পরিবাহিত হত। শাখা নদী তিনটির মিলন স্থল হুগলি নদী। এটা ঘটনা যে কোম্পানি পলি সরানোর ব্যবস্থা করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন চালিয়ে জলপরিবহণ ব্যবস্থাকে সুগম করে তুলেছিল। গোটা শহরে খনন করেছিল প্রচুর খাল, পানীয় ও নিকাশি ব্যবস্থা দুয়ের জন্যই। হুগলি নদীর পূর্ব তীরে অবস্থিত কলকাতার প্রাকৃতিক ঢাল ছিল লবণহ্রদ অভিমুখী। অথচ তার নালাগুলোর গতিপথ ছিল গঙ্গার দিকে। আবার কলকাতার চেয়ে উঁচু ভূ-পৃষ্ঠে রয়েছে গঙ্গা। ফলে বৃষ্টি বা জোয়ারের সময়ে ওই নালাপথে জল ঢুকে পড়লে নগর কলকাতা বাটির মতো জলে ডুবে যেত। মশা, মাছি, মহামারীর প্রকোপ এই কারণে শুরু থেকেই ছিল। ১৮০৩ সালে পঞ্চম গভর্নর জেনারেল লর্ড ওয়েলেসলির চোখে বিষয়টি ধরা পড়লে তাঁর প্রস্তাব অনুযায়ী একটি উন্নয়ন কমিটি গঠিত হয় (১৮০৪)। সেখানে প্রস্তাবিত হয়- বর্ষার সময় গঙ্গার জলস্তর ও নর্দমাগুলির জলস্তর পার্থক্য নির্ণয় করা অবশ্য কর্তব্য। সেই সঙ্গে ঠিক হয় কলিকাতার বিভিন্ন অঞ্চলের ভূপৃষ্ঠের উচ্চতার পরিমাপ করে সেই অনুযায়ী নিকাশি নালা নির্মাণ করতে হবে এবং কলিকাতা ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলের আবর্জনা নিকাশে উপযুক্ত নিকাশি ব্যবস্থার পরিকল্পনা গ্রহণ করতে হবে। এই সময়ে লটারি কমিটি ব্যয়ভার বহন করে প্রকল্পটিকে বাস্তব অভিমুখী করে তোলে। এমনকি বেলেঘাটা খাল খনন, এলিয়ট পুষ্করিণী খননও সম্পন্ন হয় কমিটির অভিভাবকত্বে।
১৮২০ সালে চাঁদপাল ঘাটে বিশুদ্ধ জল সরবরাহের জন্য একটি পাম্পিং স্টেশন গড়ে তোলা হয়। কিন্তু সেখান থেকে জলসরবরাহ চলত বাছা কিছু এলাকায় (ধর্মতলা, পার্কস্ট্রীট, চৌরঙ্গী, লালবাজার, বউবাজার)। আগের কিস্তিতে রানাল্ড মার্টিনের নাম করা গেছিল, প্রথম তিনিই কলকাতার টোপোগ্রাফি তৈরি করেন। এর গুরুত্ব এইখানে যে নেটিভরা নগর কলকাতার যে অংশে বাস করত, সেখানকার ভূ-প্রকৃতি, আবহাওয়া, স্বাস্থ্য, স্যানিটেশন নিয়ে পরিবেশ আর সমাজের আন্ত:সম্পর্কীয় পাঠ নির্ণয় করা গেল। পরে তা ‘ফিভার হাসপাতাল’-এর কার্যক্রমে বিশেষ সহায়ক যেমন হয়েছিল, তেমনি তাঁর ‘Notes on Medical Topography of Calcutta’ গ্রন্থে শহর কলকাতার নিকাশী ব্যবস্থা সম্পর্কেও সচেতন সমীক্ষার পরিচয় মেলে। ফিবার কমিটিতে পুরসভার তরফে নিকাশী নালা সম্পর্কে বেহাল পুতিগন্ধময় অবস্থার কথা জানানো হয়েছিল। নালাগুলির ‘আউটলেটে’র ব্যবস্থাও ছিলনা। নালা ভরে গেলে উপচে পড়ে রাস্তাঘাটের দুর্দশার অন্ত থাকত না। সমস্যা মেটাতে শহরের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত উত্তর ও দক্ষিণে প্রবাহিত একটি খাল এবং তার পাশে প্রধান নর্দমার এমন নকশার আশু প্রয়োজন ছিল, যাতে পরিস্থিতি অনুযায়ী হুগলি বা সল্টলেক- উভয় দিকেই প্রবাহিত হতে পারে। এই প্রেক্ষিতে স্যানিটারি ইঞ্জিনিয়ার উইলিয়াম ক্লার্ক ১৮৫৫ সালে যুগান্তর আনলেন। আগে লেনিন সরণি (অ্যাভিনিউ) নর্দমার মতো ইট নির্মিত নর্দমা ছিল। তিনি পাঁচটি ভূগর্ভস্থ পয়:প্রণালীর মাধ্যমে শহরের বর্জ্য লবণ হ্রদে নিয়ে যাওয়ার প্ল্যান কষলেন এবং কার্যত এক নতুন নিকাশী ব্যবস্থার দিক উন্মোচন করেন। সেই মতো ড্রেনেজ কমিটি গঠন করা হয় (১৮৫৬) ও পরিকল্পনাটি অনুমোদিত হয়ে ১৮৫৯ সালের ২০ শে এপ্রিল থেকে কাজ শুরু হয়। শোভাবাজার স্ট্রিট থেকে ধর্মতলা (মৌলালি) মোড় পর্যন্ত আপার সার্কুলার রোড (বর্তমানে এপিসি রায় রোড) বরাবর দুটি প্রধান নর্দমা নির্মাণ করা হয়, যেখানে এটি লোয়ার সার্কুলার রোড (বর্তমানে AJC) বরাবর আরেকটির সাথে যুক্ত হয়। টালির নালা মৌলালি মোড় পর্যন্ত আসছিল। সঙ্গে একটি প্রধান আউটফল নর্দমা ছিল এই সম্মিলিত প্রবাহকে পামার’স ব্রিজ পাম্পিং স্টেশনে (PBPS) পৌঁছে দেওয়ার জন্য। দীর্ঘকাল উপযুক্ত বিজ্ঞানসম্মত পয়:প্রণালীর অভাবে নেটিভরা কলেরা, আন্ত্রিকের মতো রোগে ভুগত। ঊনবিংশ শতাব্দীর ছয় থেকে আটের দশকের মধ্যে কলকাতার হাতে গোনা বাড়িতে বিশুদ্ধ পানীয় জল আনার ব্যবস্থা এবং এলাকার কঠিন বর্জ্য চক্ররেলের মাধ্যমে শহরের বাইরে নিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। কোম্পানির বণিকদের অধিকাংশই স্বার্থের বাইরে বেরিয়ে কলকাতার ভূপ্রকৃতি, জলবায়ুর ভঙ্গি বুঝতে চায়নি প্রথমদিকে।

৩
অষ্টাদশ শতকের শুরুতে (১৭০৭, ঔরঙ্গজেবের মৃত্যুর পরে) কলকাতার জমি জরিপের যে হিসেব মেলে, তাতে দেখা যায়-
বাজার কলকাতায় জলাজমি ৩ বিঘা ১২ কাঠা আর ঘরবাড়ি ৪০২ বিঘা মত।
গোবিন্দপুরে পুকুর, জলাজমি ৯ কাঠা আর ১৮ বিঘার মত। সেখানে ঘরবাড়ি ৫৭ বিঘায়। সুতানুটিতে পুকুর আর পথ ৭২ বিঘা, ঘরবাড়ি ১৩৪ বিঘায়। লটারি কমিটির উন্নয়ন প্রকল্পে স্বল্প স্থানে বাড়ি তৈরি করা হয়ে থাকে, জনসংখ্যা বাড়তে থাকলে আরো ছোট হয়ে আসে বসত বাড়ি এবং শহরের, ‘স্পেসে’র ব্যবহার বেড়ে যেতে থাকে। পরিস্ফুট হয় যান্ত্রিক মনোভাব, ল্যুইস মামফোর্ড যাকে ‘বারোক শহর ও মন’ বলে চিহ্নিত করেন। A griffin: sketches of calcutta (১৮৪৩) বইটি চৌরঙ্গির প্রাসাদ ব্যতিরেকে চুনকাম করা ঘিঞ্জি ঘনসন্নিবিষ্ট বসতির সন্ধান দেয়- “In other parts of native town the houses are covered with tiles, these houses if possible closer to one another than the flat roofed ones and have not a pleasing appearance.” উনিশ শতকের মধ্যে কলকাতায় অস্বাস্থ্যকর বস্তিও এসে যায়।
শ্রীপান্থের বর্ণনা অনুযায়ী এখন যার নাম ফ্যান্সি লেন, তা আগে বনাঞ্চল ছিল। আর তার পাশ দিয়ে যে ছোট নদী প্রবাহিত হতো, তা বুজে কিরণশঙ্কর রায় রোডে পরিণতি লাভ করেছে। কলকাতার সঙ্গে বড় রাস্তার সংযোগ ঘটে যে সার্কুলার রোডের মাধ্যমে, তা ১৭৪২ সালে খোঁড়া মারহাট্টা বা বাগবাজার খাল বুজিয়ে নির্মিত। বিনয় ঘোষ তাঁর কলকাতাকেন্দ্রিক সামাজিক গবেষণার ভিত্তিতে আমাদের জানান আঠারো শতকের চারের দশকে কলকাতায় ঘোড়ার প্রচলন হচ্ছে, তার আগে অবধি পরিবহন ও চলাচলের উপায় ছিল পাল্কিই। ১৭৯৯ সালে ওই সার্কুলার রোডের ব্যবহার শুরু হয় অর্থে ঘোড়া চলতে পারার মতো রাস্তা তৈরি হয়ে যায় তখন৷ এরপর একে একে ঘোড়ায় টানা ট্রাম আর ইলেকট্রিক ট্রাম আসে যথাক্রমে ১৮৭৩ এবং ১৯০২ সালে। তারই মাঝে ১৮৫৮ সাল নাগাদ কলকাতার রাস্তার সঙ্গে প্রথম সংযুক্তি ঘটে ফুটপাথের। স্পষ্টতই কাঁচা, কর্দমাক্ত পথ আর থাকল না; মাটির জমিই আর থাকল না তেমন করে কৃষিজমিটুকু ছাড়া। এর মাশুল গুনতে হল নগরবাসীকে। প্রাকৃতিক জলচক্রে যে জল মাটি চুঁইয়ে নেমে ভূগর্ভস্থ জলস্তরের ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করে তুলত, সেই স্বাভাবিক প্রক্রিয়াই বন্ধ হয়ে গেল। আজ বিশ্ব উষ্ণায়নের যুগে আমাদের মেট্রোপলিটন শহরে গরমে ত্রাহি ত্রাহি অবস্থা হয়, সে এই কান্ডজ্ঞানের অভাবে। ক্লান্ত শ্রান্ত পথিক ভিজে মাটিতে খানিক জিরোতে অবধি পায়না, যদিবা খানিক বৃষ্টি হয়, পিচের রাস্তায় কয়েক ফোঁটা পড়তে না পড়তেই তা মিলিয়ে যায়। আর মাটি, গাছ, জলের সুস্থ সম্পর্কজালটিই না থাকায় বৃষ্টি আমন্ত্রণ পায় কই!
পর্ব – ৭
জল-চক্র : পর্ব এক
জলই যে জীবন, তোতা-ইতিহাসের মত এ শিক্ষা কোন ছোটবেলা থেকে আমাদের মগজে ঢুকিয়ে দিয়েছে ইস্কুল। কিন্তু পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা ত নয় সে শিক্ষা, ফলে মাথা ধরে নাড়িয়ে দিলেও চৈতন্য হয়না। বাষ্পীভবন, ঘনীভবন ও অধঃক্ষেপণের মাধ্যমে ভূপৃষ্ঠ আর ঊর্ধ্বাকাশের মধ্যে আবর্তিত জলচক্রের ভৌগোলিক আর বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা না হয় ছবি দিয়ে আঁকা থাকল বইয়ের পাতায়। তার গুরুত্ব জানার সঙ্গে সুস্থ নাগরিকের দায়দায়িত্বের সম্পর্কটা যে কোথায় তা বুঝতে মাথা চুলকোতে হয় বৈকি! ভারতীয় সংবিধানের একাদশতম তালিকায় ‘ফান্ডামেন্টাল ডিউটিজ’ এর এগারোটির মধ্যে অন্যতম হল বন, হ্রদ, নদী সহ প্রাকৃতিক পরিবেশ রক্ষা করা, তার স্বাস্থ্য বজায় রাখা এবং জীবিত প্রাণীর প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করা। অধিক কথনে বাচালের মাত্রাছাড়া হওয়ার আশঙ্কায় কেবল ‘জলজীবন’কেই আলোচনার কেন্দ্রবিন্দু করা হল। তাই হাঁটি পা পা করে প্রথমে বুঝতে হবে জলকে ঘিরে যে জীবনচক্র চরকি পাক খাচ্ছে, তার কথা। একবিংশ শতাব্দীতে এসে আজ আমরা স্মৃতিচারণ করছি আমাদের ফেলে আসা জলজীবনের, তার মূল্যবোধের, বুঝতে পারছি গত কয়েক বছরে আমাদের জলচর্যার বদল ঘটেছে বিপুল। বুঝতে হবে গ্রাম ও শহরের জলজীবনকে, আসুন কান্ডজ্ঞানে ফিরি। প্রথমেই বলার যে শক্তি ও ধৈর্য্য স্বরূপিণী ধরিত্রীদেবীর চারটি প্রধান মন্ডলের (Sphere) বিন্যাস লক্ষ্য করার মত। ‘লিথোস্ফিয়ার’, ‘হাইড্রোস্ফিয়ার’, ‘বায়োস্ফিয়ার’ ও ‘এটমোস্ফিয়ার’ পর্যায়ক্রমে অবস্থান করে মাটির ওপর জল, জলের ওপর জীবমন্ডল এবং তার ঊর্ধ্বে বায়ুমন্ডলের সুষম বন্টন ঘটায়। জল ছাড়া গোটা প্রাণমন্ডলেরই (বায়োস্ফিয়ার) অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। ‘ভূ-পৃষ্ঠের তিনভাগ জল’ অর্থাৎ পঁচাত্তর শতাংশ জলভাগ। শিল্পের ও কৃষিকাজের প্রয়োজনীয় জল, পরিশ্রুত পানীয় জলের উৎস সমুদ্র, ছোট- বড় জলাশয়, হ্রদ, খাল-বিল, নদী-নালা। কিন্তু এই যে জল খরচ হচ্ছে, তবু তার সাম্রাজ্য শেষ হচ্ছেনা তার কারণ বারিচক্র (water cycle)। সূর্যের তাপে ভূ-পৃষ্ঠের জল (এমনকি প্রাণী শরীর থেকে নির্গত বর্জ্য জল) বাষ্পীভূত হয় এবং মেঘ থেকে বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পৃথিবীতে ফেরত আসে। কোথাও কোথাও তুষারপাত বা শিলাবৃষ্টির মধ্যে দিয়ে জল ফিরে আসে পৃথিবীর বুকে, ভরিয়ে তোলে আমাদের ব্যবহার উপযোগী জলের উৎস গুলিকে। প্রাকৃতিক নিয়মে ঐ জলের অণু ভেঙে (H₂O) অক্সিজেন আর হাইড্রোজেন পরমাণু অক্সিজেন চক্র ও হাইড্রোজেন চক্রে প্রবেশ করে অর্থাৎ অন্য কাজে যোগ দেয়। গাছ তার সালোকসংশ্লেষে জল বা জলীয় বাষ্পকে কাজে লাগিয়ে তার হাইড্রোজন থেকে গ্লুকোজ (C₆H₁₂O₆) তৈরি করে। অন্যদিকে জলের দুটি অণুর দুই পরমাণু অক্সিজেন মিলে একটি অক্সিজেন অণু (O2) গঠন করে, যা আমাদের শ্বাস-প্রশ্বাসে সাহায্য করে। পরবর্তীতে ঐ পরমাণুগুলিই আবার সমযোজী বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে জল তৈরি করে।
২
আধুনিকতা’র গোলকধাঁধায় আসার বহু আগে থেকেই খাল, বিল, নদীসহ অন্যান্য জলাশয় নির্মাণের মধ্যে দিয়ে সমাজ আর তার সদস্যদের যুগলবন্দী পথ চলা ছিল। বসত গড়ার জন্য প্রাথমিক শর্তই ছিল বসতিস্থলের সুরক্ষা, গাছের ছায়া আর জলের সুলভতা, তা সে দীঘি-পুকুরের হোক বা কুয়োর হোক। দেশের বিভিন্ন প্রান্তে যখনই মানুষ একের অধিক হয়ে সঙ্ঘবদ্ধ ভাবে বাস করতে গেছে, প্রয়োজন অনুযায়ী গড়ে নিয়েছে তালাব (পুকুর), বেরি (ছোট কুয়ো), চৌকরি প্রভৃতি। পানীয় জলের জন্য, সেচের জলের জন্য, নিত্য ব্যবহারের জন্য তখন এলাকার জনসংখ্যা অনুযায়ী পুকুর কাটার রেওয়াজ ছিল। পুকুর কখনও প্রাকৃতিক কারণে তৈরি হত কখনও বা মানুষ তৈরি করত। এতে সাধারণ মানুষের লোকালয়ের দৈনন্দ্যিন কাজ মিটত। তবে পুকুরের বদ্ধ জল খানিকটা মজে যাওয়া ধরনের হয়ে যেত রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে। অভিধানে পাচ্ছি ‘পনড’ (pond) বা ডোবা বলতে ‘a pool of stagnant water’। আবার দিঘি সাধারণত শাসকবর্গ দ্বারা খনিত হত সমাজের জন্য। তখন দীঘি-পুকুর কাটা ‘পুণ্য’ কাজের সঙ্গে জড়িত ছিল, রাজা-রানী-গৃহস্থ ‘মহাত্মা’র শিরোপা পেতেন লোকালয়ে এসব নির্মাণের জন্য। প্রতি গ্রামে নানা উপলক্ষ্যে ছোটো বড়ো প্রচুর দিঘি পুকুর কাটা হত। সরোবর অনেক বড় জলাশয়, একে সুদৃশ্য ভাবে বাঁধানো হত। আর বাংলায় হ্রদ বলতে আমরা সমুদ্র লগ্ন জলাশয় বুঝি। পাহাড় থেকে নিঃসৃত বৃহৎ প্রাকৃতিক জলাধার কেও ‘লেক’ বা হ্রদ বলি। অভিধান অনুযায়ী- a large body of water entirely surronded by land। তা সে জলের বহুধারার মত পুকুর, নাছপুকুর, সরোবর, দিঘি, তাল, বাঁধ, ডোবা, ঝিল, বিল, হ্রদ, গইড়া- প্রভৃতি বিভিন্ন রকম বা ফর্ম হলেও জলাশয় তো জলাশয়ই। ব্যবহারের ধরন অনুযায়ী পৃথক করা থাকত সেসব জলাশয়, যেমন গ্রামের মন্দিরটার জন্য আলাদা পুকুর (সংরক্ষিত পুকুর), বর্ধিষ্ণু পরিবারগুলোর খিড়কি দরজার কাছে রাখা হত নাছপুকুর আর তুলনায় সামান্য অবস্থার গৃহস্থের মেয়েদের আব্রু ছিল বাঁশঝাড় লাগোয়া ‘গড়্যা’ বা ডোবা। এখন ভূ-প্রকৃতি ও আবহাওয়ার বৈচিত্র্যে বিভিন্ন স্থানে জলপ্রবাহ ও জল ধরার কৌশল ভিন্ন ভিন্ন, ফলে জলজীবনের ধারাও পৃথক হয়ে যায়। যেমন ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চলে জলের অভাব সবচেয়ে বেশি। রাজস্থানের আরাবল্লি পার্বত্য অঞ্চলের গাছগাছালির জন্য বাতাসে যতটুকু ভাসমান জলীয় কণার পরিমাণ বাড়ে তার ফলস্বরূপ অল্প বৃষ্টিপাতেই আলোয়ার দিয়ে রূপারেল নদী প্রবাহিত হত। কিন্তু ক্রমে গাছশূন্য হওয়ায় বৃষ্টিপাতের পরিমাণ উল্লেখযোগ্য ভাবে কমে যায়, মাটির লেয়ার পাতলা হতে থাকে এবং কৃষিকাজ প্রায় বিলুপ্ত হয়। এলাকাবাসী জোহড় নির্মাণ করে এই সমস্যার সমাধান করল। যে অঞ্চল দিয়ে ঐ যৎসামান্য বৃষ্টির জল প্রবাহিত হয়ে যায় (আগোর), সেখানে পাথরের খন্ড সাজিয়ে সীমানা গেঁথে দেওয়া হল। তাতে যেমন পানীয় জল মিলল, তেমনি সেচের কাজে প্রয়োজন মত ব্যবহারও করা গেল। আর এক জায়গায় জল জমা থাকার ফলে সছিদ্র মাটি দিয়ে ভূমিগর্ভে জল সহজেই প্রবেশ করতে পারে, বাড়ে ভৌমজলস্তর। লোকালয়ের বহু পাতকুয়ো যেমন তাতে ভরে উঠল তেমন বহু শুকনো নদীও টলটলে জলে ভরে গেল। এছাড়াও আশেপাশের নরম ভিজে উর্বর মাটিতে সবুজ ঘাস আর গাছ জন্মাল। কোথাও কোথাও সামাজিকভাবে কুন্ড তৈরি করে নয়তো বাড়ির ছাদে টাঁকা তৈরি করে বৃষ্টির জল বা ‘পালরপানি’ ভরে রাখার ব্যবস্থা করা হয়। ইঁট- ফৌগ কাঠ-বালি-খড়িয়া পাথর প্রভৃতি যখন যেখানে যা মেলে তাই দিয়ে সর্বজনীন কুন্ডি, তার ঢাকনা তৈরি হয়। সঙ্গে থাকে জল ওঠানোর জন্য প্রয়োজনীয় কপিকল। বাড়ির মেয়েরা ঘরে চৌকাবর্তন তৈরি করে জল সংরক্ষণ করে। ছোটনাগপুর মালভূমি অঞ্চলের পূর্ব ঢালে অবস্থিত পুরুলিয়াতেও জল সংরক্ষণের চেষ্টা চালাতে হয়। ল্যাটেরাইটযুক্ত অনুর্বর মৃত্তিকা, ভূমি সিঁড়ির ধাপের মতো উঁচু নীচু অসমতল হওয়ায় বৃষ্টির জল জমবার এখানে সুযোগই পায় না। আবার ভূস্তর কঠিন শিলাযুক্ত হওয়ায় জল মাটির নীচে বেশি দূর চুঁইয়ে চুঁইয়ে ঢুকতেও পারে না। ফলে বৃষ্টিতে গড়িয়ে যাওয়া জলের পথে শুধুমাত্র একদিকে একটি পাড় বেঁধে দিয়ে পুকুর নির্মাণ করেই জল সংরক্ষণ করা যায়। বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, বীরভূমের কাঁকুড়ে মাটি বেয়ে পরিষ্কার জল নীচে গড়িয়ে যেতে পারার পথ বন্ধ করে মাটি বেঁধে ‘বাঁধ’ (এই জলাশয়ের তিনদিক খোলা), জলাশয় বানিয়ে নেওয়া হয়। এই যে বাঁধ, কুন্ড, পুকুর, দিঘি, কুয়ো খোঁড়ার সবচেয়ে জরুরি তত্ত্ব-গ্রামের সাধারণ মানুষদের সেসব জানা ছিল।
পর্ব – ৮
জল-চক্র : পর্ব দুই
জলের জীবন, জলের পেশা
উত্তরাধুনিক শহুরে আমরা পরিবেশ বাঁচানোর সেমিনারে, কর্মসূচিতে আহ্বান করে আনি নদী বিজ্ঞানীকে, গবেষককে, ইঞ্জিনিয়ারকে। অথচ যারা খুব স্বাভাবিকভাবেই জানতেন এসব, জীবনযাত্রার জন্যই জানতে হয়েছিল যাদের, তাদের ঘিরে বসে শুনি ক’জন? গেঁয়ো যোগীর ভিখ মেলে না যে! গ্রামের সাধারণ মানুষরা জানত ভূমির ঠিক কোনখান দিয়ে বৃষ্টির জল সবচেয়ে বেশি পরিমাণে গড়িয়ে আসে বা চারপাশের শুষ্কতার মধ্যেও কোন জায়গার মাটি খুঁড়লে জলস্তর মিলবে ইত্যাদি। এই কুয়ো, পুকুর কাটার স্থান নির্বাচন করতে পারা বিশেষ জ্ঞানের সাথে সম্পর্কিত ছিল। এঁরা ‘গজধর’ নামে পরিচিত ছিলেন অর্থাৎ ‘গজ’ ধারণ করেন বা মাপতে পারেন যিনি। প্রায় স্থাপত্যশিল্পীর মর্যাদা পেতেন কেননা সহজে বলতে পারতেন মাঠের কোন দিকে কতটা ঢাল, এর জন্য তাদের পুঁথিগত জ্ঞানের মুখাপেক্ষী হতে হয়নি, দীর্ঘদিনের অভিজ্ঞতায় অর্জন করেছেন জলের বিজ্ঞান। জলাশয় তৈরির সময় মাটি কাটাই প্রধান, জল গড়িয়ে আসার পথটি সযত্নে খেয়াল করে সেই গড়িয়ে আসা জল যেখানে সবচেয়ে বেশি জমে সেটাকেই কাটার সঠিক জায়গা হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। তারপর কাটা মাটি তুলে তৈরি হয় জলাশয়ের পাড়। যেখানে যেমন মাটির স্বভাব, যতখানি বৃষ্টিপাত, প্রত্যেক জায়গায় সেইমত খনিত হয় জলাশয়। কোথাও পাড় হয় এমন যেন চারপাশ থেকে গড়িয়ে আসা জল সহজে গড়িয়ে পুকুরে নামে। কোথাও মাত্র এক বা দুদিক থেকেই পরিষ্কার জমির ওপর দিয়ে গড়িয়ে আসা জল পুকুরে এসে ঢুকবে, আবার কোথাও পাড়ের কাজ বাইরের গড়িয়ে আসা জল থেকে পুকুরকে রক্ষা করা। যেমন গাঙ্গেয় উপত্যকার যে অঞ্চলে চিটামাটির প্রাধান্য, সেখানে পুকুর কাটার সময়ে খোঁড়া মাটি দিয়ে পাড় উঁচু করে দেওয়া হয় যাতে বর্ষার সময় বাইরের ময়লা জল গড়িয়ে আসতে না পারে। গজধর কাজের সময় তাঁর জোড়িয়া বা সহকারীকে সঙ্গে নিতেন। কুয়ো কাটা বা পুকুর তৈরির পর সমবেত ভোজের ব্যবস্থা থাকত, সেখানে গোটা গ্রামের জলের ব্যবস্থা করে দেওয়ার জন্য গজধরদের সম্মান ছিল দেখার মত। এই অনুষ্ঠান বোঝায় জলজীবন ‘আমাদের’ ছিল, তাকে নিয়ে তৈরি হওয়া সমস্যা আর সমাধানও ‘আমি’র পরিবর্তে আমাদেরই। বর্তমানে এই সাধারণ বোধ বিশেষে পরিণত হয়েছে, ‘আমি’ ভাবনা এতই পেয়ে বসেছে যে বুঝছিনা যৌথতা ছাড়া একটা গোটা জলজীবনের যাপন হওয়া সম্ভবই না, কাজেই দায়ভার বলো সচেতনতা বলো প্রত্যেককে ভাগ বাটোয়ারা করে নিতে হবে। আজ জল সংরক্ষণের জন্য বহু বিদেশি অভিজ্ঞ কোম্পানিকে টাকার বিনিময়ে ডেকে এনে যন্ত্রপাতি দিয়ে জলসমস্যার সমাধান করাতে হচ্ছে। টিউবঅয়েল কোম্পানিকে অনেক কষ্ট করে যন্ত্র দিয়ে জায়গা বেছে নিতে জানতে হয়, কিন্তু এসব জানাজানি খুব সহজ ছিল সাধারণ মানুষের কাছে, তাদের পরের ওপর নির্ভর করতে হয়নি। রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ, গুজরাটে গজধর, ওড় (ঔড়, ওঢিয়া, ওঢহি) দের সংস্কৃতি এখনও পাওয়া যায়৷ মধ্যপ্রদেশে গজধরেরাই ‘পথরোটা’ নামে পরিচিত। মাটির প্রকৃতি থেকে শুরু করে তার আচরণ, ভবিষ্যৎ- সবটা বুঝতেন ‘মটকুটা’রা। জল আর মাটি পরস্পর অছেদ্য সম্পর্কে আবদ্ধ, তবে না ‘জীবন’! জায়গামতো মাটি খুঁড়লেই জীবনের প্রস্রবণ বেরিয়ে আসে। মাটি তার গর্ভে জল ধারণ করেই উর্বর, ঠিক যেমন করে একজন নারীর গর্ভে তার প্রাণের ভ্রূণটির চারপাশে জলের স্তর রচিত হয়। এই মাটিকে স্বর্ণ বিবেচনা করে যারা মাটি খুঁড়ে সগর রাজার পুত্রদের মত জল আনত তারা ‘সোনকর’।
আবার পাথরের সমস্ত ধরনের কাজ ভালোমত জানতেন যারা, দক্ষিণ ভারতে তারা ‘কৌরি’ নামে পরিচিত। দশে মিলে জলজীবনকে টিকিয়ে রাখার এই প্রচেষ্টায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল ‘বুলাই’দের, তাদের কাছে জমি সহ গ্রামের সম্পূর্ণ তথ্য থাকত। ব্যক্তিগত ও সামাজিক জলাশয় নির্মাণের ক্ষেত্রে জমির মালিকানা বিষয়ে অর্থনৈতিক বর্গের দ্বন্দ্ব প্রবলভাবে রয়েছে বলেই জমি সংক্রান্ত তথ্যের গুরুত্ব অপরিসীম। স্পষ্টতই সভ্যতা বিকাশের প্রাথমিক সম্পদ ‘জল’কে ঘিরে স্বতন্ত্র পেশা গড়ে উঠেছিল।
আমাদের প্রধান উৎপাদন ব্যবস্থা ‘কৃষি সংস্কৃতি’ এমন পরিসর প্রস্তুত রাখত যাতে কৃষিকাজ, গোচারণ ইত্যাদির জন্য মাটি আলগা হয়ে গেলে জল বেশি মাত্রায় অনুস্রাবণের মাধ্যমে ভূ-অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারে। তার সাথে বরাবর হাত ধরাধরি করে থেকেছে ‘জল সংস্কৃতি’। এই জলসংস্কৃতিকে ঘিরে থেকেছে হাজারো সংস্কার, তিথি-পুজো-শ্মশানযাত্রা এমনকি অশৌচমুক্তি ইত্যাদি আচার জলে ডুব দিয়ে সম্পন্ন হয়। আমাদের কাছে দুই নদীর মিলনস্থল যজ্ঞের প্রকৃষ্টতম পুণ্যস্থান রূপে বিবেচিত হয়ে এসেছে, তীর্থযাত্রা মানেই ত ‘নদীর ঘাট’। খাল বিল সায়র পুকুরে ভরভরন্ত বাংলার জলজীবনময় সংস্কৃতির কিছুটা বোঝা যায় পূর্ণিপুকুর ব্রততে। বৈশাখে পুকুরের জল যাতে না শুকোয়, তার জন্য করা হত-
-পূর্ণিপুকুর পুষ্পমালা
কে পূজে রে দুপুরবেলা?
আমি সতী লীলাবতী
ভাইয়ের বোন পুত্রবতী,
হয়ে পুত্র মরবেনা
পৃথিবীতে ধরবেনা।
প্রতীকী পুকুর কেটে তার মধ্যে বেলের ডাল পুঁতে, জল ঢেলে পূর্ণ করে তারপর বেলের ডালে ফুলের মালা ও পুকুরের চারধারে ফুল সাজানো হয়। মনে রাখতে হবে এই ব্রতকথা মানুষের সাধারণ সম্পত্তি, সেখানে বিশেষের বদলে গোষ্ঠীগত আকুতি আছে। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝিতে স্বাধীনতার ঠিক পরপর যখন উঁচু বাঁধ প্রকল্পগুলি সামাজিক উন্নয়নের স্তম্ভ হয়ে উঠল, তখন থেকেই ‘আমরা’ থেকে ‘আমি’তে আসা, একত্রে ক্রিয়াকর্ম গুলো আর অনুষ্ঠিত হয়না। আবাদযোগ্য জমি, চারণভূমি যত বেশি করে প্রোমোটারের কাছে বিক্রি হল, ‘এ-পার্টমেন্টে’র (Apartment) কালচার যত বেশি করে চর্চিত হতে থাকল তত মাটির ওপর আচ্ছাদন রূপে কাজ করল ঘরবাড়ি, পাকা রাস্তা; কমতে লাগল ভৌম জলের স্তর। কিন্তু যে জলজীবন চর্চিত হয়েছে সুদূর প্রাচীনকাল থেকে, তার স্বাস্থ্যের কি ব্যবস্থা ছিল? বিশেষত নদী ছাড়া বাকি তৈরি করা জলাশয়গুলি স্বভাবগতভাবে বদ্ধ প্রকৃতির। যেখান থেকে জল গড়ানে এসে কুন্ড, দিঘি, পুকুরের আগোরে (জলের কোষাগার) জমা হয়, সেই জায়গাগুলিতে জুতো পরে যাওয়ার বা অপরিষ্কার রাখার অনুমতি ছিলনা। জলাশয় জলে ভরে উঠলেই তাতে মহাসমারোহে মাছ, কচ্ছপ, কাঁকড়া এনে রাখার ব্যবস্থা করা হত। এমনকি জল গভীর হলে কুমীরও। দেওয়া হত বিশেষ প্রজাতির উদ্ভিদ, যে অঞ্চলে যেমন পাওয়া যায়। যেমন রাজস্থানে কুমুদিনী, চকসু, মধ্যপ্রদেশে গদিয়া বা চিলা, যাতে জল পরিষ্কার রাখা যায়। বাংলার জলাশয়ে মূলতঃ জন্মায় শালুক, পদ্ম, কচুরিপানা, খাঁড়ি, জলজ ঘাস প্রভৃতি। আর এ তথ্য ত আমাদের সকলের জানা যে বিবিধ রকমের মাছেদের খাদ্য হয় এতে। তবে মাথায় রাখতে হয় জলাশয়ের পরিবেশে উদ্ভিদ আর হাঁস, মাছ প্রভৃতি জলচর প্রাণী সমানুপাতিক হতে হবে। আগাছা বাড়লে তা পচে জলের তলদেশে বিষাক্ত গ্যাসের জন্ম দেয়, জলে অক্সিজেন কমে গুণাগুণ নষ্ট হয়, প্রাণীরা মারা যায় ও বাস্তুতন্ত্র ভেঙে পড়ে। মোট কথা অজৈব পদার্থ, উৎপাদক জীবপুঞ্জ, খাদক প্রাণী ও বিয়োজক নিয়ে পুকুর বা অনুরূপ জলাশয় আত্মনির্ভরশীল বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্র হয়ে ওঠে। কিন্তু এর কার্যকারিতা নির্ভর করে কি পরিমাণে সৌরশক্তি গৃহীত হয় ও কি হারে এর চারপাশ থেকে জল ও অন্যান্য পদার্থ প্রাপ্তি ঘটে, তার ওপর। জলাশয়ের পাড় রক্ষার জন্য আম, নিম, অরহড় গাছ লাগানোর পাশাপাশি খেয়াল রাখা হত যেন ইঁদুর বাসা করে পাড়ের মাটি আলগা না করে দেয়। তাই নতুন তৈরি জলাশয়ের পাড়ে সরষের খোলের ধোঁয়া দেওয়া হত। সেই সম্মিলিত প্রচেষ্টা আজ কোথায়! বরং ন্যাড়া পাড়ের পুকুর, কচুরিপানায় ভরা জলাশয় দেখতেই অভ্যস্ত আমরা। আর আমরা ভুলে গেছি ঐ যে ‘কা তব কান্তা কস্তে পুত্রঃ’ এর পাঠকে ভুলভাবে ব্যাখ্যা করে আত্মকেন্দ্রিক যাপন করছি, ইঁদুরের কামড় ত সেখানেই।
পর্ব – ৯
জল-চক্র : পর্ব তিন
নদী তুমি কোথা হইতে আসিয়াছ’
“এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
ভাদুলি ঠাকুরানি ঘুচাবেন দুখ
এ নদী সে নদী একখানে মুখ,
দিবেন ভাদুলি তিনকুলে সুখ”
নদীমাতৃক এই নিভৃত নীড়ের আশায় ব্রতকথা সংগ্রহ করেছিলেন অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। টলটলে জল ভরা নদী, তার কূল ছাপিয়ে জল আর বাহিত পলি – মাটিকে উর্বর করে সোনার ফসল ফলায়; সাধারণ পল্লীপ্রধান দেশে উপচে পড়ে সুখ। হিমালয়, আরাবল্লী, বিন্ধ্য, সাতপুরা, পশ্চিমঘাট, পূর্বঘাট, নীলগিরি পাহাড়-পর্বতশ্রেণীর প্রাকৃতিক সুরক্ষা কবচ দিয়ে ঘেরা যে দেশে নদী-উপনদী, শাখানদীর শিরা উপশিরা রয়েছে, সে দেশ খাদ্য বিষয়ে পরনির্ভরশীল ছিল এ কথা সাম্প্রতিক কিছু মুষ্টিমেয় বর্গের মধ্যে চর্চিত হতে দেখে মোটেও ভালো বোধ হয়না। আর ভারতে ত শুধুমাত্র জমি না, রীতিমতো আবাদযোগ্য জমি ছিল তার চিরকালীন জলজীবনকে ঘিরে। বুন্দেলখন্ড মালভূমি, পূর্ব ভারতের ছোটনাগপুর ও দন্ডকারণ্য মালভূমি, শিলং, দাক্ষিণাত্য, কর্ণাটক, তেলেঙ্গানা, মালবা মালভূমি এবং উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমির ওপর দিয়েই নদীদের সংসার। উত্তর ভারতের গাঙ্গেয় সমভূমি পূর্বদিকেও বিস্তৃত হয়েছে। রাজ্যের উত্তরে যেমন হিমালয়ের সুউচ্চ শৃঙ্গ, তেমনি দক্ষিণে উপকূলীয় সমভূমি, পশ্চিমে মালভূমি ও পূর্বদিকে গাঙ্গেয় বদ্বীপ, অর্থাৎ মালভূমি এবং সমভূমির সহাবস্থান দেখা যায়৷ পার্বত্য, মালভূমি ও সমভূমি এলাকা ভেদে ভূমির ঢাল বাড়া কমা অনুযায়ী জলপ্রবাহ, তার ধারণক্ষমতা, ক্ষয়ক্ষমতা ইত্যাদি নির্ভর করে, এ আমাদের সকলের জানা। নদীর উচ্চগতিতে প্রধান কাজ ক্ষয়কাজ, মধ্যগতিতে মূলতঃ বহনকাজ এবং নিম্নগতিতে সঞ্চয়। সিন্ধু নদী কৈলাসের সেনগগে খাবাব হিমবাহ থেকে জন্ম নিয়ে পশ্চিমে প্রবাহিত হয়েছে এবং লাদাখ হয়ে দক্ষিণে বেঁকে পাকিস্তানে প্রবেশ করেছে৷ বোঝা যায় এই নদীর পার্বত্য গতি ভারতের ওপর দিয়ে এবং আরব সাগরের কাছে নিম্নগতিতে সঞ্চয় কাজের মাধ্যমে ব-দ্বীপ তৈরি করেছে। বামতীরে আর ডানতীরে বিছিয়েছে ধানসিঁড়ি, ঝিলম, ইরাবতী, শতদ্রু, বিপাশা, চন্দ্রভাগা, কামেং, মানস, তিস্তা, সঙ্কোশের মত নদী। উত্তরাখন্ড রাজ্যে উৎপন্ন হয়ে গঙ্গা, হরিদ্বার পর্যন্ত পার্বত্য অবস্থা এবং বিহারের রাজমহল পর্যন্ত মধ্যগতিতে সমভূমি অবস্থার মধ্যে দিয়ে গেছে। এরপর পাহাড়ের পূর্বদিক দিয়ে দক্ষিণমুখী হয়ে গঙ্গানদী পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ করেছে ও মূর্শিদাবাদের কাছে পদ্মা আর ভাগীরথীতে বিভক্ত হয়ে দ্বিতীয় শাখায় ভাগীরথী-হুগলি বদ্বীপ গঠন করেছে৷ সুদীর্ঘ গতিপথে যমুনা, শোন, গোমতী, ঘর্ঘরা, রামগঙ্গা, গন্ডক, কোশী উপনদীগুলোর নিজের কাহিনী ত আছেই। আবার ব্রক্ষ্মপুত্র চীনের চেমায়ুং দুং থেকে জন্ম নিয়ে আসামের ডিহংয়ে ঘরবাড়ি বানিয়ে বাংলাদেশে পদ্মার সঙ্গে মিশে মেঘনা নামে বঙ্গোপসাগরে মিশেছে৷ এখন ভারতের ঊর্ধাংশ থেকে কিছু নীচে মধ্যভাগের দিকে চোখ সরালে বোঝা যায় মহারাষ্ট্র, কর্ণাটকের বেশিরভাগ ও অন্ধ্রপ্রদেশের কিয়দংশ নিয়ে গঠিত দাক্ষিণাত্য মালভূমির ঢাল অনুযায়ী মহানদী, গোদাবরী, কৃষ্ণা, কাবেরী প্রভৃতি দক্ষিণ ভারতের নদীগুলি পূর্বদিকে প্রবাহিত হয়ে গতিপথ রচনা করেছে। ভারতের পশ্চিম উপকূল চ্যুতি যুক্ত হওয়ায় আরবীয় পাতের চাপ প্রতিরোধ করতে গিয়েও পশ্চিম উপকূল পূর্ব দিকে বেঁকে ঢাল যুক্ত হয়। আবার পূর্ব উপকূল অগভীর ও সমতল অংশ, ফলে পূর্ববাহিনী নদীগুলো মধ্যভাগের মালভূমি থেকে উৎপন্ন হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করে প্রচুর পলি সঞ্চয় করে সমতলে বদ্বীপ গঠনে সক্ষম। উপকূলের বালুকাময় সমভূমি, গঙ্গার বদ্বীপ অঞ্চল ও সুন্দরবন অঞ্চল এর অন্তর্গত। অন্যদিকে পশ্চিমদিকের ভূমি কঠিন শিলাভিত্তিক। পশ্চিমঘাট, বিন্ধ্য, সাতপুরার গুণে এই দিকের ঢালও খাড়া। ফলে নর্মদা, তাপ্তির মত পশ্চিমবাহিনী নদীগুলো দ্রুতগতিতে মোহনায় পড়ে সঞ্চয়কাজের সুযোগ পায়না, এমনকি বহনও করতে পারেনা বেশি কিছু। বোঝা যায় নদীর স্বল্পতা ও ভূ-প্রাকৃতিক কারণে পূর্বদিকের তুলনায় পশ্চিমদিক অনেক বেশি পাথুরে, রুক্ষ ও শুষ্ক। এই এলাকাগুলির কথা মাথায় রেখে পূর্ববাহিনী নদীগুলির কয়েকটির গতিপথ পশ্চিমবাহিনী করার কথা ভাবা হচ্ছে। এখান থেকে শুরু হয় আরেক প্রসঙ্গের- প্রাকৃতিক জলবন্টন প্রণালীকে দম্ভ ভরে পরিবর্তন করার চেষ্টা।
আগে জলব্যবস্থা যে গ্রামগত ভাবে সম্মিলিত প্রচেষ্টার অন্তর্গত ছিল, তাকে কেন্দ্র করে কিছু চর্যা ছিল, সেসব প্রশাসনিক আওতাধীন হওয়ায় বর্তমানে জলব্যবস্থা কয়েকটি সরকারি প্রকল্পের আওতাধীন হয়েছে মাত্র। পূর্বেই জেনেছি গ্রামে কুন্ড বা পুকুর তৈরি করা হলে প্রস্তুতকর্তা তার দায়িত্ব দিতেন গোটা গ্রামকে, পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতার দায়িত্ব থাকত ঐ পুকুর বা কুন্ডের সামনে বাসকারী পরিবারের। কিন্তু স্বাধীনতা পরবর্তী ভারতবর্ষে জল নিয়ে স্বয়ংসম্পূর্ণতার বদলে দেখতে হল জল’কে কিভাবে সমান ভাবে ভাগ করে দেওয়ার সম্পত্তিতে পরিণত করেছি। কাবেরী নদীর খরাপ্রবণ অববাহিকার ৩৬.৯০ শতাংশ এলাকা তামিলনাড়ুতে এবং ৬৩.১০ শতাংশ কর্ণাটক রাজ্যে অবস্থিত। সুতরাং পানীয় জল ও কৃষিতে জলসেচের পর্যাপ্ত জোগানোর জন্য দুটি রাজ্যের মধ্যে জল বন্টন নিয়ে বিবাদ ঘটলো। যে এলাকায় নদী অববাহিকার বেশিটা বর্তমান, সেই এলাকা দাবি করল নদীর অতিরিক্ত কিউসেক জল। কৃষ্ণা নদী মহারাষ্ট্র কর্ণাটক তেলেঙ্গানা অন্ধ্রপ্রদেশের মধ্য দিয়ে প্রবাহিত হওয়ায় কৃষিকাজের জন্য জল সেচ ও পানীয় জলের উৎস জন্য এই চারটি রাজ্যকে অনেকাংশে কৃষ্ণার উপর নির্ভর করতে হয়। ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দে কৃষ্ণা জল বন্টন সংক্রান্ত প্রথম ট্রাইবুনালের চুক্তিতে ৫৬০ বিলিয়ন কিউসেক, কর্নাটকের জন্য ৭০০ মিলিয়ন কিউসেক ও পূর্বতন অন্ধ্রপ্রদেশের জন্য ৪০০ বিলিয়ন কিউসেক জল নির্ধারিত হয়। কিন্তু ২০১৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশ ভেঙে তেলেঙ্গানা রাজ্য তৈরি হলে কৃষ্ণার জল বন্টন নিয়ে নতুন করে বিবাদ তৈরি হয়। একইভাবে গোদাবরীর জল নিয়ে চারটি রাজ্যের মধ্যে বিবাদ শুরু হলে পচামপাড়ু বাঁধ তৈরি করে এই বাঁধের ঊর্ধ্ব অববাহিকা ও নিম্ন অববাহিকার জল কে দুটি অংশে ভাগ করে বিলির ব্যবস্থা করা হয়। ইরাবতী, বিপাশার জল নিয়ে পাঞ্জাব ও হরিয়ানা আর নর্মদার জল নিয়ে গুজরাট, মধ্যপ্রদে, মহারাষ্ট্র, রাজস্থান বিবদমান। সিন্ধু তার উপনদীগুলো নিয়ে যে নিম্নগতিতে পাকিস্তান হয়ে আরব সাগরে পড়েছে, তাতে তার জলবন্টন নিয়ে ভারত ও পাকিস্তানের মধ্যে বোঝাপড়ার অভাব হচ্ছে। ভারত পরিমাণে কম জল পাচ্ছে ভাগে আর এই নদী অববাহিকাটি থর মরুভূমি সংলগ্ন হওয়ায় সেচের একমাত্র উৎস। শুধুমাত্র দলাদলির কারণে সিন্ধুর গতিপথ কৃত্রিমভাবে পরিবর্তন করার কথা ভাবা হচ্ছিল! আবার ভারত ও বাংলাদেশের মধ্যে সর্ববৃহৎ জলবন্টন সংক্রান্ত কমিশন আছে। গঙ্গা নদীর সামান্য অংশ পশ্চিমবঙ্গে অবস্থান করলেও তার মূল শাখা নদী পদ্মা বাংলাদেশের অন্তর্গত এবং বাংলাদেশের কৃষি কাজের অধিকাংশ পদ্মার উপর নির্ভরশীল। নিয়ম অনুযায়ী পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর উপর ফারাক্কা ব্যারেজ নির্মাণের ফলে প্রয়োজনীয় জলসেচের খুব সামান্য অংশই বাংলাদেশ সরকার পায়। আবার তিস্তা নদীর নিম্নগতি বাংলাদেশ, এখানে এই নদী ব্রক্ষ্মপুত্র তথা যমুনার সঙ্গে মিলিত হয়েছে। ফলে সম পরিমাণ জলের দাবি নিয়ে দুই প্রতিবেশী দেশের মধ্যে দড়ি টানাটানি খেলা চলছে, যে জিতবে জল তার। যে জল আমাদের প্রাকৃতিক ধন-সম্বল, তা কি করে যেন একদিন এরকমভাবে ভাগযোগ্য সম্পত্তিতে পরিণত হয়ে টুকরো হয়ে গেল! এই যে গঙ্গা-সিন্ধু-ব্রক্ষ্মপুত্রের লীলাভূমি, এখানেই গত কয়েক বছরে মজে গেছে একের পর এক অসংখ্য নদী। অবৈজ্ঞানিক কার্যকলাপে, অত্যাধুনিকতার দম্ভে পালটে দিতে চেয়েছি নদীর প্রাকৃতিক গতিপথকে। ইতিমধ্যে প্রায় সবাই জানেন, জলপাইগুড়ি জেলায় ডুয়ার্সের অন্যতম বড় নদী মাল-এর গতিধারার মাঝখানে মাটি পাথর ইত্যাদি দিয়ে আড়াআড়ি বাধা নির্মাণ করে পাশে খুঁড়ে দেওয়া নতুন ধারাতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের ব্যবস্থা হয়েছিল। তা সেই বিসর্জনের বেশ কিছু আগে থেকেই বৃষ্টিপাত হচ্ছিল, হঠাৎ নদী বেয়ে ঝড়ের গতিতে বিপুল জল নেমে আসলে কয়েক মিনিটের মধ্যে কোনও প্রস্তুতি নেওয়ার আগেই প্রচণ্ড ধারার মুখে সব ভাসান আয়োজন ভেসে যায়। নদীর যাতায়াতের পুরোনো জায়গা নদী কখনও ভোলে না, সে ইচ্ছেমত সেই খাত দিয়ে একদিন বয়ে যেতে পারে, নদীরও হাত পা ছড়ানোর ইচ্ছে হতে পারে তার তীর বরাবর। সেসব ভাবনাকে তুড়ি দিয়ে বা ‘কব্জা করতে পারব’ ভেবে উড়িয়ে দেওয়া গেছে। ‘হড়পা বান’ ডুয়ার্সের নদীগুলির স্বভাব। মধ্য বা নিম্ন হিমালয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাতের জল এরা তীব্রধারায় নীচে অপেক্ষাকৃত সমতলে পৌঁছে দেয়। ঢাল কমে আসার দরুন সমতলে জলস্রোতের তীব্রতা হ্রাস পায়, তা অনেকটা জায়গা ধরে ছড়িয়ে স্বাভাবিক বন্যার কারণ হয়। সমতলে নেমে আসা এই জল গচ্ছিত থেকে হিমালয়জাত নদীদের প্রবাহকে অক্ষুণ্ণ রাখে। কিন্তু প্রকৃতির সূক্ষ্ম শৃঙ্খলাকে বোঝার চেষ্টামাত্র না করে প্রযুক্তিদম্ভ দেখিয়ে ফেলেছি প্রবল ভাবে। এর মর্মান্তিক ফলশ্রুতি কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভাবতেও গা শিউরে ওঠে। আর যাই হোক মানুষের নৃতত্ত্বগত বিচারে যে হাত তার প্রধান প্রযুক্তিবল, তা দিয়ে জলকে কোনোদিন ধরা যায়নি আর যাবেওনা, তাকে ক্রমাগত বইতে দিতে হয়।
১৯৭১ সালে বিশ্বব্যাপী জৈবপরিবেশ রক্ষার সম্মিলিত প্রয়াসের ফলশ্রুতিতে ইরানের রামসারে জলাভূমি নিয়ে আন্তর্জাতিক চুক্তি হয়। কোনো অঞ্চল প্রাকৃতিক বা প্রায় প্রাকৃতিক বিরল অথবা অন্যান্য উদাহরণ যুক্ত জলাভূমি কে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলে সে জলাভূমি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। উলার লেক, ভেম্বনাদ কয়াল জলাভূমি, রেনুকা হ্রদ, চিল্কা হ্রদ সহ ভারতের রামসার সাইট ঊনপঞ্চাশ টি। পশ্চিমবঙ্গের দশটি রামসার সাইটের মধ্যে সুন্দরবন ও পূর্ব কলকাতার জলাভূমি বিশেষভাবে গুরুত্বপূর্ণ। সুন্দরবনের ম্যানগ্রোভের তুলনায় জলাভূমিসংক্রান্ত সমস্যাই মূল। সাম্প্রতিক গবেষণা অনুযায়ী সুন্দরবন উপকূল অঞ্চলের মাটি ক্রমান্বয়ে বসে যাচ্ছে, কিন্তু বেড়ে চলেছে সমুদ্রের জলের উচ্চতা। সঙ্গে সুন্দরবন এলাকার নদীগুলিতে ধারাবাহিক পলি জমার কারণে জলধারণ ক্ষমতা কমছে। বাঁধ নির্মাণে প্রচুর টাকা যাচ্ছে অথচ প্রাতিষ্ঠানিক দুর্নীতিতে জর্জরিত হয়ে পড়ছে উপকূলের নদী, সমুদ্র-বাঁধের গুণগত মান। আবার পূর্ব ভারতের জলাভূমি কলকাতা শহরের কিডনির মত কাজ করে জানি। ভৌগলিক ভাবে কলকাতা ভারতের অন্যতম নিচু শহর, সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে মাপলে চার-পাঁচ মিটারও হবে না। কলকাতার পশ্চিমে গঙ্গা, অথচ শহরের ঢাল পূবে। প্রতিদিন শহরে প্রায় সাতশো মিলিয়ন লিটার তরল বর্জ্য উৎপন্ন হলেও সেগুলো সব, এমনকি বৃষ্টি হলেও জল না জমে পূর্ব কলকাতার জলাভূমিতে পড়ত। আটের দশকের একজন সরকারি অফিসার ধ্রুবজ্যোতি ঘোষ চারিদিকে অনুসন্ধান চালিয়ে কলকাতার বর্জ্য জলের নিকাশি কোথায় খুঁজে বের করেন। ৯৫ শতাংশ জল এবং ৫ শতাংশ জীবাণু নিয়ে বর্জ্যজল পূব কলকাতার বিশাল জলাভূমিতে পড়ে শৈবাল ও মাছের খাদ্যে পরিণত হয়। ফলে স্রেফ প্রাকৃতিক বাস্তুতন্ত্রেই সূর্যালোকের অতিবেগুনি রশ্মির সাহায্যে ও সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ায় পুরো জল পরিশুদ্ধ অবস্থায় চলে আসে, বিপুল মাছের ভাণ্ডার তৈরি করে—পুরোটাই সম্পূর্ণ বিনামূল্যে—বিন্দুমাত্রও শোধন করাতে হয় না! ১৯৯০ সাল নাগাদ জ্যোতিবাবুর সরকার ঘোষণা করেন—ওই জলাভূমি বুজিয়ে একটা বিশাল বড় বাণিজ্যকেন্দ্র স্থাপন করা হবে। ধ্রুবজ্যোতি বাবু ও PUBLIC নামের এক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের দ্বারা হাইকোর্টে মামলা করে বন্ধ করা হয় এই রায়। প্রায় তিরিশ হাজার মানুষের জীবিকা সরাসরিভাবে জড়িত এই জলাভূমির সঙ্গে। আজও আমরা জানিই না, রোজ গরম গরম ভাতের সঙ্গে পাতে যে মাছের ঝোল বা ঝাল খাই, তার বেশিরভাগটাই আসে আসলে এই জলে গড়ে ওঠা ভেড়ি থেকে। পাশাপাশি, বিপুল পরিমাণ শাকসবজির জোগান দেয় এই এলাকা। স্রেফ এই কারণেই ভারতের সমস্ত মহানগরের মধ্যে বাজার খরচের ব্যাপারে সবচেয়ে সস্তা আমাদের কলকাতা। বিপুল পরিমাণ অক্সিজেনের জোগানও দেয় এই জলাভূমি। কার্যত একটি পয়সাও খরচ না করে দূষিত জল নিয়ে সে ফেরত দেয় টাটকা জল, মাছ, শাকসবজি, অক্সিজেন। এবং যে বিপুল পরিমাণ জলে প্রতিদিন ভেসে যেতে পারত কলকাতা, তার বেশিরভাগটাই টেনে নেয় এই জলাভূমি, তারপর অবশিষ্ট চলে যায় বিদ্যাধরী নদীতে। তাই অন্তত বছর দশেক আগে অবধি মুম্বই বা চেন্নাই নিয়মিত বন্যায় ভেসে গেলেও দিব্যি টিকে যেত কলকাতা। আজ ভেঙে পড়েছে পুরো ব্যবস্থাটাই। চলছে যথেচ্ছ প্রোমোটিং, জলাভূমি ভরাট, নগরায়ণ। চলছে দূষণ। ফলে নজিরবিহীন সংকটের মুখে পূর্ব কলকাতার এই জলাভূমি। প্রকৃতি সামান্য রুষ্ট হলেই আজ ভেসে যাচ্ছে কলকাতা। জমা জলে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, জলবাহিত ও মশাবাহিত রোগ বাড়ছে। নদীয়ার বুক থেকে জলঙ্গী প্রায় উধাও। জলঙ্গী মূর্শিদাবাদে গঙ্গার শাখানদী হিসেবে রয়েছে, আবার ভাগীরথীতে মিশে তার নিম্নভাগকে শক্তিশালী করেছে রীতিমতো। এই জলঙ্গী আর চূর্ণীর (রাণাঘাটে) মধ্যে সংযোগ ঘটায় অঞ্জনা। বিসর্জন ঘাট হিসেবে ব্যবহৃত হতে হতে, পাশে ইটভাটা গজিয়ে উঠে এবং শহরের অরক্ষিত নিকাশী নালা নদীর জলের সাথে সংযুক্ত থাকার ফলে দুই নদীই মজে গেছে। নদীয়ার এই দিকটায় মৎস্য চাষীরা সংখ্যায় বেশি, অথচ মাছের ঐতিহ্য শেষ। অঞ্জনায় পলি পড়ে চর তৈরি হয়ে গেছে। যে অঞ্জনা কৃষ্ণনগরের মাঝখান দিয়ে প্রবাহিত হয়ে সৌন্দর্য বিধান করত, সেই অঞ্জনা আর নেই। আমরা শহর গড়তে গিয়ে ভুলে গেছি জলাভূমিও শহরের সৌন্দর্য্য বিধান করতে পারে, তাকে নিয়েও শহরের সংস্কৃতি হতে পারে। আসলে প্রকৃতি’র মধ্যেই আমরা, ‘আমি’র দাম্ভিকতায় সেখানে সম্পর্ক বানাতে গেলে হবেনা, দরকার দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনা।
পর্ব – ১০
স্বার্থ
মানুষের কি লোভ তাই ভাবি।”- পোর্তুগিজ নাবিক বংশীয় অভিযাত্রী আত্তিলিও গাত্তি উনিশ শতকের আফ্রিকায় উৎকৃষ্টতম হীরের খোঁজে গিয়ে এমন উক্তি করতে পেরেছিলেন। শঙ্কর আর আলভারেজ তাদের যাত্রাপথে আফ্রিকান মাটাবেল জাতির রাজ্যে এসে পড়লে তারা সন্দেহ করেছিল যে আলভারেজরা ওদের দেশে হীরের খনির খোঁজে এসেছে। ভারত, আফ্রিকার মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলিতে তাদেরই প্রাকৃতিক সম্পদ অধিকার করে ভোগ-লুন্ঠন তো বটেই, আবার অধিবাসীদের উপর পুরোপুরি নিয়ন্ত্রণ রেখে দেশকে উপনিবেশ বানিয়ে রাখার প্র্যাকটিস আমাদের সকলের জানা। উনিশ শতকের শেষ দিকে এশিয়া, আফ্রিকা, ল্যাটিন আমেরিকা, অস্ট্রলেশিয়া যেমন পশ্চিমী দেশকে কাঁচামাল সরবরাহ করতো, সেরকমই ভারতও পুঁজিবাদী বিশ্ব অর্থনীতির বিশেষ খোপে ঢুকে পড়ে তার প্রাকৃতিক ধনসম্বলের বিনিময়ে। গোটা অষ্টাদশ শতক জুড়ে ভারতের প্রাকৃতিক ভূ-সম্বল এবং তাকে কেন্দ্রে রেখে জমিদার-রায়তের আন্ত:সম্পর্ককে মূলধন বা অর্থে সংশ্লেষিত করছিল ব্রিটিশ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। কোম্পানির স্বার্থে ও সুবিধার জন্য ১৭৬৫ সালে বাংলার কৃষিপণ্যের বাণিজ্যীকরণ হয়। প্রয়োজনে প্রাকৃতিক সম্পদকে গুদামজাত করাও হল। ওই শতকে
ইউরোপীয় বণিকরা আরেকটি পণ্যের কথা ভেবেছিল। পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে নীল চাষ ও নীল উৎপাদনের প্রযুক্তি ভারতে এনে ফরাসি বণিক লুই বোন্নাদ চন্দননগরে নীলকুঠি স্থাপন করেন (১৭৭৭)। ক্রমে ১৭৯৭ নাগাদ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সমর্থনে নীল চাষ শুরু হয়। বাধ্যতামূলক চুক্তিচাষে বাধ্য করা হত কৃষকদের, তাদের উর্বর ধানী জমি অনাবাদী পতিত জমিতে পরিণত হত। কখনো কখনো বছরে দু’বার নীল চাষ করনোর ফলে জমিতে আর অন্য কোনো ফসল ফলত না। ব্রিটিশরা আগে ‘ঔড’ (Woad) নামক একপ্রকার গাছ থেকে নীল তৈরি করত। ভারতবর্ষে বাণিজ্য শুরু করার পর ব্রিটিশ বণিকরা পশ্চিম ভারত থেকে নীল কিনে নিয়ে যেত ইউরোপে। দেশীয় আদি পদ্ধতিতে তৈরি এই নীলই ইউরোপের বাজার থেকে ঔডের রংকে সরিয়ে দেয়, এনে দেয় সন্তোষজনক মুনাফা। ভারতীয় উপনিবেশে খুড়োর কল ঝুলিয়ে দেখানো হলো যে অনাবাদি কিন্তু আবাদযোগ্য জমিকে চাষের আওতায় নিয়ে আসাটাই সভ্যতার অগ্রগতি। ফলে অরণ্য ধ্বংস করে কৃষির প্রসারণ চলল, বিতাড়িত হল জঙ্গলনিবাসীরা, শিকারি, খাদ্যসংগ্রাহক ও পশুপালকেরা।
উনিশ শতকে (১৮০৬ সালে) নেপোলিয়নের সঙ্গে যুদ্ধের সময় ব্রিটিশদের রাজকীয় নৌবাহিনীর রণতরী তৈরির কাজে নরম কাঠের জন্য প্রয়োজনীয় অরণ্যের চাহিদাও বেড়ে যায়। অবশ্যম্ভাবী নজর পড়েছিল উপনিবেশ ভারতে এবং অচিরেই ভারতীয় অরণ্যে সেরকম নরম কাঠের বৃক্ষের অভাব দেখা দেয়। শতাব্দীর গোড়াতেই বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে ওই ধরনের গাছ সংরক্ষণে, তত্ত্বাবধানে প্রথম ফরেস্ট অফিসার হিসেবে ডিয়াট্রিস ব্রান্ডিস নিযুক্ত হয় মালাবারে। এছাড়াও সেনাছাউনি, কাগজ-কল তৈরি ও রেলপথের স্লিপার বসানোর জন্য বিপুল পরিমাণে কাঠ লাগত। এই সময়ে কয়েকজন ব্রিটিশ প্রকৃতিচর্চাকারী, মূলত কোম্পানির কাজে নিযুক্ত শল্যচিকিৎসকেরা অরণ্য সংরক্ষণের দাবি তোলেন। ১৮৩২ সালে রাজ্য পরিচালনায় ‘মাদ্রাজ বোর্ড অফ রেভিনিউ’ কর্তৃক স্থানীয় অরণ্য সংরক্ষণ কার্যক্রমে নিয়মিত বন সংরক্ষণ কর্মসূচি শুরু হয় পেশাদার উদ্ভিদবিদ আলেকজান্ডার গিবসনের নেতৃত্বে। আর ১৮৬৪ সালে ডিয়েট্রিস ব্রাভিসের অধীনে সর্বভারতীয় স্তরে অরণ্য বিভাগ স্থাপিত হয় (পূর্ব বার্মার পেগু বিভাগের সমুদ্র তীরবর্তী এলাকায়)। অরণ্যের কোনো ক্ষতি না করে তার সঙ্গে পারস্পরিকতায় অরণ্য-সম্পদ ব্যবহারের জন্য (অরণ্যচারী আদিবাসীদের স্বার্থে) গবেষণা, প্রশিক্ষণ দানের প্রচেষ্টায় প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলেন তিনি। বলা যায় ‘সাস্টেনেবল’ (sustainable) উপায়ে অরণ্য-সম্পদ নিষ্কাশন করতে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছিলেন ব্রান্ডিস। এই প্রচেষ্টাই আর দু’দশক পরে বিকাশলাভ করে ‘ইম্পেরিয়্যাল ফরেস্ট স্কুল অফ দেরাদুন’ প্রতিষ্ঠায় (১৮৭৮)। বাংলার বনভূমি সম্পর্কে খোঁজ নেওয়ার উদ্যোগ কলকাতায় বন সংরক্ষকের দপ্তর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগেই শুরু হয়েছিল। সরকারের তরফে প্রতিটি বিভাগীয় অঞ্চলে বনের ধরন ও এলাকার সম্পর্কে জানতে চাওয়া হত। ছোটনাগপুরের বিভাগীয় কমিশনার এই প্রসঙ্গে পালামৌ অঞ্চলের শালগাছ পূর্ণ অরণ্য ব্যবহারের লক্ষ্যে নতুন রাস্তা নির্মাণের প্রয়োজনীয়তার কথা জানিয়েছিলেন। তখন ভাগলপুর বিভাগের অন্তর্ভুক্ত ছিল ভাগলপুর, মুঙ্গের এবং দার্জিলিং অঞ্চল। ওই বিভাগের কমিশনারও দার্জিলিং সম্পর্কে তাঁর প্রতিবেদনে জানিয়েছিলেন যে এখানকার অরণ্যভূমি মূল্যবান ও মূল্যহীন উভয় ধরনের গাছে পূর্ণ এবং সরকারি আয়ত্তাধীন। ভুটান, আসাম, কাছাড় চট্টগ্রাম ও বিহারের নতুন বনবিভাগ গঠনের প্রস্তাব রেখেছিলেন অ্যান্ডারসন সাহেব। ১৮৭৪ সালে আসাম পৃথক প্রদেশে রূপান্তরিত হওয়ার পর চট্টগ্রাম বনভূমি প্রশাসনিক দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে বহুমূল্যবান গাছের জন্য। এই বনভূমিকে বাঁশ গাছ, ঘাস জমি ও পার্বত্যখন্ডে ভেঙে নেওয়া হয়েছিল।
উনিশ শতকের মধ্য ভাগে বাংলায় যখন রেলগাড়ি সম্প্রসারণসহ নানা কারণে বন সংরক্ষেণর ভাবনা-চিন্তা চলছিল, তখনই ভারতে অরণ্য সম্পর্কিত সর্বভারতীয় আইন পাশ হয় (১৮৬৩)। এই আইনের তিনটি বিষয় সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।
প্রথমত, বৃহৎ বৃক্ষসমৃদ্ধ অরণ্য ও ঝোপজঙ্গলকে সরকারি বনাঞ্চলে রূপান্তরিত করা যাবে। তবে এই ব্যবস্থা করতে গিয়ে ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর বনের উপর যে অধিকার প্রতিষ্ঠিত রয়েছে তা কেড়ে নেওয়া যাবে না।
দ্বিতীয়ত, বন-সংরক্ষণের জন্য প্রদেশ-ভিত্তিক প্রয়োজনীয় আইন তৈরি করা যাবে। কিন্তু তা রূপায়িত করতে হবে সর্বভারতীয় আইনের প্রেক্ষিতে। তৃতীয়ত, আইন ভঙ্গকারীকে উপযুক্ত শাস্তিদান করা যাবে।
ভারতে ঔপনিবেশিক সরকারের বন-নীতি স্পষ্ট রূপ পরিগ্রহ করতে শুরু করল, যা প্রযোজ্য হল বাংলা অঞ্চলেও। এর কিছুকাল পরে ঔপনিবেশিক ভারতে ১৮৬৫ ও ১৮৭৮ সালে যথাক্রমে ‘সুরক্ষিত’ ও ‘সংরক্ষিত’ অরণ্য আইন চালু হয়। প্রথম আইনে বিশেষ কিছু গাছ কাটা নিষিদ্ধ হলেও প্রয়োজনের জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ, পশু চরানো ও অন্যান্য সম্পদ আহরণের অধিকার বজায় ছিল। দ্বিতীয় আইনে উক্ত সব অধিকার ছিনিয়ে নিয়ে রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণকে ব্যাপক করা হয়, গাছে কোপ মারাও অপরাধ হয়ে ওঠে। আগে জঙ্গলের পচা পাতা স্থানীয় কৃষিক্ষেত্রে সার হিসেবে ব্যবহৃত হতো; অধিকৃত হওয়ায় তা তো বন্ধ হলোই, এমনকি ফসল কাটার পর চষা জমিতে যে পশু চরিয়ে পশুমলে খেতের উর্বরতা বাড়ানো হতো, সেই মেষপালক ও রাখালদের অবাধে চলাফেরার অধিকারের উপরেও আইনি চাপ বাড়লো। অরণ্য, চারণভূমি আর সুস্থিত কৃষিব্যবস্থার মধ্যে পারস্পরিক যোগাযোগের ঐতিহ্য এভাবে ভেঙে পড়ে। স্থানীয় জনসাধারণ, যারা অভাবের সময়ে মূল খাদ্যশস্য ভাত পেতনা, তারা সম্পূরক খাদ্য পেত বনাঞ্চল থেকেই; মিটত পুষ্টির ঘাটতি। আগে চাষবাসে (Subsistence farming) উৎপাদিত ফসল ও পশুসম্পদ কৃষকের পরিবারের রক্ষণাবেক্ষণ করত। যা যৎসামান্য থেকে যেত, উদ্বৃত্ত রূপে পরের বছরের জন্য বা অপরকে বিক্রির জন্য। ঔপনিবেশিক শাসনে এই দীর্ঘ স্থাপিত ব্যবস্থাটাই নষ্ট হয়ে গেল। উনিশ শতকে রেলের যে সম্প্রসারণ ঘটেছিল, তা মূলতঃ ভারতের শস্য সম্পদ উপকূলীয় শহরে পরিবহনের জন্য। অর্থাৎ উপনিবেশ থেকে সাম্রাজ্যবাদী দেশে সবটাই চলে যেত। স্থানীয় প্রকৃতি-সমাজ-মানুষের মধ্যে সুষ্ঠু বিপাকীয় চক্রটি আর সম্পূর্ণ হয়নি। ফলে দেশের মানুষের অপুষ্টিতে ভোগা থামেনি, ১৮৭০ ও ১৮৯০ সালের দুর্ভিক্ষে মানবতার চরম অপমান ঘটে।
পর্ব – ১১
প্রকৃতি’র প্রাণ তখন গানে, অনুভূতিতে
১
ক. “ভবণই গহন গম্ভীর বেগেঁ বাহী।
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ ন থাহী।।”
(৫ নং চর্যা)
খ. অপণা মাংসেঁ হরিণা বৈরী।
খণহ ন ছাড়হ ভুসুকু অহেরী।।
(৬নং চর্যা)
গ. সোনে ভরিলী করুণা নাবী।
রূপা থোই নহিকে ঠাবী।।
বাহতু কামলি গঅণ উবেসেঁ।
(৮ নং চর্যা)
এই তিনটি চর্যার দু’টিতে নদীপ্রধান বাংলার ছবি আছে। আমাদের প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শন- চর্যাগীতিতে গৌড়বঙ্গের যে স্থানিক পট পাই, তা বৃহৎ বঙ্গের পট। গহন ভবনদী গম্ভীর বেগে বয়, দুই পারে তার কাদা আর মাঝে থৈ নেই। আবার ৮ নং চর্যায় সোনায় ভর্তি করুণা নৌকার আকাশের উদ্দেশ্যে বয়ে চলার কথা। অর্থাৎ চর্যায় চিত্রিত নদী নাব্য এবং বঙ্গের নাব্য এলাকা বলতে পূর্ববঙ্গ। হরিণ তার নিজের মাংসের কারণে নিজের কাছেই শত্রু, ভুসুকু তাকে ক্ষণিকের জন্যেও ছাড়েনা। জঙ্গলের চারপাশে বেড় দিয়ে এই হরিণ শিকারের গল্পই ৬ নং চর্যার মূল। “সহজ নলিনীবণ পইসি নিবিতা/ জিম জিম করিণা করিণিরে রিসঅ।” (৯ নং চর্যা)- এখানে মদমত্ত হাতির গল্প। বলতে গেলে উত্তরবঙ্গ ও আসামের গজ সম্পদ, পূর্ববঙ্গের কাউন-চিনা ও কাপাসের যে বর্ণনা পাই, তা চর্যার বহুবিস্তৃত ভৌগোলিক সীমা ছাড়া অসম্ভব। “তুলা ধুণি ধুণি আঁসু রে আঁসু।/ আঁসু ধুণি ধুণি ণিরবর সেসু।।”- তুলো ধুনে ধুনে আঁশ বের করা হল, আঁশ ধুনে ধুনে নিরবয়ব করা হল। এছাড়াও জলাশয়ে ভর্তি বাংলার পদ্ম বা কমল’কে মস্তিষ্কে অবস্থিত মহাসুখচক্র করে কমলরসকে মহাসুখরস হিসেবে পান করা, অবধূতীমার্গরূপী কমলমৃণালে বোধিচিত্তের জন্ম ও নির্বাণ লাভের গূঢ় তত্ত্বের গান গেয়েছেন বৌদ্ধ সহজিয়া সিদ্ধাচার্যেরা।
নদী, নৌকার ‘ইমেজারি’ আরো কয়েকটি চর্যায় মেলে, যেমন- ১৩, ১৪, ৩৮ ও ৪৯ নং চর্যায়। যথাক্রমে কায়-বাক-চিত্তকে নৌকা করে জলে ভাসানো, ডোমনী মেয়ের দ্বারা গঙ্গা-যমুনার মাঝে নৌকা বইয়ে নিয়ে অবলীলায় পার হয়ে যাওয়া, চিত্ত স্থির করে মনকে দাঁড় বানিয়ে ছোট নৌকার ভেসে যাওয়া ইত্যাদি৷ ৪৯ নং চর্যায় সরাসরি পদ্মাখালে বজ্র নৌবহর চলার কথা, জলদস্যুর কথা বলা আছে। যদিও এই জলদস্যুদের বঙ্গাল বলা হয়েছে। আর্যের দৃষ্টিতে বঙ্গাল তথা স্থানীয়রা দুর্ধর্ষ। চর্যার তত্ত্বানুযায়ী এই বঙ্গালদের দ্বারা আক্রান্ত হওয়া মানে দ্বৈতবোধের বিকল্প, মিথ্যা জ্ঞান থেকে মুক্ত হওয়া। বঙ্গাল আক্রমণ করে এসব বন্ধন হরণ করে। এখানে বাণিজ্য সম্প্রসারণার্থে নদী ও নৌকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ৩২ নম্বর চর্যায় সোজা রাস্তার প্রসঙ্গে পথের দুধারে ডোবা আর খালের অস্তিত্ব সম্পর্কে উল্লেখ আছে। আমাদের গ্রামবাংলার রূপ এমনই।
চর্যাগানে একটি আদি জনগোষ্ঠীর উল্লেখ পাওয়া যায়- আদি অস্ট্রাল গোষ্ঠীর শবর শবরী। এরা স্পষ্টতই আর্য পূর্ব জনগোষ্ঠীর অন্তর্গত, কাজেই তথাকথিত ‘সমাজ’ থেকে দূরে অরণ্যে-পর্বতে এদের বাস- “উঁচা উঁচা পাবত তহি বসই শবরী বালী” (২৮ নং চর্যা)। পাশেই তরু মুকুলিত হয়, কঙ্গুচিনা ফল পাকে। কৃষিতে শবর-শবরী নি:সন্দেহে দক্ষ। পুষ্প আভরণ, ময়ূর পুচ্ছ- এই সমস্ত প্রাকৃতিক উপাদানই তাদের অঙ্গসজ্জার প্রধান উপকরণ। প্রকৃতির মতো নিঃসংকোচ ও আদিম শবরীকে দেখে শবর পাগল হয়। প্রকৃতিলগ্ন এই জনগোষ্ঠীতে নারী-পুরুষ ভেদের ‘সোশ্যাল ডিসকোর্স’টি অনুপস্থিত। বরং শবর রমনীরা স্বাধীন- “একেলি শবরী এ বন হিন্ডই কর্ণকুন্ডলবজ্রধারী”। দৈনন্দ্যিন জীবনের একঘেয়েমি ব্যতিরেকে এদের জীবনের শৃঙ্গাররস যে অনুপস্থিত ছিল, এমত মনে হয়না। সম্ভোগ উপচার রূপে ব্যবহার করত তাম্বুল-কর্পূর আর বিহারের জন্য উঁচু পাহাড়ে জ্যোৎস্নাবাড়ি তৈরির প্রসঙ্গও আছে। নিসর্গের সঙ্গে জীবনের ওতপ্রোত যোগ এদের জীবন বোধ ও সৌন্দর্য বোধের নির্ণায়ক৷
২

পরবর্তী সাহিত্যিক নিদর্শন ১৯১৬ সালে বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্বল্লভ কর্তৃক বঙ্গীপ্রকাশিত শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্য৷ এখানে রাধা কৃষ্ণ উভয়েই নদী-মাঠ-প্রাকৃতিক বাগান ও জঙ্গলময় গ্রাম্য পটভূমির। রাধা দধি দুধে পসার সাজিয়ে নেতবস্ত্রের আবরণ দিয়ে সখীদের সঙ্গে করে বড়ায়িকে নিয়ে প্রতিদিন মথুরায় যায় বনপথ দিয়ে। আর কৃষ্ণ পাচনি হাতে মাঠে গাই চরায়। কৃষ্ণ রাধাকে তার প্রেম নিবেদনের ক্ষেত্রে নিতান্ত সুলভ প্রাকৃতিক সম্পদ- ফুল (চাপা, নাগকেশর), ফুলের মালা, কর্পূর মিশ্রিত পান ইত্যাদি নিবেদন করেছে। লক্ষণীয় যে রাধার রূপ সৌন্দর্যের বর্ণনায় লতাপাতা, ফুল প্রভৃতির উপমা এসেছে- “কপোল যুগল তার মহুলের ফুল/ তিল ফুল জিণী নাসা কম্বু সম গলে/ কনকযূথিকা মালা বহু যুগলে।” রাধার চুল দেখে অরণ্যের তমাল কলিকা লজ্জায় মুখ লুকায়, তার কাজল শোভিত চোখ ও স্তনযুগল যথাক্রমে নীলপদ্ম এবং পাকা ডালিম ফলের মত। এমনকি কণ্ঠদেশ দেখে শঙ্খ লজ্জায় সমুদ্রের জলে গিয়ে প্রবেশ করে। কদম গাছের তলাতেই বসে রাধাকে যমুনার তীরে দানের ছলে হেনস্থা করার ঘোট পাকায় কৃষ্ণ। যমুনা নদীর বুকে একখানি ছোট নৌকাতেই কবি গোটা নৌকা খন্ডের ঘটনা ঘটিয়ে ফেললেন। আবার ছত্রখন্ডে মথুরা নগর থেকে দধি দুধ বেঁচে ঘরে ফেরার সময় রাধা ক্লান্ত হয়ে পড়লে শীতল বাতাস তাঁর প্রাণ রক্ষা করেছে। যদিও কৃষ্ণের ঐশ্বরিক মহিমাকে অক্ষুণ্ণ রাখার জন্য দেখানো হয়েছে যে কৃষ্ণ রাধার পাশে আছেন বলেই অমন স্নিগ্ধ হাওয়া প্রবাহিত হয়েছে, তবু পটভূমি ও উপকরণ উপাচার সবই পরিবেশ প্রকৃতির। কালীদহের জল পান,স্নান সহ বিবিধ ব্যবহারের উপযোগী, অথচ তাতে বিশাল সাপের বাস। অতএব জল বিষমুক্ত করার জন্য কৃষ্ণ বিষাক্ত কালীয় নাগ দমন করলেন। বংশী খন্ডে এসে দেখব কৃষ্ণ রাধাকে এড়িয়ে অবস্থান করলে রাধা তাঁর সন্ধানের জন্য বড়ায়িকে পাঠাতে চায়৷ কিন্তু বড়ায়ির সাফাই- “যমুনা নদীতে মো কেমনে হৈবোঁ পার। ঘড়িয়াল কুম্ভীর তাহাত আপার।…বৃন্দাবন মাহা ঘোর ভয়ংকর। বাঘ ভালুক তাএ বসে বিথর।” স্পষ্টতই বৃন্দাবনের প্রাকৃতিক পরিবেশ আদিম ও ভয়ানক। বাঁশির শব্দ শুনে রাধা জানায় তার মাটির ভিতরে ঢুকে যেতে ইচ্ছে হয় পাখি হয়ে উড়ে যেতে মন চায় এবং যেখানে যেখানে ফুল ফল প্রভূত পরিমাণে ফুটে আছে সেখানে কৃষ্ণকে অবশ্য করে খোঁজ করতে বলে দিয়েছে রাধা (বড়ায়িকে)। প্রকৃতি, তার উন্মুক্ত উদার প্রফুল্ল রূপের সঙ্গে ঈশ্বরের উপস্থিতিগত অনুভূতিকে মিলিয়ে নেওয়ার এই ভঙ্গি রাধার একার নয়, বাংলার আপামর ধর্মীয় জনের। বিরহেও প্রকৃতি রাধার সঙ্গী হয়েছে নানাভাবে- কদমতলে শুলে সাধারণত শীতল হওয়ার কথা, অথচ রাধার অন্তর পুড়তে থাকে, এমনকি সজল পদ্মদলে শয়ন করলেও রাধার দহন জ্বালা কমে না। চন্দ্রকিরণে তীব্র উষ্ণতা অনুভূত হয় ও চন্দনের প্রলেপ রাধার উপশম ঘটাতে পারেনা। বিরহের নায়িকা হিসেবে রাধার বারমাস্যা অর্থাৎ প্রকৃতির ছয় ঋতুর বারো মাসের দু:খ-পাঁচালি বিবৃত আছে। সংস্কৃত সাহিত্যের শকুন্তলা যেমন প্রকৃতির কন্যা ছিল, ‘nature’ বা প্রকৃতি তেমনি রাধার কাছে তাঁর জীবনানুভূতি ও আরো অনেক কিছুর সহায়ক এমনকি কিছু ক্ষেত্রে ত্বরকও বটে। এজন্যই রসশাস্ত্রে রসের উদ্দীপন বিভাব রূপে পরিগণিত হয়েছে প্রকৃতি।
প্রাকৃতিক পরিবেশ অনেক আগে থেকেই সাহিত্যে এসেছে। কিন্তু অত্যাধুনিক জীবনের আধুনিক মানদণ্ডে সাহিত্যে প্রকৃতি-পরিবেশকে দেখা হল মূলত: ‘ইকো ক্রিটিসিজম’ এর হাত ধরে। খ্রিস্টিয় ১০০০ থেকে ১২০০ শতাব্দীর মধ্যে পশ্চিমি সভ্যতা ভৌত পরিবেশের (জৈব ও অজৈব) উপর জ্ঞানের আধিপত্য বিস্তারের কৌশলটি আয়ত্ত করে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে বিশ্ব-বিজ্ঞানে নেতৃত্ব দখল করে (ইউরোপ) এবং শিল্পবিপ্লবকে (১৭৫০) অনিবার্য করে তোলে। এই সময়পর্বে (১৭-১৮ শতক) যুক্তি ও বিজ্ঞানের শক্তি সর্বৈব বিস্তৃত হয়, কিন্তু ক্রমে যান্ত্রিক যৌক্তিকতাবাদ পুঁজিবাদের সহায়ক হয়ে উঠলে শুরু হয় প্রাকৃতিক ধনসম্বলের প্রক্রিয়াকরণ। স্পষ্টতই বিজ্ঞান নির্দেশিত পরিবেশ-সচেতনতাকে মানুষ অগ্রাহ্য করতে থাকে ধর্মীয়-সামাজিক-দার্শনিক প্রেরণায়। উনিশ শতকে নগরায়ণ-শিল্পায়নের প্রভাবগত ফলাফল, শ্বাসরোধকারী কুৎসিত পরিবেশ নিয়ে তাত্ত্বিক আলোচনা প্রসঙ্গে কার্লাইল ‘এনভায়রনমেন্ট’ শব্দটির সংজ্ঞায়ন করেন (১৮২৮) এবং আর্নেস্ট হেকেল ‘ইকোলজি’র ধারণা প্রচার করেন (১৮৬৬)। বস্তুত এই শতক যুগপৎ মানুষের বিনাশী কর্মকান্ড আর পরিবেশ সচেতনতার কাল। ১৮৯৫ সাল নাগাদ জোহানেস ইউজিন ওয়ার্মিং কর্তৃক ইউনিভার্সিটি পাঠক্রমে একটি স্বতন্ত্র শাস্ত্র হিসেবে ‘ইকোলজি কোর্স’ চালু করেন। এরপর জটিল পরিবেশগত সমস্যা বিশ্লেষণের জন্য ১৯৫০ সালে স্ট্যানলি আর্বাচ ‘এনভায়রনমেন্টাল সায়েন্স’ বিভাগের প্রতিষ্ঠা করেন। মাঝে ওই শতকেরই তিনের দশকে (১৯৩৫) আরেকবার ‘ইকোলজি’কে ফিরে দেখার তাগিদে আর্থার ট্যান্সলে ‘ইকোসিস্টেমে’র কথা বলেন।
সাতের দশকে Eco-fiction anthology ও Literature and ecology, An experiment in eco-criticism গ্রন্থে ‘ইকোক্রিটিসিজম’ শব্দের ব্যবহার হলেও ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে গবেষক চেরিল গ্লটফেল্টি Ecocriticism reader গ্রন্থে ‘ইকোক্রিটিসিজম’কে একাডেমিক ডিসকোর্সে জনপ্রিয় করে তোলেন।
পর্ব – ১২
‘ইকোক্রিটিসিজম’- একটি ‘গ্রিন’ পরিভাষা কিংবা আরো কিছু
Joseph W. Meeker প্রথম ‘Literary ecology’ শব্দবন্ধ চালু করেন। পরে ১৯৯৬ সালে William Rueckert ব্যবহার করেন ‘Eco-criticism’ কথাটি। ‘Eco-criticism’ বলতে আমরা আমাদের কৃষ্টিগত/সংস্কৃতিগত ক্ষেত্রে (সংস্কারের ফসল) যেভাবে, মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেকার সম্পর্ককে কল্পনা করা হয়, চিত্রিত করা হয়- তাকে বোঝায়। এটি আধুনিক পরিবেশ আন্দোলন দ্বারা অনুপ্রাণিত। Greg Garrard তাঁর ‘Ecocriticism’ বইতে একবিংশ শতাব্দীর বিশেষত গত ত্রিশ দশক ধরে মানব-প্রকৃতি সম্পর্ক অধ্যয়নে যে যে পরিবর্তনগুলি দেখা দিয়েছে সেগুলি নিয়ে সুস্পষ্ট তথ্য (account) দিয়েছে। পরিবেশ যেখানে গাছ-পালা, লতাপাতা ও অজস্র সবুজ নিয়ে বর্তমান- সেটা দেখা মানেই কিন্তু cco-criticism না। বরং সবুজের সঙ্গে মানুষের সম্পর্কের গ্রাফ যখন সাহিত্যের অধ্যয়নে চর্চিত হয়, তখন সেটা উক্ত ধরনের ক্রিটিসিজমের অন্তর্গত হয়। মানুষ-পরিবেশ সম্পর্কের বুননক্ষেত্রে দাঁড়িয়ে সেই সম্পর্কের প্রেক্ষণবিন্দু থেকে
প্রকৃতিকে দেখা, তার মধ্যেকার উপাদানগুলির ভারসাম্যাবস্থা ও ভারসাম্য-হীনতা দুই’ই সাহিত্যে (literature) পর্যবেক্ষণ করাটা ecocriticism-এর অন্তর্গত। এই পর্যালোচনা ও বিশ্লেষণের ফলে প্রকৃতি ও চরাচরের প্রতি (পরিবেশ-প্রতিবেশ) মানুষের সচেতনতা, সংরক্ষণশীলতার প্রসঙ্গ আসে। অর্থাৎ মানব- প্রকৃতি সম্পর্কের বিন্যাস, পর্যবেক্ষণ, পর্যালোচনা যখন সাহিত্যে প্রতিফলিত হয় (ecocriticism) পরিবেশ সমালোচকরা তাদের সাংস্কৃতিক বিশ্লেষণগুলি স্পষ্টতই এক সবুজ নৈতিকতা ও রাজনৈতিক বিষয়সূচি বা আলোচ্য সূচিতে বেঁধে রাখেন। ১৯৯০ এর সময়ে ‘Ecocriticism’-এর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দু’টি কাজের উদাহরণ হল – ওয়ার্ডস ওয়ার্থ ও শেলি’র সাহিত্য পর্যালোচনা। এই ক্রিটিসিজমের পরিধি যত বেড়েছে তত পরিবেশ সংক্রান্ত নানা প্রশ্ন ও সমস্যা, এমনকি চিন্তাভাবনার দিক উন্মোচিত হয়েছে। ইকোক্রিটিক’রা পরিবেশগত ধারণা ও পরিবেশগত প্রকাশের সেই দিকগুলি খুঁজে পেতে চায় যা বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে আলোচনা-সমালোচনার পরিসর তৈরিতে সক্ষম। তাঁদের প্রধান কাজই হল যতদূর সম্ভব পরিবেশ সাক্ষরতা তৈরি করা
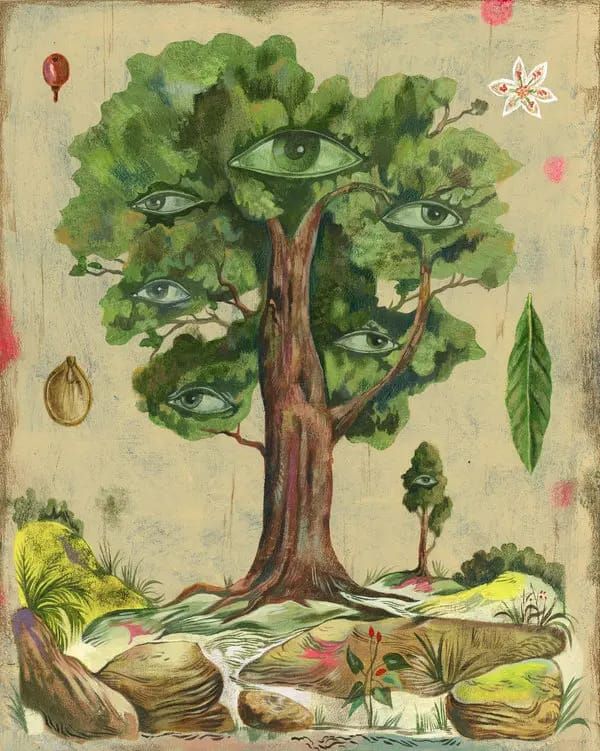
আধুনিক পরিবেশবাদ শুরু হয় র্যাচেল কারসনের ‘Silent Spring’ (১৯৬২) গ্রন্থটি থেকে। বইটির প্রথম অধ্যায় ‘A fable for Tomorrow’তে দেখানো হয়েছে প্রাচীন আমেরিকার সেই প্রাচীন সময়কে, যখন প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে ঐক্যের সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত ছিল। এই বইটির বর্ণিত রূপকথা গল্প চারণভূমি ও মেষপালক সংক্রান্ত ‘প্যাসটোরাল’ ঐতিহ্যকে বহন করে, যেখানে আছে ‘সমৃদ্ধ খামার’, ‘সবুজ ক্ষেত্র’, পাহাড়ি শেয়াল, নীরব হরিণ, ফার্ন ইত্যাদি। কিন্তু এদের পারস্পরিক শান্তি, জালিক সম্পর্কের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। ‘Malady’ বা ব্যাধি ও ‘spell’ তথা জাদুমন্ত্র, বলা ভালো কু-জাদুমন্ত্রের দ্বারা। গ্রামীণ জীবনের প্রতিমা, প্রতীক গুলির প্রতিটি উপাদান ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে পরিবর্তনের প্রতিনিধি দ্বারা। এবং এই পরিবর্তনের রহস্য ক্রমিক ব্যবহারবিধির মাধ্যমে কেবলই বেড়েছে। ‘Silent Spring’ রূপকথার গল্পের মাধ্যমে দেখায় যে পৌরাণিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কাহিনীটি অতিপ্রাকৃত হলেও তা মানুষের কৃতকর্মের ফল। আবার John Keats রচিত ‘La belle Dame Sans Merci’তে সুন্দরী একজন মহিলার জাদু দন্ডের রহস্যময় অশুভ প্রভাবে গাছপালা সহ প্রকৃতির বিভিন্ন অঙ্গ-উপাঙ্গে রোগ উপস্থিত হলেও আসলে আর কেউ নয়, মানুষই এর জন্য দায়ী- “No whichcraft no enemy action had silenced to the rebirth of new life in this stricken world. The people had done it themselves.” ‘Silent Spring’ দেখায় যে এরকম প্রাকৃতিক বিপর্যয় গোটা আমেরিকায় শুরু হয়েছে বিচ্ছিন্নভাবে।
একাডেমিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে
‘Association for Study of literature & the environment’ (ASLE) প্রথম ‘Ecocriticism’ নিয়ে চর্চা শুরু করে। আমেরিকায় প্রথম এর চর্চা শুরু হয়। ক্রমে ব্রিটেনে, জাপানে এই অ্যাসোসিয়েশনের শাখাগুলি চালু হয়। ১৯৯৮ সালে ISLE বা Interdisciplinary studies in literature and Environment শুরু হয় ব্রিটেনে৷ এমনকি বর্তমানে আয়ারল্যান্ডেও চালু হয়েছে। এর অফিসিয়াল জার্নাল ‘Green letters’ প্রকাশিত হয় ২০০০ সালে। ১৯৯৬ সালে প্রকাশিত ‘Ecocriticism reader’, ইকোক্রিটিকাল প্রবন্ধের প্রাথমিক সংগ্রহের ভূমিকায়, শেরিল গ্লটফেল্টি সেই সময়ে বিদ্যমান পরিবেশগত সমালোচনার অভাবকে নির্দেশ করেছেন-
“If your knowledge of the outside world were limited to what you could infer from the major publications of the literary profession, you would quickly discern that race, class, and gender were the hot topics of the late twentieth century, but you would never suspect that the earth’s life support systems were under stress. Indeed you would never know that there was an earth at all.” (xvi)
জাতি, শ্রেণী এবং লিঙ্গগত বিষয় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকের আলোচিত বিষয় হয়ে থেকেছে। কিন্তু আপাতত আমরা সন্দেহ করিনি যে পৃথিবীর জীবন ব্যবস্থা ভয়ানক সমস্যার মধ্যে আছে। প্রকৃতপক্ষে কখনও হয়তো আমরা ভেবেও দেখিনি যে আমরা, আমাদের চারপাশ- সবটা নিয়েই গোটা একটা পৃথিবী। এই ধীর অগ্রগতির প্রধান কারণ সম্ভবত এই যে পরিবেশগত বিজ্ঞানের ডোমেইনে ‘বৈজ্ঞানিক’ সমস্যা হিসাবে যা সাধারণত বিবেচিত হয়, তার সাথে নিজেকে জড়িত করতে পারার মানসিকতার অভাব। ব্রিটেনের শিক্ষাবিদ পাপ্পা মারল্যান্ডের (Pappa Marland, University of Worcester, institute of humanities and creative arts-UK) মতে- “Another issue was the difficulty of speaking of the earth itself.”
তত্ত্বের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলি ১৯৭০-এর দিকে চলমান ছিল, যেমন ‘নারীবাদ’ এবং ‘উত্তর-ঔপনিবেশিকতা’। উভয়েই মূল ধারা থেকে ‘অপর’ (other) করে দেওয়ার রাজনৈতিক এবং সামাজিক প্রভাবগুলির সমালোচনা করেছিল। এবং আধিপত্যবাদী মতাদর্শ দ্বারা স্তব্ধ কণ্ঠস্বরগুলিকে সনাক্ত করার, তাদের জায়গা করে দেওয়ার উপায় নির্দেশের জন্য তত্ত্বগুলির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কিন্তু, বিশেষ করে ইকোক্রিটিকদের মধ্যে প্রাথমিকভাবে এই অনুভূতির জন্ম হয়েছিল যে কোনো ‘ক্রিটিকাল থিয়োরি’, ‘লাইফ সিস্টেম’ পৃথিবীর হয়ে তাদের ওকালতির প্রচেষ্টাকে ব্যর্থ করে দেয়। জন পারহাম (John Parham) যথার্থই প্রথম তরঙ্গ ইকোক্রিটিসিজম-এর তত্ত্বের প্রতি একটি ‘প্রতিকূল ও আক্রমণাত্মক’ মনোভাব পোষণ করেছেন। নতুন ইতিহাসবাদের প্রেক্ষাপটে অ্যালান লিউ (Alan Liu) দাবি করেন যে মানুষের পৃথিবীতে মানব সৃষ্ট সরকার দ্বারা প্রযুক্ত রাজনৈতিক সংজ্ঞার বাইরে পরিবেশ-প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করা যায়না। তিনি ‘Nature’ বলতে অন্তস্থ ধ্যানের সম্পদকে মনে করেছিলেন, যা শব্দাতীত। কিন্তু টেরি গিফর্ড (Terry Gifford) এই বক্তব্য ও মনোভাবের প্রতিক্রিয়ায় লেখেন-
“While Liu is right to identify the word ‘nature’ as a ‘meditation’, the general physical presence that is one side of that meditation.” (Green voice, 15)
উত্তর ঔপনিবেশিকতায় একদিকে পরিবেশ-প্রকৃতির ব্যাখ্যাতীত উপস্থিতি, অন্যদিকে এর যতটুকু চোখে দেখা যায় সেই ‘physical appearance’কে ধরে থিয়োরির বৈশ্বিক চর্চা শুরু হয়। প্রকৃতির বাহ্যিক উপস্থিতির চর্চায় মানুষের ‘ভোগী’ সত্তা এবং ভোগের স্বভাব, ভোগের অধিকারের অসম বৈশ্বিক বন্টন নিয়ে আওয়াজ উঠল। এল পরিবর্তনের আকাঙ্খার কথা।
পর্ব – ১৩
ইকোক্রিটিকাল ওয়েভ
বিংশ শতকের ছয়ের দশকে (১৯৬০) পরিবেশগত আন্দোলনের সূচনা এবং ১৯৬২ সালে রাচেল কারসনের ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ প্রকাশের মাধ্যমে ‘ইকো’ (Eco) সম্পর্কিত ‘ক্রিটিসিজমে’র (criticism) আবির্ভাব ঘটে। তবে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে এই ধরনের সমালোচনা শুরু হয় আটের দশকে এবং পর্যায়ক্রমিকভাবে কয়েকটি ধারায় তা বিকাশ লাভ করে। এখনও পর্যন্ত পরিবেশ-সমালোচনার যে তরঙ্গ দেখা দিয়েছে – একটি ১৯৮০ সালে এবং অপরটি ১৯৯০ তে। লরেন্স বুয়েল ও চেরিল গ্লটফেল্টির মতো পরিবেশবাদী তাত্ত্বিকরা মোটামুটি এই দুই তরঙ্গকেই চিহ্নিত করেছিলেন। ‘ইকোক্রিটিসিজম’- এই বিশেষ ধরনের সমালোচনাগত অধ্যয়নে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রথম পাঠ্য সীমার বাইরে বিশ্ব-সাহিত্যের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করা হয়। এমনকি অভিব্যক্তিগত দিক থেকে সাহিত্যের সেই ফর্মগুলির সন্ধান চালানো হয়, যা খুব শক্তিশালী পরিবেশগত বার্তা রাখতে সক্ষম। ‘The environment imagination’-এ লরেন্স বুয়েল (১৯৩৯) একটি পরিবেশ-ভিত্তিক কাজের বিষয়ে চারটি ‘উপাদানের’ চেকলিস্ট তৈরি করেন:
১। ‘Non human environment’ তথা অ-মানুষী পরিবেশ শুধুমাত্র একটি ফ্রেমিং ডিভাইস হিসাবে পৃথিবীতে উপস্থিত নয়। বরং তার ইতিহাসের সাথে মানব ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত,
২। মানুষের স্বার্থই একমাত্র বৈধ স্বার্থ বলে বিবেচিত হতে পারে না,
৩। পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতা কোনো টেক্সটের নৈতিক অভিযোজনের দিক,
৪। কোনো ধ্রুবক নয়, তার পরিবর্তে একটি প্রক্রিয়া হিসাবে পরিবেশের উপস্থিতির অনুভূতি (sense of environment as process) অন্তত টেক্সটের অন্তর্নিহিত ব্যাপার হবে।
স্পষ্টতই এই চেকলিস্ট পরিবেশ সংক্রান্ত সমালোচনার প্রতি লক্ষ্য রেখে তৈরি। পরিবেশের প্রতি কোনো টেক্সটের ‘নৈতিক অভিব্যক্তি’র দিকটি নিয়ে প্রশ্ন তুলে লরেন্স বুয়েল ‘ইকোক্রিটিসিজমে’ গুরুত্বপূর্ণ উপাদানকে নির্দেশ করেন- ‘পরিবেশবাদী অনুশীলন অঙ্গীকারের চেতনা’ (Spirit of commitment to environmentalist praxis)। একটি তাত্ত্বিক ক্ষেত্র হিসাবে সংস্কৃতি থেকে রাজনীতি পর্যন্ত ছড়িয়ে পড়ে এই চিন্তা ও চেতনার চর্চা। ‘ইকোক্রিটিসিজমে’র প্রথম তরঙ্গটি দু’টি মাত্রায় পরিবেশ-প্রকৃতি সম্পর্কে লেখালেখির উপর জোর দেয়- ক. অধ্যয়ন (Study) এবং খ. একটি অর্থপূর্ণ অনুশীলন (Meaningful Practice)-এর ক্ষেত্রে।
‘ইকো-ক্রিটিসিজমে’র প্রথম তরঙ্গ প্রকৃতির মূল্য এবং প্রকৃতির পক্ষে কথা বলার ও দাঁড়ানোর প্রয়োজনীয়তাকে উন্নীত করেছিল। এই সময়ে মানুষ বিশ্বাস করতে শুরু করে যে মানবিক ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের দায়িত্ব একসাথে সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং পরিবেশ ও জলবায়ু সংকটের সমাধান নিয়ে আসা। আমেরিকায় ‘ইকোক্রিটিসিজম’ মূলত: ‘নন ফিকশন’ জাতীয় লেখাপত্রের সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। তাই বলে সর্বত্র এরকমটা হয়নি, কোথাও কোথাও কবিতার মাধ্যমে ‘ইকোক্রিটিসিজমে’র চর্চা হয়েছে। জোনাথান বেট তাঁর ‘Romantic Ecology: Wordsworth and the environmental tradition’ (১৯৯১) এবং ‘The song of Earth’ (২০০০) বইতে রোমান্টিক কবি হিসাবে পরিচিত উইলিয়াম ওয়ার্ডসওয়ার্থকে ‘প্রকৃতির কবি’ তথা ‘Poet of nature’ অভিধায় ভূষিত করেন। ফলে ‘ইকোক্রিটিসিজম’কে আগে রোমান্টিকতায়, বন্য আখ্যান (Wild narrative) সহ নানা প্রকৃতিকেন্দ্রিক লেখালেখি দিয়ে বিশেষিত করা হত। বলতে বাধা থাকেনা যে এই পর্বে ‘Nature’ বা ‘প্রকৃতি’ মানব বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতোই এক ‘romanticised idea’ বা ‘ধ্যান’ হয়ে থেকে যায়।
প্রায় কাছাকাছি সময়পর্বে আরো এক গোষ্ঠীর ‘ইকোলজিস্ট’ আমাদের অতিপরিচিত প্রিয় গ্রহ ‘পৃথিবী’তে মানুষ-প্রকৃতির অবস্থানের পুনর্বিবেচনার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। তাঁরা ‘ইকো’কেন্দ্রিক দৃষ্টিভঙ্গি সমর্থিত ‘বায়োস্ফিয়ারিক্যাল সমতাবাদ’কে গ্রহণ করলেন। এখানে আর এককের স্বার্থ না, বরং সমগ্র বায়োস্ফিয়ারের স্বার্থ সমর্থিত হল। নিজের গভীর ‘আত্ম’কে পরিবেশের সঙ্গে এমনভাবে যুক্ত করতে চাইলেন যাতে পরিবেশ সচেতনতা স্বতঃস্ফূর্ত নৈতিকতার অংশ হয়ে ওঠে। প্রাকৃতিক বিশ্ব আধুনিক মানব সভ্যতার ‘সম্পদ’ (Resource), ইচ্ছে মতো ভোগের অধিকার মানুষের আছে- এই আধিপত্যবাদী দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি চ্যালেঞ্জ তৈরি হল। আমরা, তথাকথিত সভ্যতাধারী মানুষেরা যে বৃহৎ ‘জীবন চক্রে’র (Life circle) অন্তর্ভুক্ত, আমাদের সংসার শুধু আমাদের নিজেদের নিয়ে নয়- চিন্তার পরিধি ব্যস এতদূর বাড়াতে পারলেই প্রাকৃতিক বিশ্বের প্রতি আচরণগত বিপুল পরিবর্তন ঘটানো সম্ভব; আমরা আদপেই এক বৃহত্তর বৃত্তের অন্তর্গত। সামাজিক পরিবেশবিদরা (social environmentalist) বিশ্বাস করলেন ও করালেন যে প্রকৃতির উপর মানুষের আধিপত্য লাভের ধারণাটি মানুষ কর্তৃক মানুষের উপর মানুষের আধিপত্য বিস্তারের পরিস্থিতি থেকে উদ্ভূত। এখানেই ‘ইকোক্রিটিসিজমে’র দ্বিতীয় তরঙ্গের যৌক্তিকতা। পন্ডিতেরা (literary scholars) বুঝতে শুরু করলেন প্রথম তরঙ্গে প্রকৃতিকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি আধুনিক জীবনের জায়মান পরিবেশগত সমস্যা ও সংকটের সমাধানগত আলোচনায় অক্ষম। ফলে তাঁরা ‘পরিবেশ’- এই পরিভাষাটির পরিসীমাকেই বর্ধিত করলেন; মানুষ ছাড়াও অপরাপর প্রাণ, এমনকি অজৈব উপাদানও এই বৃত্তেরই। বাস্তুতন্ত্রে (Ecology) সমাজকে অন্তর্ভুক্ত করার অর্থ হচ্ছে সমাজ দ্বারা পরিবেশের প্রভাবিত, বলা ভালো ক্ষতি হওয়ার সমস্যাটি উত্থাপিত হচ্ছে। জলবায়ু পরিবর্তনের উদগাতা রূপে মানুষের ভূমিকাকে স্বীকার না করলে ‘ইকোক্রিটিসিজম’ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বদলে যাওয়া অভ্যাস ও ক্রমবিবর্তিত সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া আর পণ্যের বিস্তৃত পরিসরে মনোযোগ এসে পড়েছে, যেখানে ও যার মাধ্যমে প্রকৃতি আর সংস্কৃতির জটিল আলোচনা সংঘটিত। চেরিল গ্লটফেল্টি তাঁর বইতে ১৯৯৬ তে বলেন- শ্রেণি, লিঙ্গ বৈষম্য বিশ শতকের সবচেয়ে চর্চিত বিষয়; কিন্তু আমরা জানতে পারিনি যে আমাদের পৃথিবীর লাইফ সাপোর্ট সিস্টেমটাই সঙ্কটাপন্ন। আমরা আসলে ভেবেই দেখিনি যে আমাদের এই ভোগ, ভোক্তা, উৎপাদন, উদ্যোক্তা ও প্রযুক্তির বাইরে পৃথিবী বলে কিছু আছে। প্রথম তরঙ্গ থেকে দ্বিতীয় তরঙ্গে ‘ইকোক্রিটিসিজম’ ও পরিবেশচিন্তার ফোকাসের কিছু পরিবর্তন হল। একটি গুরুত্বপূর্ণ সুবিধা হল এই যে, পরিবেশগত সমালোচনা পরিবেশগত সমস্যাগুলিকে উপস্থাপন করার জন্য নির্দেশিত হল। এরই উত্তরাধিকারে একবিংশ শতাব্দীতে ‘ইকোক্রিটিসিজমে’র একটি বাস্তব সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা বজায় রইল।
লরেন্স বুয়েল নিজে ‘ইকোক্রিটিসিজম’ তরঙ্গের প্রবক্তা হলেও তরঙ্গগুলি সম্পর্কে তাঁর মন্তব্য ছিল যে সাহিত্যের অধ্যয়নে পরিবেশগত সমালোচনার কোনো নির্দিষ্ট মানচিত্র সম্ভব না। তবুও ‘ইকোক্রিটিসিজমে’র প্রথম তরঙ্গ থেকে দ্বিতীয় বা নতুনতর সংশোধনবাদী তরঙ্গে বিবর্তনকে চিহ্নিত করে বেশ কয়েকটি প্রবণতা-রেখা নির্দেশ করা যেতে পারে।
“No definitive map of environmental criticism in literary studies can be drawn. Still, one can identify several trend-lines marking an evolution from a ‘first wave’ of ecocriticism to a ‘second’ or newer revisionist wave or waves increasingly evident today. This first-second wave distinction should not, however, be taken as implying a tidy, distinct succession. Most currents set in motion by early ecocriticism continue to run strong, and most forms of second-wave revisionism involve building on as well as quarreling with precursors.” (‘Future of ecocriticism’, 17)
অনেকে এমন যুক্তিও দেন যে দ্বিতীয় তরঙ্গ নারীবাদী চিন্তার গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ নিসর্গ নারীবাদকে যথাযথ মূল্য দেয়নি। এখন বুয়েলীয় বক্তব্য অনুসারে ‘ইকোক্রিটিসিজমে’র দ্বিতীয় তরঙ্গটি পরিবেশ-সমালোচনাকে সংশোধিত করেছিল বটে, তবে এটি প্রথম তরঙ্গের উপাদানগুলির মধ্য দিয়েই প্রবাহিত হয়েছিল।
পর্ব – ১৪
ইকোফেমিনিজম : পর্ব এক
“Eco-feminism is a recent development in feminist thought which argues that the current global environmental crisis is a predictable outcom of patriarchal culture.”
-Ariel Salleh, অষ্ট্রেলিয়ান সমাজবিজ্ঞানী
প্রথমে ছিল কৃষি উৎপাদনের শান্তিপূর্ণ মাতৃতান্ত্রিক যুগ, খৃঃপূঃ ৪৫০০ বছর আগে ইউরেশিয়া থেকে যাযাবর জাতির ইন্দো-ইউরোপীয় অঞ্চলগুলিতে অভিযান চালানোর সময় থেকেই প্রকৃতি ও নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্যের সূত্রপাত হয়, তথা কৃষিযুগের শেষ বা বলা ভালো কৃষি-জমি অধিকারের যুগ শুরু। শিল্পবিপ্লবের সময় থেকেই আসলে পুরনো পৃথিবীর ধ্যান-ধারণা পাল্টে গিয়ে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের সম্পৃক্ততার সম্পর্ক বিচ্ছিন্নতার সম্পর্কে মোড় নেয়। জন্ম হয় যুক্তিবাদী যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি ও আধুনিক বিজ্ঞানের।
মানবী নিসর্গবাদ বা ‘Eco feminism’ পরিভাষাটি ১৯৭৪ সালে প্রথম ব্যবহার করেন ফ্রাঁসোয়া দ্য ওবোন (Françoise d’Eaubonne, ১৯২০-২০০৫)। এই দর্শনের ধারণাটি মূলধারায় আসে ১৯৮৭ সালে ইকোফেমিনিস্ট ইনেস্ত্রা কিং (Ynestra King) রচিত একটি নিবন্ধ ‘What is Ecofeminism?’-এর মাধ্যমে। এই মতবাদে বিশ্বাসীরা আসলে মিথোজীবীতা বা ‘সিম্বায়োটিক রিলেশনশিপ’- এর ওপর ভরসা করেন। মূলতঃ নিসর্গ ন্যায়ের সমস্যামূলক অবস্থান থেকেই নিসর্গনীতি, যেখানে মনে করা হয় প্রকৃতি-মানুষ ও নারী-পুরুষের কোনো এক পক্ষ দুর্বল হলে অপর পক্ষ তার উপরে আধিপত্যমূলক শাসন চালাবেনা। এমনকি কোনো এক পক্ষের মতামত অপর পক্ষকে নির্বিশেষে পরিচালনা করবে না। অর্থাৎ প্রতিষিঠত সামাজিক বিন্যাসকে অন্যভাবে, বলা ভালো নতুনভাবে পারষ্পরিকতার সম্পর্কে সাজাতে বলা হয় এখানে। কোনো একাধিপত্যের বদলে স্থান পাবে বহুত্ববাদ (Pluralism) ও সাম্য। নিসর্গ নারীবাদে সমাজকে অস্বীকার করা হয়নি, বরং মানুষের সাথে প্রকৃতির প্রয়োজনের সম্পর্ককে সামাজিক নির্মাণের ফসল বলে স্বীকার করে নেওয়া আছে। সমাজের বদল ঘটানোতে, আসলে বিপল্প দৃষ্টিভঙ্গি নির্মাণে বিশ্বাস স্থাপনের কথা পাই। ‘ইকোফেমিনিজমে’র দর্শন কতকগুলি নৈতিকতার অনুশীলনে গুরুত্ব আরোপ করে-

প্রথমত, মানবী ও প্রকৃতির পারস্পরিক সম্পর্ককে নিয়ে কোনো কাব্য বা রহস্যময় আবরণ তৈরি করা নয়, বরং তাকে দৃশ্যায়িত করে তোলা। নারী ও প্রকৃতি উভয়কেই যে কোনো রকম আধিপত্যবাদ থেকে মুক্তি পেতে হবে। ‘ওম্যান-নেচার’ (woman-nature) সম্পর্কই ইকোফেমিনিজমের মূল ভিত্তি।
দ্বিতীয়ত, পারস্পরিক প্রভেদ থাকলেও বিসম আচরণ থেকে নিবৃত্ত থাকার অনুশীলন,
তৃতীয়ত, নব সামাজিক বিন্যাসের চাহিদা থেকেই (ধ্বংস ও সামাজিক পচনশীলতার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে) শীল ও চর্যার অনুশীলন। মানবিক নানা গুণাবলি, যেমন- ‘সম’ আচরণ করা, দুর্বলের প্রতি নিপীড়নের সমাপ্তি ঘটিয়ে দরদপূর্ণ মনোভাবের চর্চা করা ইত্যাদি। আমাদের যাকিছু মানবিক মূল্যবোধ, তাকে লিঙ্গ নিরপেক্ষ করতে হবে। অর্থাৎ উত্তরাধিকার সূত্রে আমরা লাভ করেছিলাম কিন্তু শিল্পবিপ্লব ও পুঁজিবাদ আমাদের সরল সাধারণ জীবন থেকে কেড়ে নিয়েছে। এর ফলে ব্যক্তিত্বকেও নতুনভাবে গড়ে তোলা সম্ভব যেহেতু ব্যক্তিত্ব জন্মদত্ত নয়, সৃজিত।
মানবী নিসর্গবাদ অনুযায়ী প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সম্পর্কের একটি দীর্ঘ ইতিহাস আছে, যা পুরুষ (বা ক্ষমতা) নিয়ন্ত্রিত সমাজের ইতিহাস। এই ইতিহাস বিশ্লেষণ করলে প্রকৃতির সঙ্গে নারীর সমার্থক ‘আইডেন্টিটি’ বোঝা সম্ভব৷ পরিবেশবিদ বন্দনা শিবার মতে- “Eco feminism is to redifine how societies look at productivity and activity of both women and nature who have mistakenly been deemed passive, allowing for them be ill-used.”
তৃতীয় বিশ্বের মানুষের শ্রম, ঘাম, রক্ত ও প্রাকৃতিক সম্পদ লুঠ করে প্রথম দুনিয়ার একনায়কতান্ত্রিক বিশ্ব ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে- এই ভাবনায় প্রাকৃতিক বিপর্যয় ও নারীর অবমূল্যায়ন পরস্পরের সমার্থক হয়ে যায়। পণ্য ও পুঁজিবাদ প্রভাবিত সমাজ কিভাবে দেখে প্রাকৃতিক উর্বরাশক্তি ও নারীর উৎপাদন ক্ষমতাকে, যে নদীর জল বিদ্যুৎ উৎপাদনে তেমন কাজে লাগানো যায়নি, যে অরণ্যের সম্পদ বিদেশে রপ্তানি করে ‘ডলার’ উপার্জন করা যায়নি, তার গুরুত্বকে? নতুন দৃষ্টিভঙ্গীতে বোঝা শুরু হল সেসব। যায়নি, সেই অরণ্য ও নদীর কোনো মূল্য নেই। রিলায়েন্স কোম্পানি শীততাপ নিয়ন্ত্রিত শপিং মলে শাকসব্জির জোগান বাড়াতে ‘রিটেইল শপ’ খুলতে চলেছে। ফলে চাষযোগ্য জমির ফসল হচ্ছে ‘রিলায়েন্স’ নামক কোম্পানির, জন্ম নিচ্ছে অদৃশ্য মালিক। কোম্পানি নির্দিষ্ট করে দেবে নির্দিষ্ট পরিমাণ ফসল ফলাতে কতজন শ্রমিক চাষী লাগবে, এবং অবশ্যই সেখানে ছেলে চাষি অগ্রাধিকার পাবে ছাঁটাই পড়বে মেয়েরা। কোম্পানি নির্দিষ্ট সারে জমির বিপুল ক্ষতি হতে থাকে। জলের ধারা বেঁধে শিল্প ও পণ্য-পুঁজির কাজে লাগানোয় ক্ষতিগ্রস্ত হয় নদীর আশেপাশে থাকা অভাবী মানুষেরা বা অরণ্যচারী সম্প্রদায়গুলি;বিশেষত পরিবারের মেয়েরা। কেননা ঘরে-সংসারে জলের যোগান তাদেরই দিতে হয়, খাদ্য সরবরাহের দায়ও তাদেরই।
প্রথম বিশ্বের উন্নয়ন ও শিল্পায়ন সম্পর্কিত নানা নীতিসমূহের ফলে নারীরাই ক্ষতিগ্রস্ত হয় সবচেয়ে বেশি। আর প্রাচীনকালে আদিম মানুষের যা কিছু সাংস্কৃতিক ও আধ্যাত্মিক ধ্যান-ধারণা গড়ে উঠেছিল, সেই সবই নারীদের সঙ্গে প্রকৃতির সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে নির্মিত। পুঁজি ও পণ্য তাকে আঘাত করলে যে সংকটের সৃষ্টি হয়, তার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ফেলে আসা চর্যার নিরিখে সমাজের নববিন্যাসের উদ্দেশ্য নিহিত থাকে। এখানেই চর্চা করতে হয় ‘ইকোফেমিনিজম’-এর-
“Ecofeminism is then presented os as offering alternative Spiritual symbols (e.g- Gaia, os goddess symbols), spiritualities, theo logies & even utopian Societies.”
-J. Waren
‘লিবারেল ফেমিনিজম’-এ (Liberal Feminism) প্রকৃতি আধিপত্যবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার চোখে কল্পিত। আবার ‘মার্ক্সিস্ট ফেমিনিজম’-এ (Marxist Feminism) নারী নিপীড়নকে শ্রেণী নিপীড়নের দৃষ্টিতে বিচার করা হয়। মানুষের প্রয়োজন মেটাতে আধুনিক পুঁজিবাদের যে গতিশীল চরিত্র, তা প্রকৃতিকে দোহন করেই সম্ভব হয়েছে। আবার ‘র্যাডিকাল নারীবাদ’ (Radical Feminism) নারী ও প্রকৃতির উপর অত্যাচারের মূল সূত্র খুঁজে পায় প্রজনন জীববিজ্ঞান ও যৌন-লিঙ্গ ব্যবস্থায় (Reproductive biology and Sex gender system)। নারীর সমস্যাকে পরিবেশ সমস্যার অন্তর্ভুক্ত করে নিলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হয়। নারী-নিপীড়ন ও প্রকৃতি-ধ্বংস একই মুদ্রার এপিঠ ওপিঠ। জৈবিক চাহিদা মেটাতে নারী দেহের উপর চাপ সৃষ্টি, উত্তরাধুনিক সমাজের চাহিদা পূরণে প্রকৃতি আর তার উপাদানের অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আর নারী-প্রকৃতির স্ব অধিকারে মুক্তির দাবি নারী নিসর্গবাদী ভাবনায় ত্রিবেণী সঙ্গম ঘটায়। ‘ইকোফেমিনিজম’-এর একটি মৌলিক সমস্যার সঙ্গে বহুস্তরীয় বিন্যাস যুক্ত হয়ে যায়, ক্ষমতা-অত্যাচার-শোষণ ও প্রকৃতি-নারী-তৃতীয় বিশ্ব।
পর্ব – ১৫
ইকোফেমিনিজম : পর্ব দুই
ইকোফেমিনিস্ট পরিচয়
১৯৭৭ সালে প্রফেসর ওয়াংগারি মাথাই-এর নেতৃত্বে কেনিয়ার ‘গ্রিন বেল্ট’ আন্দোলনে নারীরা একত্রিত হয়েছিল, উদ্দেশ্য বৃক্ষ রোপণ এবং ক্ষয়প্রাপ্ত জমি পুনরুজ্জীবিত করা। ভারতের উত্তরাখণ্ডে চিপকো আন্দোলনে স্থানীয় গ্রামবাসীরা তাদের অরণ্যসম্পদ রক্ষা করেছিল অসাধু ব্যবসায়ীদের নীতি বর্জিত ব্যবসার হাত থেকে। কানাডিয়ান মহিলারা তাদের শহরের কাছাকাছি এলাকায় ইউরেনিয়াম প্রক্রিয়াকরণ ইউনিট থাকার বিরুদ্ধে প্রচার ও প্রতিবাদ চালায়। এঁরা সকলেই ‘ইকোফেমিনিস্ট’, আবার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গৃহিণীরা বিপজ্জনক বর্জ্য স্থানগুলি পরিষ্কার করে ‘ইকোফেমিনিস্ট’ হিসেবে পরিচিত হন। কারণ উল্লেখিত নারীরা পৃথিবীতে জীবনচক্রের ধারাবাহিকতাকে সুস্থ রাখার জন্য নিবেদিত। যখনই নারীরা পরিবেশগত অবনমন, পারমাণবিক ধ্বংস, জৈবপ্রযুক্তি, জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এবং প্রজনন প্রযুক্তির উন্নয়নের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেছে, তারা ক্ষমতার আধিপত্যজনিত লালসা এবং নারীর (প্রকৃতির) প্রতি সহিংসক মানসিকতার মধ্যে সংযোগ আবিষ্কার করেছে। ‘Ecofeminism at the crossroads in India’ বইতে লেখিকা মনীষা রাও লিখেছেন- “they discovered the connections between patriarchal domination and violence against women, the colonized non-western, non-White peoples and nature. It led to the realization that the liberation of women cannot be achieved in isolation from the larger struggle for preserving nature and life on earth.”
প্রসঙ্গক্রমে বলা জরুরি যে নিসর্গ-নারীবাদের মতাদর্শে বিশ্বাসী পুরুষও একজন ‘ইকোফেমিনিস্ট’ বিবেচিত হতে পারেন। রাজস্থানের শ্যাম সুন্দর পালিওয়াল ‘নিসর্গ-নারীবাদের জনক’ নামে পরিচিত। ২০০৬ সালে জলের অভাবে কন্যাসন্তান হারান, কারণ তাঁর গ্রামে ভূগর্ভস্থ জলের স্তর সাতশো মিটারেরও নিচে নেমেছিল। এরপর থেকে গ্রামে প্রতিবার মেয়ে শিশুর জন্ম হলে গাছের চারা রোপণ করেন তিনি।
ভেনেসা নাকাতে উগান্ডার ‘ক্লাইমেট জাস্টিস্ এক্টিভিস্ট’। উগান্ডায় হঠাৎই তাপমাত্রার মাত্রাতিরিক্ত বৃদ্ধির কারণে ভেনেসা পরিবেশ বিষয়ক আন্দোলন সক্রিয়ভাবে শুরু করে ২০১৮ সালে। পরিবেশবাদী কর্মী গ্রেটা থুনবার্গের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে ভেনেসা, জলবায়ু সংক্রান্ত সমস্যায় রাষ্ট্রের তথা সরকারের কোনো ভূমিকা না নেওয়ার বিরুদ্ধে পার্লামেন্ট গেটের বাইরে সরব হয় জানুয়ারি ২০১৯-এ। সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করে সে সমবয়সীদের কঙ্গোলিয়ান রেইন ফরেস্টের দুর্দশার দিকে দৃষ্টি ফেরানোর আর্জি জানিয়েছে। সে ‘ইয়ুথ ফর ফিউচার আফ্রিকা’ ও ‘রাইজ আপ মুভমেন্ট’ প্রতিষ্ঠা করে। ২০২০ সালের জানুয়ারিতে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের কুড়ি জন যুব জলবায়ু কর্মীদের সাথে যোগ দেয় ও ‘ওয়ার্ল্ড ইকোনমিক ফোরাম’- এর সদস্যদের উদ্দেশ্যে খোলা চিঠি লেখে ব্যাঙ্ক, সরকারকে জীবাশ্ম জ্বালানির ভর্তুকি বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে। অক্টোবর, ২০২০ সালে আন্তর্জাতিক শান্তি সম্মেলনে ভেনেসা জলবায়ু পরিবর্তনের সঙ্কটকে মেয়েদের প্রতি সংঘাত, সহিংসতার সাথে সম্পর্কিত করে চিহ্নিত করে। তার বক্তব্য ছিল যে জলবায়ু পরিবর্তন এক দুঃস্বপ্ন যা আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেএকে প্রভাবিত করে, এই সংকটের দিকে না তাকিয়ে কি ভাবে আমরা দারিদ্র্য বিমোচন করতে পারি? কি করে আমরা ‘শূন্য ক্ষুধার্তে’র লক্ষ্যসীমায় পৌঁছাতে পারি যখন জলবায়ু পরিবর্তন লক্ষ মানুষকে না খাইয়ে রাখছে! সে ‘গ্রিন স্কুল প্রকল্প’ শুরু করে, যা নবীকরণযোগ্য জ্বালানির উদ্যোগ নেয়। এর লক্ষ্য উগান্ডার স্কুলে সৌরশক্তির ব্যবহার ও পরিবেশ বান্ধব চুলা বসানো।
সুইডেনের পরিবেশবাদী আন্দোলনকারী গ্রেটা থুনবার্গের সক্রিয়তার শুরু তার পরিবারবর্গের জীবনশৈলীগত কিছু পরিবর্তনমূলক পছন্দের মাধ্যমে। তারা ব্যক্তিগত জীবনশৈলীর জন্য ‘কার্বন ফুট প্রিন্টে’ গ্রিনহাউস গ্যাসের নিঃসরণের পরিমাণ কমাতে উদ্যোগী হয়। ২০১৮, আগস্ট মাসে ১৫ বছর বয়সী গ্রেটা জলবায়ুর জন্য স্কুল ধর্মঘট করে। জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে দৃঢ় পদক্ষেপ নেওয়ার আহ্বান জানিয়ে সুইডেনের সংসদের বাইরে স্কুলের দিনগুলো কাটাতে শুরু করে। এরই অনুকরণে ‘ফ্রাইডে ফর ফিউচার’ নামে স্কুল জলবায়ু ধর্মঘট আন্দোলন আকারে শুরু হয়। ‘ইউনাইটেড নেশন ক্লাইমেট চেঞ্জ কনফারেন্স’, ২০১৮-তে বক্তৃতার পরে বিশ্বের কোন না কোন জায়গায় প্রতি সপ্তাহে ছাত্র ধর্মঘট হতে থাকে। আমেরিকান পরিবেশবাদী কর্মী মার্টিনেজ ‘আর্থ গার্ডিয়ান’ (১৯৯২) নামক পরিবেশ সংরক্ষণমূলক সংগঠনের কর্মী এবং ডিরেক্টর৷ আদিবাসী ও অন্যান্য প্রান্তিক সম্প্রদায়ের উপর জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ক্ষতিকর প্রভাব সম্পর্কে মার্টিনেজ স্বর তুলেছে। মিচিগানের সক্রিয় পরিবেশ আন্দোলনকারী আমেরিয়ানা কোপেনি জল সংকটের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে।
ভারতীয় পরিসরে পরিবেশ চর্চা ও গবেষণার কেন্দ্র ‘সেন্টার ফর সায়েন্স এন্ড এনভারমেন্ট’-এর পরিচালক সুনীতা নারাইন। তিনি দিল্লিতে পরিবেশবাদী পত্রিকা চালানোর পাশাপাশি ‘সোসাইটি ফর এনভায়রনমেন্টাল কমিউনিকেশনে’র প্রবর্তক। পরিবেশ নারীবাদের অন্যতম প্রবক্তা, বিশ্বায়ন বিরোধী লেখিকা এবং আন্দোলনকারী বন্দনা শিবা (১৯৫২) কৃষিক্ষেত্রে বীজের উৎপাদন ক্ষমতা বৃদ্ধি, শস্য বৈচিত্র্য বৃদ্ধি, পুষ্টি বৃদ্ধি ও কৃষকের অধিকার নিয়ে কাজ করেন। তাঁর মতে সবুজ বিপ্লবের ফলে রাসায়নিক সার ও কীটনাশক প্রয়োগে বীজের প্রাকৃতিক উৎপাদন ক্ষমতা, শস্যের প্রাকৃতিক পুষ্টি উভয়ই নষ্ট হয়েছে। এমন কি শস্যের মধ্যে থাকা বিবিধ কীটনাশক খাদ্যের মাধ্যমে শরীরে প্রবেশ করে বিপুল ক্ষতি করতে পারে, এই বিষয়েও সচেতনতা তৈরি করেন। জলবায়ু নিরাপত্তার স্বার্থে তিনি ‘ওয়ার্ল্ড ফিউচার কাউন্সিল’ তৈরি করেছেন। ‘ইকোফেমিনিস্ট’ বন্দনা শিবা ও মারিয়া মায়েজ উভয়েই উপনিবেশবাদ, পুঁজিবাদ সহায়ক বিজ্ঞানের সমালোচনা করেছেন। সভ্যতা ‘আধুনিকতা’র বৈশিষ্ট্যকে যত আত্তীকরণ করেছে, বৈশ্বিক প্রকৃতির সবকিছুকে দেখার বস্তুবাদী দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট হয়েছে। এমনকি ‘ক্ষমতা’ সুবিধা মতো আধুনিক বিজ্ঞান ও তার যুক্তিকে স্বার্থপূরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করেছে। বন্দনা শিবার মতে- “we name ‘science’ what is mechanistic and reductionist”
দশোলি গ্রামের চন্ডীপ্রসাদ ভাট (১৯৩৪), সুন্দরলাল বহুগুণা (১৯২৭), তাঁর স্ত্রী বিমলা বহুগণা পরিবেশবাদে বিশ্বাসীদের পরিচিত মুখ। সুন্দরলাল হিমালয়ের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণ, তেহরি ড্যাম মুভমেন্টে যুক্ত ছিলেন। কেরালার ইকোফেমিনিস্ট সুগাথা কুমারী, ঝাড়খণ্ডের দয়ামনি বাড়লা প্রমুখ প্রকৃতি আর প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য নীতিগত লড়াই লড়ে গেছেন। আসামের মাজুলি দ্বীপের বাসিন্দা যাদব পায়েঙ (১৯৬৩) তো ভারতের জঙ্গল মানব নামে পরিচিত। ইনি ব্রহ্মপুত্র নদীর তীরে প্রায় ১৩৬০ একর জায়গা জুড়ে প্রচুর গাছ লাগিয়ে অরণ্য সৃজন করেন। মনে করব পাঞ্জাবের ভগৎ পূরণ সিং-এর কথা, যিনি পুনর্বব্যবহারযোগ্য কাগজে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে গণসচেতনতা বর্ধক বিভিন্ন বিষয়ে প্যাম্ফলেট লিখতেন।
ইকোফেমিনিস্টরা কার্যত এমন কিছু পরিবেশগত নীতির পক্ষে কথা বলেন যা নারী ও প্রকৃতির উপর যুগপৎ আধিপত্য, নিপীড়নের মোকাবিলা করে যত্ন এবং লালন-পালনের নৈতিকতাকে আশ্রয় করে। এই নীতি নারীরা অর্জন করে তাদের সাংস্কৃতিকভাবে নির্মিত অভিজ্ঞতা (Culturally constructed experience) থেকে। দার্শনিক কারেন ওয়ারেন যেমন ধারণা করেছেন- “An ecofeminist ethic is both a critique of male domination of both women and nature and an attempt to frame an ethic free of male-gender bias about women and nature. It not only recognizes the multiple voices of women, located differently by race, class, age, [and] ethnic considerations, it centralizes those voices.” এই আদর্শে বিশ্বাস করা হয় ‘সমতা’র ভাবনায়। কোনোরকম আধিপত্যবাদী ক্ষমতার সম্পর্কের বিন্যাস ব্যতিরেকে লিঙ্গ, জাতি, শ্রেণি নির্বিশেষে মানুষ স্থান-সময়-যত্নের পারস্পরিক বিনিময় ঘটাবে। তেমনি মানুষ আর প্রকৃতির সহাবস্থান জরুরি, যেখানে প্রকৃতিও একইভাবে স্থান-সময় আর যথাযথ পরিচর্যায় বিকশিত হতে পারে ও পুনরুৎপাদনে সক্ষম হয়।
পর্ব – ১৬
পরিবেশ আন্দোলন : পর্ব এক
‘পরিবেশ আন্দোলন’ পরিভাষাটি উন্নয়নের বৃহত্তর প্রেক্ষাপটে জীবিকার সমস্যা এবং পরিবেশগত নিরাপত্তার সাথে সম্পর্কিত বিভিন্ন ধরনের স্থানীয় সংগ্রাম-আন্দোলনকে বোঝার জন্য ব্যবহৃত হয়। এই আন্দোলনগুলি প্রকৃতপক্ষে ঔপনিবেশিক সময় থেকে ভারতীয় রাষ্ট্র এবং এর কর্মকর্তাদের দ্বারা অনুসৃত উন্নয়ন এবং সংরক্ষণমূলক বাস্তুবিদ্যার (Conservation Ecology) ধারণা, নীতির প্রতি সমালোচনা এবং প্রশ্ন তুলেছিল। ভারতের পরিবেশ আন্দোলনের সূত্রপাত উত্তরাঞ্চলের গাড়ওয়াল এলাকার চিপকো আন্দোলন (১৯৭৩) থেকে। প্রকৃতপক্ষে, ১৯৭০ থেকে ১৯৮০-এর মধ্যে ভারতে বন ও জলের অধিকার কেন্দ্রিক বেশ কয়েকটি আন্দোলন হয়েছিল যা বন সম্পদে উপজাতিগুলির অধিকার, বাঁধের মতো বৃহত্তর পরিবেশগত প্রকল্পের স্থায়িত্ব, বাস্তুচ্যুতি এবং পুনর্বাসনের সমস্যার মতো বৃহত্তর পরিবেশগত উদ্বেগের দিক উত্থাপন করেছিল।
ভারতীয় পরিবেশ আন্দোলন উত্তর-ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র দ্বারা অনুসৃত উন্নয়নের ঔপনিবেশিক মডেলের সমালোচনা করে। জনগণের চাহিদার উপর ভিত্তি করে স্বাধীনতা পরবর্তী রাষ্ট্র একটি স্থায়ী উন্নয়ন পরিকল্পনা তৈরি করতে ব্যর্থ হয়। পরিবর্তে আধুনিক পুঁজিবাদী পরিকাঠামো ও বিষয়সূচি পরিকল্পনার পরিপোষণ পরিবেশ ধ্বংস, দারিদ্র্য এবং গ্রামীণ জনগোষ্ঠীকে প্রান্তিকতার দিকে পরিচালিত করে। জাতীয় উদ্যান, অভয়ারণ্য, সংরক্ষিত এলাকা গঠনে ভারতে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য বজায় রাখার স্বার্থ নিহিত ছিল। কিন্তু এই নির্দিষ্ট এলাকার পরিসীমা থেকে জনজীবনকে দূরে ঠেলে দেওয়া হয়েছিল। এর প্রতিক্রিয়ায় ভারতের পরিবেশবাদী আন্দোলনগুলি প্রাকৃতিক পরিবেশে জনসাধারণের অধিকার ও পারস্পারিকতার সম্পর্কের সপক্ষে প্রতিনিধিত্ব করে। পরিবেশ আন্দোলনগুলি শুধুমাত্র আধুনিক উন্নয়নবাদের সমালোচনাই করেনা বরং প্রথাগত ‘স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রাম অর্থনীতি’র পুনরুজ্জীবনের পক্ষেও জোরালোভাবে সমর্থন দেখায়। এতে পরিবেশলগ্ন সম্প্রদায়গুলি ভারতীয় পরিবেশগত আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে এসেছে। পরিবেশবিদদের মতে, স্থানীয় (বিভিন্ন উপজাতি) সম্প্রদায়গুলি প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণে সবচেয়ে উপযুক্ত ভূমিকা গ্রহণ করে, যেহেতু তাদের বেঁচে থাকা এই সহায় সম্বলের সহনশীল ব্যবহারের উপর নির্ভর করে। একভাবে বলতে গেলে তাদের দৈনন্দিন পারস্পরিক সম্পর্কই স্থানীয় পরিবেশের রক্ষক। পরিবেশ আন্দোলনগুলি প্রাকৃতিক সম্পদের প্রাপ্যতা ও ব্যবহারে জনসাধারণের প্রথাগত অধিকার বা ঐতিহ্যগত অধিকারগুলি (যা কেড়ে নেওয়া হয়েছিল) ফিরিয়ে দেওয়ার সঙ্গে সম্পর্কিত।
পশ্চিমী ধারার বিপরীতে, ভারতে পরিবেশ আন্দোলনের উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যই হল এই যে তারা প্রধানত নারী, দরিদ্র এবং সুবিধাবঞ্চিত সেই সমস্ত জনসাধারণকে একত্রিত করতে পেরেছে যারা পরিবেশগত অবক্ষয়ের দ্বারা সরাসরি প্রভাবিত। প্রাথমিকভাবে এই আন্দোলনগুলিকে পরিবেশগত অবক্ষয়ে ক্ষতিগ্রস্ত স্থানীয় সম্প্রদায়ের সংগ্রামের রাজনৈতিক অভিব্যক্তি হিসেবে দেখা যায়।
পরিবেশবিদ মাধব গডগিল এবং রামচন্দ্র গুহ আদর্শ, দৃষ্টিভঙ্গী এবং কৌশলের ভিত্তিতে ভারতে পরিবেশগত আন্দোলনগুলিকে চারটি সূত্রে গ্রথিত করেছেন। প্রথম সূত্রে প্রাকৃতিক সম্পদের মাত্রাতিরিক্ত অপব্যবহার রোধ করার এবং দরিদ্র ও প্রান্তিকদের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার নৈতিক প্রয়োজনীয়তার উপর জোর দেয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে সংগ্রামের মাধ্যমে অনৈতিক ও ঊর্ধ্বতন-অধস্তন, ভোগের সামাজিক ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার প্রয়োজনীয়তা পরিলক্ষিত হয়। তৃতীয় এবং চতুর্থ ক্ষেত্রে, পরিবেশ রক্ষার দায়িত্ব বিষয়ে নতুন সমাজ ও জীবনদর্শনের প্রয়োজনীয়তার পাশাপাশি পুনর্নবীকরণযোগ্য প্রকৃতিজাত বস্তু ও প্রয়োজনীয় প্রযুক্তির ব্যবহারের বিষয়টি আসে। যেমন বিজ্ঞানীদের সচেতনতায় পরিবেশ-বান্ধব কৃষি পদ্ধতির উদ্ভাবন, গ্রাম পর্যায়ে প্রকৃতিলগ্ন সম্প্রদায়ের স্বতঃস্ফূর্ত প্রচেষ্টায় বন রক্ষা ও উক্ত কৃষি পদ্ধতির অনুসরণ।
ভারতে সংঘটিত পরিবেশ আন্দোলনগুলিকে সমস্যা, বিভাগ এবং উদাহরণগুলির ভিত্তিতে বিশ্লেষণ করা যায়-
- অরণ্য ও ভূমি ভিত্তিক পরিবেশ আন্দোলন যে সমস্যা বা ‘ইস্যু’তে কেন্দ্রীভূত-
ক. বনজ সম্পদের প্রাপ্যতা সংক্রান্ত অধিকার,
খ. প্রাকৃতিক সম্পদের অ-বাণিজ্যিক ব্যবহার,
গ. জমির ক্ষয় রোধ
ঘ. সামাজিক ন্যায়বিচার/মানবাধিকার।
যেমন- চিপকো, অ্যাপিকো, সারা দেশের উপজাতি আন্দোলন (উদাহরণস্বরূপ, ঝাড়খণ্ড বা বস্তার ‘বেল্ট’)
- সমুদ্র ও সামুদ্রিক সম্পদ (মৎস্য প্রভৃতি জলজ পালন ও অন্যান্য ‘অ্যাকোয়া কালচার’) কেন্দ্রিক পরিবেশ আন্দোলনের লক্ষ্য
ক. ট্রলিং নিষিদ্ধ করা, চিংড়ি চাষের বাণিজ্যিকীকরণ রোধ করা
খ. সামুদ্রিক সম্পদের সুরক্ষা
গ. উপকূলীয় অঞ্চলে নিয়ম ও ব্যবস্থাপনার বাস্তবায়ন করা।
যেমন- কেরালা, ওড়িশার ঐতিহ্যবাহী মৎস্যজীবীদের জন্য জাতীয় মৎস্যজীবী ফোরাম কাজ করছে কেরালায়, ওড়িশায় চিল্কা বাঁচাও আন্দোলনে।
- শিল্প দূষণ প্রতিরোধী আন্দোলনে
ক. কঠোর পদক্ষেপে দূষণ নিয়ন্ত্রণ ও দূষণ প্রভাবিত ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের ব্যবস্থা করা,
খ. এলাকার ভৌগোলিক অবস্থান, নকশা, স্থানীয় জনগণের জীবিকা সমস্যা বিবেচনা না করেই শিল্পের বেপরোয়া সম্প্রসারণ প্রতিরোধ ইত্যাদি লক্ষ্য অর্জনের সীমা নির্ধারিত থাকে।
ভোপালে জাহিরো গ্যাস মোর্চা, বিহারে গঙ্গা মুক্তি আন্দোলন, কর্ণাটকের হরিহর পলিফাইবার কারখানার বিরুদ্ধে আন্দোলন, মধ্যপ্রদেশের শাহদোল জেলার বিদুষক কারখানা গ্রুপের নেতৃত্বে গোয়ালিয়র রেয়ন কারখানার বিরুদ্ধে সোন নদীর দূষণকে কেন্দ্র করে আন্দোলন; কেরালা শাস্ত্র সাহিত্য পরিষদ (KSSP) দ্বারা কেরালায় চেলিয়ার নদীতে বিষক্রিয়ার বিরুদ্ধে আন্দোলন।
বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প, যেমন- বাঁধ এবং ব্যারাজ প্রকল্প বিরোধী আন্দোলনের লক্ষ্য- গ্রীষ্মমন্ডলীয় অরণ্যের সুরক্ষা, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা, ধস-রোধী পরিকাঠামো তৈরি এবং বাস্তুচ্যুতদের পুনর্বাসন ঘটানো।
মনে করব নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, ‘সায়লেন্ট ভ্যালি মুভমেন্ট’, তেহরি বাঁধ বিরোধী সমিতি কর্তৃক আন্দোলন, কোশি গন্ধক বোধঘাট ও বেদথি: পশ্চিমে ভোপালপত্তনম এবং ইছামপল্লী, দক্ষিণে তুঙ্গভদ্রা, মালাপ্রভা এবং ঘাটপ্রভা প্রজেক্টের কথা। এছাড়া বিদ্যুৎ প্রকল্প ও খনি এলাকাকে কেন্দ্র করে যেসমস্ত আন্দোলন হয়েছে, তার মধ্যে রয়েছে কোয়না হাইড্রো-ইলেকট্রিক প্রজেক্ট প্রভাবিত জন আন্দোলন, দ্যুন উপত্যকার খনি বিরোধী আন্দোলন, ওড়িশার ‘অ্যান্টি-বক্সাইট মাইন মুভমেন্ট’।
রেলওয়ে প্রকল্প, বিমানবন্দর প্রকল্প, সামরিক ঘাঁটি নির্মাণ প্রকল্পে অবৈজ্ঞানিক নির্মাণ ভূ সম্পদের অবনমন ঘটায়। ‘রেইলওয়ে রি-এলাইনমেন্ট অ্যাকশন কমিটি’র প্রতিবাদ, প্রতিরোধ এই সমস্যাকে কেন্দ্র করে। আসাম রেলওয়ে এবং ট্রেডিং কোম্পানির হাত ধরে ১৮৮২ সালে পাটকাই পাহাড় গুঁড়িয়ে কয়লা তোলা শুরু হয়। চলতে থাকে পাহাড় জঙ্গল ধ্বংস করে কয়লা তুলে আনার কালো কারবার। বাড়তে থাকে পরিবেশ দূষণ, কমতে থাকে স্থানীয় আদিবাসীদের জঙ্গলের ওপর অধিকার। ২০০৩ সাল অবধি অনুমোদন ছিল, তারপরেও চলেছে বেআইনিভাবে কয়লা উত্তোলন৷ পশ্চিমবঙ্গের দেউচা-পাচামি, ওড়িশার তালারিয়া জঙ্গলের একাংশে, আসামের সংরক্ষিত বনাঞ্চল দেহিং-পাটকাই সহ নয়া নয়া কয়লাখনি প্রকল্প সহজেই ছাড়পত্র পাচ্ছে। ২০২০ সালের জানুয়ারি মাসে ন্যাশনাল বোর্ড অফ ওয়াইল্ড লাইফ, আসামে হাতিদের জন্য সংরক্ষিত বনাঞ্চলে কয়লা উত্তোলনের ছাড়পত্র দেয় কোল ইন্ডিয়া লিমিটেডকে। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে ‘ট্যুরিজম’ অন্য একটি দিগন্ত খুলেছে। কিন্তু এর কারণে কোনো জীববৈচিত্র্য ও প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ এলাকায় ঘটে থাকে ‘ডিসপ্লেসমেন্ট’, সাংস্কৃতিক পরিবর্তন। কোন দেশের ক’টি অভয়ারণ্য, ন্যাশনাল পার্ক আছে, তার উপরে সেই দেশের পরিবেশ দরদী ইমেজটি নির্ভর করে থাকে। কিন্তু বিনিময় মূল্য কি? মহারাষ্ট্রের ভীমশংকর এলাকায় ‘একজোট’ আন্দোলন, মুম্বইয়ের সঞ্জয় গান্ধী ন্যাশনাল পার্কে শ্রমিক মুক্তি আন্দোলন, হিমাচল বাঁচাও আন্দোলন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।
পর্ব – ১৭
পরিবেশ আন্দোলন : পর্ব দুই
“Many small people, who do many small things in many small places, can change the face of world.” (Berlin wall) তেমনই অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ইচ্ছে, প্রচেষ্টা আর স্বর মিলিত হয়ে পরিবেশ আন্দোলনের জন্ম। আলেকজান্ডার ভন হাম্বল্ট প্রথম পরিবেশবিদ, যিনি ভেনেজুয়েলার জমিতে কেবল একই রকমের শস্য চাষ, শুধুমাত্র অর্থকরী ফসল চাষে ও অনুপযুক্ত সেচ পদ্ধতিতে ভূমির উর্বরতা নষ্ট হওয়ার বিষয়টি বুঝতে পারেন। এমনকি অরণ্য ধ্বংসের নমুনা দেখে পরিবেশ বিপর্যয়ে মানুষের কার্যকলাপের প্রত্যক্ষ ভূমিকা দেখিয়েছিলেন উনিশ শতকের শুরুতেই। সেই দিক থেকে সবচাইতে প্রাচীন পরিবেশবাদী আন্দোলন হলো অষ্টাদশ শতকের শেষ পর্ব থেকে উনিশ শতকের প্রথম পর্বের মধ্যে ঘটে যাওয়া রোমান্টিক আন্দোলন, যা ‘ব্যাক টু নেচার’ নামে পরিচিত। শিল্প বিপ্লব, যুক্তির বাহুল্য এবং প্রকৃতিকে শুষ্ক প্রয়োজনের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখার বিরুদ্ধ প্রতিক্রিয়ায় এই আন্দোলন। বিশ শতকে এসে বায়ুদূষণের সঙ্গে শিল্পজাত রাসায়নিক বর্জ্য, মনুষ্য ব্যবহৃত দ্রব্যের বর্জ্য এসে যুক্ত হয়। ১৮৬৩ সালে ব্রিটেনে প্রথম ‘অ্যালকালি এ্যাক্ট’ নামক পরিবেশবাদী আইন পাশ হয়, অ্যালকালি ইন্সপেক্টর নিযুক্ত হয় বাতাসে মিউরিয়াটিক অ্যাসিড মিশ্রিত হওয়ার মাত্রা নির্ধারণ করতে। উইলিয়াম ব্লেক রিচমন্ড ‘কোল স্মোক অ্যাবেটমেন্ট সোসাইটি’ প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৯৮ সালে। ১৮৬৫ সালে ‘কমন্স প্রেজারভেশন সোসাইটি’ (ব্রিটেন) গঠিত হয় গ্রামীণ সংরক্ষণকে শিল্পায়নের দখলের বিরুদ্ধে দাঁড় করাতে। এবং ১৮৯৪ সালে একটি জাতীয় সংস্থা গঠন করা হয় পরিবেশ সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে, যার নাম ‘ন্যাশনাল ট্রাস্ট ফর প্লেসেস অফ হিস্টরিক ইন্টারেস্ট অর ন্যাচারাল বিউটি’। উনিশ শতকের শেষ দিকে বন্যপ্রাণী সংরক্ষণের জন্য কিছু সোসাইটি গড়ে উঠেছিল, যেমন ‘প্লুমেজ লিগ’ (১৮৮৯)। এই সোসাইটি পোশাকে পাখিদের চামড়া ও পালক ব্যবহার করার বিরুদ্ধে প্রচার চালায়। ১৮৬৯ সাল নাগাদ গ্রেট ব্রিটেনে সামুদ্রিক পাখি সংরক্ষণমূলক অ্যাক্ট চালু হয়। এর দ্বারাই প্রভাবিত হয়েছিল ‘প্লুমেজ লিগ’-এর প্রচারাভিযান।
চিত্র ১.১, ১.২
দ্বিতীয় ছবিতে ইংল্যাণ্ডের ‘লেডি’দের কাছে পাখির পালক যুক্ত ‘হ্যাট’ ব্যবহার বন্ধ করার অনুরোধ সংক্রান্ত বার্তাটি খুব স্পষ্ট।
ভারতের প্রথম পরিবেশ আন্দোলন সম্ভবত অষ্টাদশ শতকের পশ্চিম রাজস্থানের থর মরুভূমির অধিবাসী বিশনয়ীদের আন্দোলন। পরিবেশ সচেতনতা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে এদের অবদান ভারতে প্রথম স্থানের দাবীদার। গুরু জাম্বোজি দ্বারা ১৪৮৫ সালে পশ্চিম রাজস্থানের মারোয়ার প্রান্তরে প্রকৃতির উপাসনামূলক অহিংস সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ১৭০০ সালে অরণ্য ধ্বংসের প্রতিবাদে এই সম্প্রদায় আন্দোলন করে শম্ভুজির নেতৃত্বে। ১৭৩৭ সালে খেজরালি গ্রামে একদল লোক ঢুকে গাছ কাটতে শুরু করলে অমৃতা দেবী ও তাঁর তিন কন্যা এর বিরোধিতা করে। বিশনয়ী ধর্মে সজীব গাছ কাটা ধর্মবিরুদ্ধ। এমনকি মৃতকেও কাঠ দিয়ে না পুড়িয়ে মাটিতে কবর দেওয়া হয়। ১৯৭৩ সালে উত্তরাখণ্ডের চামোলিতে ঠিকাদার কর্তৃক হিমালয়ের গাছ কাটার বিরুদ্ধে সুন্দরলাল বহুগুণা ও চন্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে চিপকো আন্দোলন হয়।
চিত্র ১.৩, গুগল
গাড়োয়ালের অধিবাসী চন্ডীপ্রসাদ ভাটের গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চামোলি জেলায় দশোলি গ্রাম স্বরাজ মন্ডল স্থাপন করা। লক্ষ্য ছিল- হিমালয়ের প্রাকৃতিক সম্বল অরণ্যকে কেন্দ্রে রেখে কাঠ দিয়ে সরঞ্জাম বানানো, রেজিন জোগাড় করা, স্থানীয় কুটির শিল্প স্থাপন প্রভৃতি। অর্থাৎ পুঁজিবাদের মুনাফার উল্টোদিকে স্থানীয় পরিবেশ-প্রকৃতিকে কেন্দ্রে রেখে মানব শ্রম নির্ভর ছোট মাপের কর্মকাণ্ড ও বিকেন্দ্রীভূত স্বনির্ভর জনগোষ্ঠী তৈরি করতে চেয়েছিলেন চণ্ডীপ্রসাদ ভাট। কৃষিকাজ ছাড়া গাড়ওয়ালের যুবকরা জীবিকা নির্বাহ করত সেনাবাহিনীতে যোগদানের মাধ্যমে, কিংবা দিল্লি-দেরাদুনে গিয়ে মজুর হিসেবে খেটে, রাস্তার পাশে খাবারের ঝুপড়িতে কাজ করে। বলা বাহুল্য চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের এই উদ্যোগ যুবক সম্প্রদায়কে স্থানীয় কর্মসংস্থানের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে যুক্ত করতেও সক্ষম ছিল। আমাদের মনে পড়বে ই. এফ শুমাখার (E.F Schumacher) রচিত ‘স্মল ইজ বিউটিফুল’ (১৯৭৩) বইটির কথা, যেখানে পুঁজিবাদ-অর্থনীতির জনপ্রিয় ধারণা ও বিশ্বায়নের ধারণাকে সমালোচনা করা হয়েছে। পাহাড়ের অরণ্য সম্পদ আহরণের ক্ষেত্রে ঠিকাদার ও স্বরাজ মণ্ডলের মধ্যে আদর্শগত লড়াই দেখা দেয়।
১৯৭৩ সালের ২৪ শে এপ্রিল চণ্ডীপ্রসাদ ভাটের নেতৃত্বে দশোলি গ্রাম স্বরাজ মন্ডল এলাহাবাদের একটি সংস্থার গাছ কাটা বন্ধ করে গাছকে ‘চিপকে’ অর্থাৎ জড়িয়ে ধরে। ডিসেম্বর মাসে কিছু দূরের গ্রামে প্রায় একই রকম ভাবে প্রতিরোধ হয়। এরপর ১৯৭৪ সালের ২৬ শে মার্চ চামোলি জেলার রেনি গ্রামের নারীরা গৌড়া দেবীর নেতৃত্বে গাছ জড়িয়ে ধরে হৃষিকেশের ঠিকাদারের গাছ কাটা বন্ধ করে। তখনই চিপকোর সঙ্গে নারী এবং পরিবেশের সম্পর্ক একই সূত্রে গ্রথিত হয়ে যায়। ১৯৭৫ সালে দশ বছরের জন্য রেনি গ্রাম সংলগ্ন অলকানন্দা উপত্যকার প্রায় বারো’শ বর্গ কিলোমিটার এলাকায় বাণিজ্যিকভাবে কাঠ কাটা বন্ধ হয়। ক্রমে উত্তর কাশি, কুমায়ুন অঞ্চলে বনের গাছ কাটা বন কাটার ইজারা দেবার নিলাম বন্ধ করে দেওয়া হয় এই আন্দোলনের অনুপ্রেরণায়। লিলাম বন্ধ করাকে দাবিতে ছাত্র আন্দোলনও শুরু হয় নৈনিতালে এবং একে কেন্দ্র করে এমনকি ১৯৭৭ সালে পুলিশ গুলিও চালায়। এর পাশাপাশি গান্ধীবাদী সুন্দরলাল বহুগুণা পাহাড়ে থেকেই অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলন, মধ্যপান বিরোধী আন্দোলনের নেতৃত্ব দিচ্ছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন সমবায় সংস্থাও। তিনিই চিপকোর স্থানীয় মানুষের জঙ্গল ব্যবহার ও কর্মসংস্থানের অধিকারকে হিমালয়ের পরিবেশ রক্ষার আন্দোলনে রূপান্তরিত করেন। তিনি পাহাড়ের সীমানা ছাড়িয়ে আন্দোলনকে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন দিল্লির কেন্দ্রীয় সরকার কংগ্রেস দলের জাতীয় নেতৃত্বের সামনে। ফলে সুন্দরলাল বহুগুণা হয়ে উঠলেন চিপকো নামের পরিবেশ আন্দোলনের জাতীয় মুখ। ১৯৭৯ সালের ৯ জানুয়ারি তিনি গাছ কাটার বিরুদ্ধে অনশন শুরু করেন ও গ্রেপ্তার হন এবং ৩১শে জানুয়ারি মুক্তি পান। তাঁর অনশনের গুরুত্বপূর্ণ দিক ছিল ১৯৮১ সালে তিনি সমগ্র হিমালয়ের হাজার মিটারের উপরে সম্পূর্ণ গাছ কাটা আইনত বন্ধ করার দাবি তুলেছিলেন। চিপকো আন্দোলন প্রথম পরিবেশ আন্দোলনের রাজনৈতিকভাবে সফল হওয়ার দৃষ্টান্ত নির্মাণ করতে পেরেছিল।
১৯৭৩ সালেই কেরালার চিরসবুজ বৃক্ষরাজির এলাকায় হাইডেল বিদ্যুৎ প্রকল্প স্থাপনের বিরুদ্ধে আন্দোলন হয় এবং ১৯৮৫ সালে সরকার এই এলাকাকে বাধ্যতামূলকভাবে সংরক্ষণের ব্যবস্থা করে। ঝাড়খণ্ডের সিংভূম এলাকার আদিবাসীরা সরকারের ১৯৮২ সালের অরণ্যনীতির বিরুদ্ধে জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলন করেছিল। সরকার বিহারের সিংভূম জেলার (বর্তমানে ঝাড়খণ্ড) প্রাকৃতিক শাল বনকে বাণিজ্যিক সেগুন বাগানে প্রতিস্থাপন করার প্রস্তাব দেয়। এর প্রতিবাদে অরণ্যভূমির আর্থ-সামাজিক অধিকার নিয়ে জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। প্রথমে বিহারে এবং ধীরে ধীরে ঝাড়খণ্ড ও ওড়িশার মতো বিভিন্ন রাজ্যে ছড়িয়ে পড়ে। পরিবেশবাদীরা এই আন্দোলনকে লোভের রাজনৈতিক খেলা হিসেবে দেখেছিলেন। ১৯৮৩ সালে কর্ণাটকের উত্তর কন্নড় এবং শিমোগা জেলায় আপ্পিকো আন্দোলনের আবির্ভাব ঘটে, যার নেতৃত্বে ছিলেন পান্ডুরং হেগদে। অরণ্য ধ্বংসের প্রতিবাদে ও অরণ্য সম্পদের যথাযথ ব্যবহারের দাবিতে, অরণ্যকেন্দ্রিক প্রাচীন জীবিকা সংরক্ষণের লক্ষ্যে এই আন্দোলন সংঘটিত হয়েছিল। ‘আপ্পিকো’ অর্থে আলিঙ্গন করে গাছের প্রতি নিজের স্নেহ প্রকাশ করা। চিপকো আন্দোলনের প্রভাব এই আন্দোলনে স্পষ্ট প্রতিফলিত।
চিত্র ১.৪- আপ্পিকো আন্দোলন, চিত্র ১.৫- জঙ্গল বাঁচাও আন্দোলন
মেধা পাটকরের নেতৃত্বে ১৯৮৫ সালে জলবিদ্যুৎ প্রকল্পের জন্য নর্মদা নদীতে বাঁধ দেওয়ার বিরুদ্ধে গণ আন্দোলন হয়। মধ্যপ্রদেশের অমরকণ্টকের মহাকাল পাহাড়ে উৎপন্ন হয়ে নর্মদা নদী পশ্চিমদিকে প্রবাহিত হয়েছে ও আরব সাগরে মিলিত হয়েছে। নর্মদা উপত্যকার পাহাড়ী অংশগুলিতে গোণ্ড, কোরকু, ভীল ও ভীলালা জনজাতিদের আদি বাসস্থান। নর্মদা উপত্যকায় হাজার হাজার বছর ধরে মানবসভ্যতা ধীরে ধীরে বিকশিত হয়েছে। নর্মদা উপত্যকার বহুমুখী বিকাশ ও উন্নয়নের জন্য ভারত সরকার নর্মদা ভ্যালি ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট গ্রহণ করে। এই প্রকল্পে ছোট, বড় ও মাঝারি অনেক বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা ছিল। বাঁধ নির্মাণের ফলে যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে যাচ্ছেন তাদের পুনর্বাসনের প্রস্তাব ছাড়া আর কোনো তথ্য দেওয়া হয়নি। গ্রামবাসীদের সাথে পরামর্শও করা হয়নি। ফলস্বরূপ গুজরাট, মহারাষ্ট্র ও মধ্যপ্রদেশের আড়াই লক্ষেরও বেশি অধিবাসীর জীবন, জীবিকা বিপর্যস্ত হওয়ার মুখে পড়ে। ১৯৭৯ সালে প্রথম সরকারি অনুমোদন আসে এবং ১৯৮৫ সালে বিশ্বব্যাপ্ত এই প্রকল্পের জন্য বিপুল পরিমাণ ঋণ মঞ্জুর হয়। ১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মহরাষ্ট্রের বাস্তুহারা মানুষেরা এই প্রকল্পের বিরুদ্ধে সমিতি গঠন করে। ক্রমশ আদিবাসীদের গ্রামগুলিতে ছোট ছোট জন-আন্দোলন ও প্রতিবাদ গড়ে ওঠে।
চিত্র ১.৬- নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন ‘লোগো’
১৯৮০ থেকে ২০০৪ সাল পর্যন্ত স্থানীয়রা তেহরি ড্যাম বিরোধী বিদ্রোহ করেছিল তেহরি শহর ও অরণ্যাঞ্চল ডুবে যাওয়ার ঘটনা আটকাতে। তবুও পুলিশ মোতায়েন করে এই প্রজেক্ট চালানো হতে থাকলে সুন্দরলাল বহুগুণা অনশন শুরু করেছিলেন। তেহরি বাঁধ ভারতের উত্তরাখণ্ডের তেহরি গাড়োয়াল জেলার নিউ তেহরিতে ভাগীরথী নদীর উপর নির্মিত। ২৬০.৫ মিটার উচ্চতা সহ ভারতের সবচেয়ে উঁচু এই বাঁধ টিএইচডিসি ইন্ডিয়া লিমিটেড এবং তেহরি হাইড্রোইলেকট্রিক কমপ্লেক্সের দ্বারা নির্মিত হয়েছিল ১৯৭৮ সাল থেকে ২০০৪ সালের মধ্যে। বলা হয়েছিল যে এই প্রকল্প থেকে দিল্লি শহরের প্রয়োজনীয় ৩০০ কিউসেক জলের জোগান দেওয়া হবে। এই বাঁধটির নির্মাণ বাস্তবায়িত হলে যে পরিবেশগত ক্ষতি হওয়ায় সম্ভাবনা ছিল, তা হল- হিমালয়ের ভূমিকম্প প্রবণ নবীন ভঙ্গিল পার্বত্য অঞ্চলে এই প্রস্তাবিত বাঁধ নির্মাণের পরিকল্পনা যেকোনো সময়ে ধস নামার আশঙ্কাকে বর্ধিত করে। আর বাঁধ বা জলাধার ভেঙে পড়লে প্রচুর বনভূমি ও কৃষিজমি, এমনকি ঐতিহাসিক শহর তেহরির ডুবে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে এবং বসবাসকারী প্রাণীর জীবন বিনষ্টির সম্ভাবনা থেকে যায়। বাঁধ নির্মাণের জন্য ভাগীরথী নদী অববাহিকা বরাবর প্রচুর পরিমানে বৃক্ষচ্ছেদনও পরিবেশের ক্ষতি সাধনের কারণ।
উন্নয়নমুখী বাঁধ নির্মাণের বিরূপ প্রভাবগুলি বুঝতে পেরে পরিবেশবিদদের একাংশ, এমনকি চিপকো আন্দোলনের নেতা সুন্দরলাল বহুগুণা অগণিত প্রশ্ন তোলেন তথাকথিত উন্নয়নের প্রতি। ফলস্বরূপ বিখ্যাত স্বাধীনতা সংগ্রামী বীরেন্দ্র দত্ত সাকলানির নেতৃত্বে তেহরি বাঁধ বিরোধী সংঘর্ষ সমিতি প্রতিষ্ঠিত হয়। যা প্রায় এক দশক ধরে এই বাঁধ নির্মানের বিরোধিতা করে। তেহরি সহ বহু গ্রাম নিমজ্জিত হওয়ার ভয়, ১৯৯১ সালে ঊর্ধ্ব ভাগীরথী উপত্যকায় ভূমিকম্পের পর বাঁধের জীবনকাল ও সুরক্ষা সংক্রান্ত জায়মান প্রশ্ন পরিবেশবিদ ও তেহরি বাঁধ বিরোধী সমিতির চিন্তাভাবনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বাঁধের প্রভাব বিশ্লেষণের জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে রায় কমিটি গঠিত হয়। ১৯৮০ সালের মার্চ মাসে কমিটির রিপোর্টে বাঁধ নির্মাণের পরিবেশগত দিকটি পর্যালোচনা না করার অসন্তোষ ব্যক্ত হয়। ১৯৯১ সালের ভূমিকম্পের পর কেন্দ্রীয় সরকার আবার বাঁধটির ভূমিকম্প সংক্রান্ত নিরাপত্তা পরীক্ষার জন্য রোরকি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূমিকম্প বিশেষজ্ঞ জয় কৃষ্ণ এর নেতৃত্বে পাঁচ জন সদস্যের একটি দল গঠন করে। আলোচিত হয় পরিবেশ উদ্বাস্তুতা এবং পুনর্বাসনের প্রসঙ্গ। পরিবেশবিদদের চিন্তা, চাহিদা ও দাবিগুলির প্রতিনিধিত্ব করে সুন্দরলাল বহুগুণা যথাক্রমে ১৯৯২, ১৯৯৫ ও ১৯৯৭ সালে অনশনে বসেছিলেন।
বেশ কিছু পরিবেশ আন্দোলনে প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহারে স্থানীয় জনগণের আর্থিক-সামাজিক অধিকার স্বীকৃতিই প্রধান ব্যাপার হলেও শেষ পর্যন্ত ধর্মীয় বিশ্বাস পরিবেশ রক্ষার লড়াইয়ের অবলম্বন হয়ে উঠেছিল। যেমন- ওড়িশার কালাহাণ্ডি ও রায়গড়া জেলায় অবস্থিত নিয়মগিরি শৈলমালা। ওই এলাকার আদিবাসী গোষ্ঠীর কাছে তাদের দেবতাদের বাসস্থল হল এই নিয়মগিরি শৈলমালা, ঠিক যেভাবে আমাদের কাছে কৈলাস। পাহাড়ের চূড়া তাদের কাছে নিয়ম-রাজা নামে পরিচিত। পাহাড়ে কোন্ধ উপজাতি ঝুম চাষ করে এবং বিভিন্ন রকমের ফলের চাষ করে দিন অতিবাহিত করে। ওই পাহাড়েরই উপরের দিকে আবার অ্যালুমিনিয়াম ধাতুর আকর বক্সাইটের উপস্থিতির সন্ধান পাওয়া যায়। ইস্পাত, অ্যালুমিনিয়াম যে কোনো উন্নয়নকামী রাষ্ট্রের আকাঙ্খার বিষয়। কিন্তু ডোঙ্গারিয়া কোন্ধ ও কুটিয়া কান্ধা আদিবাসী গোষ্ঠীর প্রতিনিধিরা নিয়মগিরি আন্দোলন (২০০৩-২০১৩) করে দাবি জানায় যে বক্সাইট আকর খাননে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস আর জীবনযাত্রার উপরে কু-প্রভাব পড়বে। ফলে আদিবাসী গোষ্ঠীর আপত্তি, খনি মালিকদের পাল্টা যুক্তি, কেন্দ্রীয় সরকারের বন ও পরিবেশ মন্ত্রকের তত্ত্বাবধানে বৈজ্ঞানিক-সামাজিক সমীক্ষা চলতে থাকে। ১৮ই জুলাই ২০১৩ সালে দেশের সর্বোচ্চ আদালত সুপ্রিম কোর্ট এই খনি প্রকল্পের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের দায়িত্ব দেয় আদিবাসী জনগোষ্ঠীর গ্রামসভার উপরে। ফরেস্ট এডভাইসারি কমিটি অরণ্য অধিকার আইনের প্রসঙ্গক্রমে আদিবাসীদের উপাসনার অধিকারকে প্রাধান্য দেয় এবং সুপ্রিম কোর্ট এই প্রস্তাব গ্রহণ করে।
একইভাবে সিকিমের রাথং-চু জলবিদ্যুৎ প্রকল্প ধর্মীয় আপত্তির কারণে বন্ধ করা হয় ১৯৯৭ সালে। মনে করা হয় রাথং-চু একটি পবিত্র নদী, যার উৎস ন’টি প্রবিত্র হ্রদ। এই নদীকে ঘিরে ধর্মীয় আচার, অনুষ্ঠানের সময় নদীর জল সাদা হয়ে যাওয়া ও সংগীত শুনতে পাওয়ার জনশ্রুতি এর আধ্যাত্মিক মাহাত্ম্যকে বর্ধিত করে। ভারতীয় বিজ্ঞান একাডেমির সদস্য অধ্যাপক প্রকৃতিবিদ পি.এস.রামকৃষ্ণন এই প্রকল্প তৈরীর বিরোধিতা করে রিপোর্ট জমা দিয়েছিলেন, যা এই প্রকল্প বন্ধের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মধ্যপ্রদেশের সিংগরৌলি জেলার অরণ্য অধ্যুষিত গ্রাম আমেলিয়া গ্রাম। এই অরণ্যের কিছু অংশে বক্সাইট খনির প্রকল্প হিন্ডালকো-এর। গ্রামের জনগোষ্ঠী জঙ্গল নির্ভর হওয়ায় তারা এই প্রকল্পের বিরোধিতা করে, তৈরি হয় মহান সংঘর্ষ সমিতি। কিন্তু অরণ্য অধিকার আইন অনুযায়ী দাবি জানানো হলেও তাতে কাজ না হওয়ায় শেষ পর্যন্ত জঙ্গলের রক্ষাকর্তা ডিহ বাবার উপাসনা ক্ষেত্রে ধর্মীয় অধিকারের দাবিতে অরণ্য বাঁচানোর প্রয়াস স্থান পায়৷
এছাড়াও ১৯১৯ সালে ইয়াংসি নদীতে তিনটি গিরিখাত বাঁধ তৈরির বিরুদ্ধে আন্দোলন, রাশিয়ার বৈকাল হ্রদের ইকো-সিস্টেম বিনষ্টকারী পাঁচটি বড় সেলুলোজ ও কাঠের কারখানার বিরুদ্ধে আন্দোলন, ১৯৯৪ সালের বীরভূমের খাদান বিরোধী গণ আন্দোলনের স্বাক্ষর তো আছেই। দুন উপত্যকার চুনাপাথর খাদে খনি মালিকদের দায়িত্ব সংযমহীন কাজের জন্য এলাকার প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার অভিযোগ আনে স্থানীয় অধিবাসীরাই। লক্ষণীয়, এরা সকলেই যে আর্থিক দিক থেকে খুব অবস্থাপন্ন, এমনটা নয়; তবু তারা নিজেদের চরাচরে প্রাকৃতিক ভারসাম্যের সম্বল নষ্ট করতে চায়নি, মাত্রার অতিরিক্ত উন্নয়নও তাদের চাহিদার অন্তর্ভুক্ত ছিল না।
পর্ব – ১৮
কার্ল মার্ক্সের পরিবেশ ভাবনা
পরিবেশ ভাবনায় কার্ল মার্ক্স-এর গুরুত্বপূর্ণ কাজ পাওয়া যায় ‘প্যারিস পাণ্ডুলিপি’ (১৮৪৪) আর ‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’তে (১৮৪৮)। ‘প্যারিস পান্ডুলিপিতে’ তাঁর বক্তব্য- পরিবর্তন মূলতঃ পরিবর্তনমূলক। এই পরিবর্তন ও সমাজ বিকাশের ধারায় প্রকৃতি থেকে অতিরিক্ত দাবি করতে গিয়েই উৎপাদন প্রক্রিয়ার প্রতিটি পর্যায়ে প্রকৃতি মানবেতিহাসের খাঁজে অনুপ্রবিষ্ট হয়েছে। প্রতিটি উৎপাদন মানুষের শরীরকে বাঁচিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে। ফলে মানবেতিহাসের আবহমান ধারায় প্রকৃতি ও শরীর পরস্পর অবিছিন্ন। এমনকি প্রযুক্তির দ্বারাও প্রকৃতি অনুপ্রবেশ করে মানবেতিহাসে। প্রযুক্তি নিজে উৎপাদন প্রক্রিয়ার পরিণতি, যা প্রকৃতির রূপান্তরের প্রক্রিয়াকে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করলেও তার সংরক্ষণ সম্পর্কিত জ্ঞান অর্জন করাতে পারে না৷
মার্ক্সের মৌলিক প্রস্তাবটি এই যে- ধনতান্ত্রিক উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে পরিবেশের দ্বন্দ্ব অমীমাংসেয়। তাঁর সময়ে অর্থাৎ উনিশ শতকে সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রে উৎক্রমণের প্রক্রিয়াটি গতিশীল ও মানুষের স্মৃতিতে ক্রিয়াশীল ছিল। তাই প্রকৃতি ও সমাজের দ্বান্দ্বিক সম্পর্ক বিষয়ে মৌলিক সমস্যাগুলি তাঁর কাছেও জীবন্ত ছিল। তিনি পরিবেশের সমস্যাকে শুধু প্রযুক্তির সমস্যা নয়, তাকে ধনতন্ত্রের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য হিসেবে দেখেছিলেন। তিনি দেখান কীভাবে ধনতন্ত্র মানুষকে ‘বস্তু’ হিসেবে বিবেচনা করে তার শ্রমশক্তির দ্বারা সামাজিকভাবে উৎপাদিত বস্তুকে পণ্য করে তোলে। এমনকি এই পণ্যের উপর জাদুময় ব্যক্তিত্ব আরোপ করে পণ্যমোহ’ও তৈরি করা হয়। ফলে ঘটতে থাকে প্রকৃতি লগ্নতা থেকে বিচ্ছিন্নতা ও প্রকৃতিলগ্ন জীবনচর্যার সার্বজনীন বিস্মৃতি। ধনতন্ত্রে বুর্জোয়া শ্রেণি কখনোই শ্রমশক্তির পুরো মূল্য দেয় না বলেই উদ্বৃত্ত মূল্যে মুনাফা অর্জন করতে পারে। অতি উৎপাদনের সংকট থেকে মুক্তি পায় না ধনতন্ত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে এই সমস্যা থেকে অব্যাহতির জন্যই তথ্যপ্রযুক্তিকে ব্যবহার করে, তথা রাষ্ট্রীয় তথ্য প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে ধনতন্ত্র চেষ্টা করছে চাহিদার চরিত্রের পরিবর্তন ঘটিয়ে পণ্যমোহ’র তীব্রতাকে ধারাবাহিক ভাবে বিকশিত করে তুলতে। ‘Amazon’, ‘Google’, ‘Apple’-এর বৃহৎ পুঁজির সাথে যুক্ত হচ্ছে রাষ্ট্রীয় আনুকূল্য নির্ভর দালাল পুঁজিবাদী গোষ্ঠী (‘Crony capitalist’), যারা একত্রে বিশ্ব-বাণিজ্যে একচেটিয়াকরণকে গতিশীল করেছে।
বিশ্ববাজরকে কাজে লাগাতে গিয়ে ধনতন্ত্র প্রতিটি দেশের উৎপাদন ও উপভোগের চালচিত্রকে একটি বিশ্বজনীন চরিত্র দান করেছে। নতুন চাহিদা মেটাতে সুদূর দেশ-বিদেশের নানা আবহাওয়ায় উৎপন্ন পণ্য দরকার হয়েছে। ফলে পরিবেশের ধ্বংস সাধনের বিশ্বজনীনতা অনিবার্য হয়েছে। এই ভয়ঙ্কর বিকাশে শ্রম হয়েছে অপাঙক্তেয়, ‘জ্ঞান’ (Knowledge) হয়েছে বাণিজ্যের বিষয় এবং ভোগ্য পণ্যের পাহাড় বর্জ্যকে বাড়িয়ে তুলেছে- যা ক্রমাগত ভেঙে চলেছে প্রকৃতির সমগ্রতাকে, স্বাভাবিকতাকে। প্রকৃতিকেন্দ্রিক সংস্কৃতির জায়গায় পণ্যকেন্দ্রিক ‘ফেটিস’ (Fetish) সংস্কৃতি প্রশ্রয় পেতে পেতে একবিংশ শতাব্দীতে এই সংস্কৃতির একাধিপত্যে এসে পড়েছি আমরা। ম্যাক ডোনাল্ডস-এর আউটলেটে খাবার খেলে সেখানে বসে ফ্রি ওয়াইফাই’তে কাজ করা যাবে। অর্থাৎ পণ্যের সঙ্গে পরিষেবায় দেওয়া হল ওয়াইফাই এবং ‘রিলাক্সিং’ একটা পরিবেশ যেখানে মন দিয়ে কাজ করা যায়। ঠিক যেমন একটা বড় কফি কাপে খুব ধীরে চুমুক দিতে দিতে অনেকক্ষণ বসে থাকা যায়, ক্রেতা ‘ফ্রি মাইন্ডে’ গল্প জমাতে পারে, ল্যাপটপে কাজ করতে পারে; কেউ তাকে উঠে যেতে বলবে না। পুঁজিবাদী অর্থনীতি বর্তমানে আধিপত্যবাদী শক্তি। আর এই একচেটিয়া পুঁজিবাদের উন্নয়নের মূলে যে অর্থনৈতিক গতিশীলতা, সেটাই পরিণত হয়েছে জলবায়ু সঙ্কটের মূল চালিকাশক্তিতে। বিগত শতকের সাত ও নয়ের দশকের মধ্যে কৃষির কর্পোরে্টাইজেশন এবং নয়ের দশক থেকে জলবায়ু উদ্বাস্তু সমস্যা সচেতনতার প্রধান জায়গা হয়ে ওঠে।
‘কমিউনিস্ট ম্যানিফেস্টো’ অনুযায়ী বুর্জোয়া শ্রেণি যে উৎপাদন শক্তি সৃষ্টি করেছে, তা অতীতের সকল যুগের উৎপাদন শক্তির চেয়েও বিশাল, অতিকায়। সামাজিক শ্রমের কোলে যে এতটা উৎপাদন শক্তি সুপ্ত ছিল, পূর্বতন শতকে তা কল্পনাও করা যায়নি। এই উৎপাদন শক্তির সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মানুষের সৃজনশীলতা ও উৎপাদন ক্ষমতা পরিবেশ সহায়ক শক্তিতে রূপান্তরিত হতে পারেনি। সৃজনশীলতাকে নিয়ে ধনতন্ত্র বস্তুত বাণিজ্য করেছে। প্রাকৃতিক পরিবেশ ও তার উপাদানগুলিকে ধনতন্ত্র সর্বদাই মুনাফা অর্জন ও পুঁজি সঞ্চয়ের সর্বোচ্চ লক্ষ্য অর্জনের উপায় হিসেবেই দেখেছে। সেজন্য ধনতান্ত্রিক ব্যবস্থায় কিছু সংস্কারমূলক পদক্ষেপ ও শক্তিশালী পরিবেশ আন্দোলনের বিকাশ হওয়া সত্ত্বেও পরিবেশ-সঙ্কট ক্রমবর্ধমান। আসলে ধনতন্ত্রের মর্মবস্তুটি এক থেকে যায় বলে পরিবেশের সঙ্গে দ্বন্দ্বটি অমীমাংসেয় থেকে যায়।
ঊনবিংশ শতকের তিনের দশকে একজন ইংরেজ, স্যার জন বেনেট লয়েস রাসায়নিক সার নিয়ে পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। ১৮৪০ সালের মধ্যে জমিতে ফসলের উপর রাসায়নিক সারের প্রভাব পরীক্ষিত হলে সার শিল্পের জন্ম ও সম্প্রসারণ ঘটে। অন্যদিকে এই সময়ে একজন জার্মান রসায়নবিদ ইয়ুস্টস ফন লিবিগ ‘এগ্রিকালচারাল কেমিস্ট্রি’তে দেখান যে জমির উর্বরতা সহায়ক উপাদানগুলো কিভাবে উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। সুপার ফসফেট বানানোর কারখানা তৈরি হয়, প্রযুক্তির বিপুল বিস্তার হয়। কিন্তু ১৮৬০ সালের দিকে ফন লিবিগ ধনতন্ত্রের চরিত্র সম্পর্কে সচেতন হয়ে তার তীব্র ইকোলজিক্যাল সমালোচনা করেন। পরিসংখ্যান অনুযায়ী ১৮৫৬ থেকে ১৯০৩ সালের মধ্যে মার্কিন পুঁজিপতিরা গুয়ানো স্যারের জন্য ৯৪ টি দ্বীপ দখল করে। এই ভূমিগত দখল কৃষিগত জনসংখ্যাকে কমায় ও নগরে বাড়তে থাকে শিল্পগত জনসংখ্যা। অপূরণীয় ক্ষতির জন্ম হয়, অপচিত হয় মৃত্তিকার প্রাণ শক্তি। উনিশ শতকে জমির উর্বরতা হ্রাস, শহরে দূষণ বৃদ্ধি ও বনাঞ্চলের ধ্বংস সাধন চিন্তাবিদদের উদ্বেগের বিষয় হয়। মার্ক্সের পরিবেশ ভাবনার কেন্দ্রে ছিল ‘সোশিও ইকোলজিকাল মেটাবলিজম’ (Socio-Ecological metabolism)। প্রকৃতি থেকে সমাজ সম্পদ নিয়ে শিল্প গড়ছে, গ্রাম কিংবা উপনিবেশ থেকে কৃষিজ ও অন্যান্য জৈব সার শহরে, সাম্রাজ্যবাদী দেশে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। কিন্তু ব্যবহারের পর বর্জ্যকে ‘ডি-কম্পোজ’ রূপে প্রকৃতিতে বা মাটিতে ফেরানো হচ্ছে না। ফলে সম্পূর্ণ হচ্ছে না বিপাক চক্রটি। এতে জৈব-অজৈব বস্তু এবং প্রকৃতি ও সমাজের মধ্যে স্বাভাবিক আবর্তন বা বিপাক প্রক্রিয়ায় ভাঙন দেখা দেয়। কার্ল মার্ক্স প্রকৃতি, মানুষ ও সমাজের মধ্যে বিপাকীয় মিথষ্ক্রিয়ায় বৃহৎ কৃষি খামারের উৎপাদন পদ্ধতিকে গুরুত্ব দেন।
প্রসঙ্গত বলা উচিত যে মার্ক্স, পরিবেশ ও সমাজের মধ্যে যে ‘মেটাবলিক রেট’ ও চক্র পূর্ণ করার কথা বলেছিলেন, বিশেষত তৃতীয় দুনিয়ায় সেটা সম্ভব হচ্ছেনা। প্রথমত, প্রযুক্তির উন্নয়নে শহরে শিল্প বৃদ্ধিতে ও ‘অটোমেশন’-এর (Automation) যুগ এসে পড়ায় গ্রামের লোক কাজ হারিয়ে শহরে জনসংখ্যা বাড়াতে থাকে। এত লোকের খাদ্য চাহিদা মেটাতে প্রাকৃতিক পরিবেশে উৎপাদিত খাদ্য ও তন্তু (fibre) শহরে চলে গেল কিন্তু তা আর প্রকৃতিতে ফিরে এলনা। আবার অন্যদিকে সেগুলো শহরের বর্জ্যকেও বাড়িয়ে চলল। দ্বিতীয়ত, মাটির প্রাকৃতিক সার ও মাটি তথা প্রাকৃতিক খনিজে সমৃদ্ধ মাটি উপনিবেশে, শহরে রপ্তানি হয়ে যায়। তৃতীয়ত, এরকম ধারণা আছে যে কহুজাতিক সংস্থাগুলির তৈরি করা ‘Genetic engineered’ বীজ, ‘High yeilding’ বীজ ব্যবহার না করলে খাদ্য সমস্যা মেটানো যাবে না। কিন্তু উপযুক্ত পরিবেশে দেশীয় ধানবীজ ও সঙ্গে অল্প রাসায়নিক সার ব্যবহার করে চাহিদার সামাল দেওয়া সম্ভব। সমস্যাটা এই যে ওই সার থেকে প্রয়োজনীয় খনিজকে শোষণ করে বেড়ে ওঠা খাদ্যশস্য আঞ্চলিক ভাবে ভোগ্য না হয়ে বাইরে চলে যাচ্ছে। এই পর্যায় থেকেই মার্ক্স পরবর্তী দার্শনিকদের কেউ কেউ প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্ক নিয়ে বিকল্প দর্শনের কথা বলবেন।
পর্ব – ১৯
বাস্তুতন্ত্রের স্বাধীনতা ও স্বাধীনতার বাস্তুতন্ত্র
উত্তরাধুনিক বিশ্বে উপযোগবাদ থেকে যে সাম্রাজ্যবাদ ও ঔপনিবেশিক চিন্তার বিকাশ ঘটেছে, সেখানে মানুষ এবং প্রকৃতি মুখোমুখি দাঁড়িয়েছে। প্রকৃতি সেখানে অধস্তন হয়েছে, আর মানুষ হয়েছে ‘ফ্রাঙ্কেস্টাইন’। সমাজবিজ্ঞানী ও চিন্তক কার্ল মার্ক্স এই ব্যবস্থা থেকে বেরিয়ে এসে এমন সমাজব্যবস্থা গড়ার কথা বলেছিলেন যেখানে প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের আর মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সুষম বণ্টন ব্যবস্থা স্থাপিত হয়। এদিক থেকে মার্ক্সের নীতি যেমন বিপ্লববাদী, তেমনি পরিবেশবাদীরও নীতি। তিনি প্রকৃতির সঙ্গে সহনশীল উৎপাদনের কথা বলেছিলেন। কিছু পশ্চিমী সিনেমা, যেমন- ‘বার্ন’ (Burn), ‘ব্যাটেল অফ আলজিরিয়া’ (Battle of Algeria)তে দেখানো হয়েছে কিভাবে উপনিবেশবাদ কাউকে হাতের মুঠোয় আনতে তার পরিবেশ-প্রকৃতি, তথা তার বেঁচে থাকার উৎসকে ধ্বংস করছে। বিশ শতকের প্রথম দশক থেকেই পরিবেশের মধ্যে ‘একত্বে’র বোধ বিপন্ন হচ্ছে, স্বাস্থ্যগত সংকটও প্রকট। প্রকৃতপক্ষে মানুষ আর পরিবেশ-প্রকৃতির মুখোমুখি দাঁড়ানোর অবস্থানে কার জয় কার পরাজয়, বলতে পারা মুশকিল। ১৯৩০-৩৫ সালের মধ্যে একজন আমেরিকান মার্ক্সবাদী মারে বুকচিন (Murray Bookchin) এই প্রেক্ষিতে গুরুত্বপূর্ণভাবে বুঝতে পেরেছিলেন যে মানুষ মোটেও ভালো নেই। তিন্নি বুঝেছিলেন যে বিশ শতকীয় সামাজিক বিন্যাস তেমন সুখকর নয়, মানুষ যেমন প্রকৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়িয়েছে- সেটাও খুব একটা সুখকর ফসল দান করেনা। এখান থেকে মারে বুকচিন ফিরে যাচ্ছেন কৌম জীবনের স্মৃতির কাছে (সামাজিক বিবর্তনের পথ বেয়ে), যেখানে উৎপাদন ও বণ্টন সুষম ছিল। ছিল সৌহার্দ্য ও সহানুভূতি। সেই সমাজে বণ্টনের সুষমতার মতো ব্যাপারের কারণ খুঁজতে গিয়ে অনুধাবন করেন ‘অর্গ্যানিক সোসাইটি’র (Organic Society) দর্শনকে, যেখানে বর্তমান সাম্যের স্বাধীনতা। এই ধরনের সমাজে এমন ভাবনা ক্রিয়াশীল যে সকলে সকলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত হয়ে স্বতন্ত্র অর্থাৎ প্রত্যেকে প্রত্যেকের উপরে নির্ভরশীল এবং মানুষ সেখানে প্রকৃতিরই অংশ। ফলে প্রকৃতির প্রতি সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণের মাধ্যমে মানুষ একে অপরের সঙ্গেও সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণে অভ্যস্ত হয়।
‘ইগো’ নয়, চাই ‘ইকো’
মারে বুকচিনের ‘ইকোলজি অফ ফ্রিডম’ (Ecology of freedom, ১৯৮২) বইতে দেখানো হয়েছে যে ‘ইকোলজিকাল নীতি’কে মাথায় রেখে সমাজ পুনর্গঠনের মাধ্যমে পরিবেশগত সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। এক্ষেত্রে তিনি বরঞ্চ কৌম দুই সম্প্রদায়ের উপরে নৃতাত্ত্বিকের গবেষণা কাজের সমর্থনে জানান, তাদের জীবনাচরণে এমন কোনো শব্দই নেই যা আধিপত্যবাদ, শোষণ, নিপীড়ন, বৈষম্যকে ‘বিশেষ’ করে চিহ্নিত করে। সেখানে প্রথা আছে, কোনো নতুন শিশু জন্মালে তার মা’ই কেবল গর্ভধারিণী হননা, ওই সমাজের সকল মায়েরাই হয়। মায়েদের মুখের চেবানো খাদ্য ওই শিশুর মুখে দিয়ে দেওয়া হয়- এমন সংস্কারমূলক ক্রিয়াকর্মের মধ্যে বিশ্বাস লুকিয়ে আছে যে খাদ্যে মেশানো লালারস শিশুর শরীরে মিশে যাওয়ায় সে একসঙ্গে বহু মায়ের ধারণাকে ধারণ করে। এখানে প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিকতার সম্পর্ককে স্বীকার করা হয় (involving interaction between two different organisms living in close physical Association)। এই সম্পর্কে উধাও হয় ঊর্ধ্বতন-অধস্তনের ভাবনা। বলা বাহুল্য তিনি কখনওই এমনটা বোঝাতে চাননি যে আমাদের, এই আধুনিক পৃথিবীর মানুষদের কৌম জীবনযাপনে ফিরে যেতে হবে, তবে ‘অর্গ্যানিক সোসাইটি’গুলি থেকে শিক্ষা নিয়ে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলা সম্ভব। মানুষ যতই আধুনিক হোক না কেন, পরিবেশেরই অন্তর্গত ও বর্ধিত অঙ্গ। পরিবেশ সংকট আমাদের এমন এক অবস্থানে নিয়ে যায়, যেখানে আমরা আমাদেরকে চেনার উপায় খুঁজি না, মানুষ মানুষের সঙ্গে সম্পর্ক খোঁজেনা। নরওয়ের পরিবেশ দার্শনিক আর্নে নেস (১৯১২-২০০৯) তাঁর ‘ডীপ ইকোলজি’র দর্শনে (Deep ecolog, ১৯৭৩) ‘প্রকৃতি এক’ ও ‘প্রকৃতি দুই’ (Nature one and two)-এর কথা বলেছেন। প্রকৃতি, তার উপাদান প্রথমটির অন্তর্ভুক্ত এবং ‘প্রকৃতি এক’কে ব্যবহার করে মানুষ তার চারপাশে যে নতুন পরিবেশ (environment) গড়ে তোলে, তাকেই বলা হচ্ছে ‘প্রকৃতি দুই’ বা ‘সেকেন্ড নেচার’। মারে বুকচিন এই ‘প্রকৃতি এক’ এবং ‘প্রকৃতি দুই’-এর মধ্যে ব্যবধান হ্রাস করার কথা বলেছেন।
জীবিত কিংবা নির্জীব সমস্ত বিষয়ই ‘ইকোসেন্ট্রিক’ ভাবনার কেন্দ্রবিন্দু
‘ইকোলজিকাল ফ্রিডম’ (ecological freedom)-এর প্রসঙ্গে মারে বুকচিন নির্দেশ করতে চেয়েছেন প্রকৃতির প্রতি উপাদান যে অবস্থায় সমান গুরুত্বপূর্ণ, সেই অবস্থাকে। সমাজকে প্রকৃতির বর্ধিত ফর্ম হিসেবে ভাবা গেলে প্রকৃতি সম্পর্কে শিক্ষা সমাজ জীবনের শিক্ষার সঙ্গে যূথবদ্ধতা তৈরি করে। ফলে মানুষ যেমন প্রকৃতিকে বুঝবে, তেমনি তার সামাজিক জীবনকেও বুঝবে- এই বোঝাপড়ার মধ্যে দিয়েই মুছে দেওয়া যায় ‘সোশ্যাল হায়ারার্কি’কে। তিনি সেই ‘কমিউন’ সমাজের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেন, যেখানে বর্তমান পারস্পরিকতার সম্পর্ক ও তাকে সম্মান করে সমতাবাদী প্র্যাকটিস। ‘যুদ্ধ’, ‘পুঁজি’- এই পরিভাষাগুলোর জন্ম যখন থেকে, আধিপত্যবাদ-শোষণ এবং মানুষের প্রান্তিকতার ধারণার জন্ম তখন থেকেই। সম্পর্কে যারা জানেনা তারা যুদ্ধে ও পুঁজিবাদীদের মাধ্যমে দমিত হল। মারে বুকচিন একে সমাজের অধঃপতনের দিক হিসেবে চিহ্নিত করছেন। সেখানে পৃথিবীর আদি প্রাণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে মাড়িয়ে যাওয়ার রাস্তাতেই আদর্শ সমাজের পতন। উপায়, সমাজের সেই আদিতম অবস্থানে ফিরে যাওয়া, যেখানে পারস্পরিক শ্রদ্ধা ও ভালোবাসার সম্পর্কগত বিন্যাস মূল্য পায়।
পর্ব – ২০
এনভায়রনমেন্ট – নীতি ও নৈতিকতা
গ্রীক ‘এথোস’ থেকে আগত ‘এথিক্স’, ‘এথনিক’ (Ethics, Ethnic) অর্থাৎ অভ্যাস (Habit)। ‘এথিক্স’ আক্ষরিক অর্থেই দড়ি, যা মানুষকে নিয়ে যায়, যার মাধ্যমে মানুষ নীত হয়। নিজেকে নিজে উপদেশ দেওয়াটা যেখানে ‘এথিক্সে’র ব্যাপার, অপরকে উপদেশ দিয়ে পরিচালিত করাটা ‘এথিকাল’। পরিবেশগত নীতিশাস্ত্রের আধুনিক দর্শন বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বিকশিত হয়। জনসংখ্যা বিস্ফোরণ, পরিবেশ ও পরিবেশগত সম্পদের অবক্ষয়, সংকট ইত্যাদি সমস্যা পরিবেশগত উদ্বেগের দিকে মনোযোগ আকর্ষণ করেছিল সেই সময় থেকেই। তবে, সমসাময়িক পরিস্থিতিতে পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র নির্ধারণের সময় কিছু চ্যালেঞ্জও উত্থাপিত হয়। সমাজ, জাতি এবং অঞ্চলের মধ্যে বৈষম্য; দৈনন্দিন জীবিকার জন্য সম্পদ সংগ্রহের মৌলিক অধিকার ইত্যাদি ছিল পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র নকশার মূল চ্যালেঞ্জ। এর ফলে পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি হয়েছে। পরিবেশগত নীতিশাস্ত্র সম্পর্কে মূলত তিন রকমের দৃষ্টিভঙ্গি পাই :
১. উদারপন্থী দৃষ্টিভঙ্গি (Libertarian view)
২. পরিবেশগত দৃষ্টিভঙ্গি (Ecological view)
৩. সংরক্ষণ দৃষ্টিভঙ্গি (Conservation view)
একটি নদী বনভূমির অভ্যন্তরে খাল এবং পাথুরে গিরিখাতের মধ্য দিয়ে সমুদ্রের দিকে প্রবাহিত হয়। রাজ্য জলবিদ্যুৎ কমিশন এই জলপ্রবাহকে অব্যবহৃত শক্তি হিসেবে দেখে। গিরিখাতের উপর একটি বাঁধ নির্মাণ করলে এক হাজার লোকের জন্য তিন বছরের কর্মসংস্থান এবং বিশ বা ত্রিশ জন লোকের দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থান হতে পারে। এই বাঁধ পর্যাপ্ত জল সঞ্চয়ের মাধ্যমে নিশ্চিত করবে সংশ্লিষ্ট রাজ্য পরবর্তী কয়েক দশক ব্যাপী প্রয়োজনীয় ‘এনার্জি’ তথা শক্তির চাহিদা কতটা মেটাতে পারবে। এর ফলে ‘এনার্জি ইন্টেন্সিভ ইন্ডাস্ট্রি’র ধারণা দৃঢ় হয়, যাতে কর্মসংস্থান এবং অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ঘটতে পারে।
হয়তো নদী উপত্যকার গভীরতর এলাকায় এমন অনেক গাছ রয়েছে, যা হাজার বছরেরও বেশি পুরানো। উপত্যকা এবং গিরিখাতগুলি অনেক পাখি এবং প্রাণীর আবাসস্থল, যার মধ্যে রয়েছে বিপন্ন প্রজাতির প্রাণীও। অন্যান্য বিরল উদ্ভিদ এবং প্রাণ থাকতে পারে, কিন্তু কেউ জানে না। কারণ বিজ্ঞানীদের গবেষণায় সেই অঞ্চল উঠে আসেনি তখনও।
এখন প্রশ্ন হল- বাঁধটি কি তৈরি করা উচিত? এখানে এমন এক পরিস্থিতি উপস্থিত, যেখানে সমাজ সমর্থিত বহুজনের ভিন্ন ভিন্ন মূল্যবোধের মধ্যে থেকে একটিকে বেছে নিতে হবে। এমন উদাহরণ আমাদের চারপাশের যে কোনো ঘটনা থেকে তৈরি করা যায়, যেমন- অস্ট্রেলিয়ার দ্বীপীয় এলাকায় তাসমানিয়ার দক্ষিণ-পশ্চিমে ফ্র্যাঙ্কলিন নদীর উপর প্রস্তাবিত বাঁধ, কিংবা বিশ শতকের ছয়ের দশকে দামোদর ভ্যালির উপর ডিভিসি’র বাঁধ নির্মাণ প্রকল্পকালীন দ্বন্দ্ব। পরিবেশ নীতি বা মূল্যবোধের ‘চয়েজ’ সংক্রান্ত প্রশ্নে উপস্থাপিত করা যায় একাধিক বিষয়- অরণ্যে বৃক্ষ নিধন, কাগজের কল স্থাপন যা জলে দূষণের পরিমাণ বৃদ্ধি করে, অথবা নতুন খনির সন্ধান পাওয়া ইত্যাদি।
সাধারণভাবে আমরা বলতে পারি যে যারা বাঁধ নির্মাণের পক্ষে, তারা অরণ্য, অরণ্য-সম্পদ, উদ্ভিদ ও প্রাণী (সাধারণ এবং বিপন্ন প্রজাতির সদস্য উভয়ই) সংরক্ষণ এবং ‘আউটডোর রিক্রিয়েশনাল অ্যাকটিভিটি’-এর তুলনায় কর্মসংস্থান এবং রাজ্যের জন্য মাথাপিছু আয় বৃদ্ধিকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। আর তৈরি করতে গেলে অসংখ্য প্রাণীর আবাসস্থল ভেসে যাবে, তারা উদ্বাস্তু হবে। মানুষের বিশিষ্টতা এখানেই যে সে সংবেদনশীল এবং নীতিপ্রবণ। বাঁধ নির্মাণের কারণে একজন মানুষের ভেসে যাওয়ার বর্ণনা যতখানি ভয়ানক, একটা গরু-ছাগল কিংবা অন্যান্য বসবাসকারী প্রাণীর ভেসে যাওয়ার কথা, কোনো এলাকায় গাছের গোটা ‘কমিউনিটি’র মৃত্যুর কথা ততটা বীভৎসতা তৈরি করে না। কার্যতই মানুষ নামক প্রাণীর বাইরেও নীতিশাস্ত্রকে যুক্তিসঙ্গতভাবে প্রসারিত করা একটি কঠিন কাজ।
প্রকৃতির প্রতি পাশ্চাত্য দৃষ্টিভঙ্গি বাইবেলের প্রাথমিক বইগুলিতে বর্ণিত হিব্রু জনগণের এবং প্রাচীন গ্রীকদের দর্শন, বিশেষ করে অ্যারিস্টটলের দর্শনের মিশ্রিত রূপ। হিব্রু এবং গ্রীক উভয় ঐতিহ্যই মানুষকে নৈতিকতার কেন্দ্রে পরিণত করেছিল। পশুর সঙ্গে মানুষের পার্থক্যই এখানে যে ‘আত্ম’ জ্ঞান সবার থাকলেও একমাত্র মানুষই ‘এথিকাল’ (ethical)।
আদিপুস্তকে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেলের গল্পটি ঐশ্বরিক পরিকল্পনায় মানুষের বিশেষ স্থান সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গি স্পষ্ট করে:
ঈশ্বর বললেন, “আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মানুষ সৃষ্টি করি; তারা সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি, পৃথিবী এবং পৃথিবীতে গমনশীল সমস্ত সরীসৃপের উপর কর্তৃত্ব করুক।” এইভাবে ঈশ্বর মানুষকে তাঁর নিজের প্রতিমূর্তিতে সৃষ্টি করলেন, তাদের আশীর্বাদ করলেন- “তোমরা ফলবান হও, বহুবংশ হও, পৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর, বশীভূত কর; সমুদ্রের মাছ, আকাশের পাখি এবং পৃথিবীতে বিচরণশীল সমস্ত জীবন্ত প্রাণীর উপর কর্তৃত্ব কর।”
সেই অনুসারে ঈশ্বর যখন মানুষকে অবাধ্যতার জন্য শাস্তি দিতে পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি প্রাণীকে ডুবিয়ে দিয়েছিলেন তখন ঈশ্বর যে উদাহরণ স্থাপন করেছিলেন, তাতে অবাক হওয়ার কিছু নেই যে মানুষ একটি নদী উপত্যকার বন্যা নিয়ে চিন্তা করার মতো কিছু পাবে না।
এইরকম ‘অধিকার’ প্রদানের অর্থ নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে বহু; এবং পরিবেশ সম্পর্কে যারা উদ্বিগ্ন তারা দাবি করে যে এমন ‘ডিক্রি’কে আমাদের চারপাশের অন্যান্য জীবন্ত প্রাণীর সাথে ইচ্ছামত আচরণ করার অনুমতি হিসাবে বিবেচনা করা উচিত নয়। পরিবর্তে ঈশ্বরের সন্তান হিসেবে আমাদের পরিবেশ এবং তার সম্পদের যত্ন নেওয়ার, তাদের সাথে আমরা যেভাবে আচরণ করি তার জন্য ঈশ্বরের কাছে জবাবদিহি করার নির্দেশ হিসাবে বিবেচনা করা উচিত। এর তাৎপর্য স্পষ্ট- এমনভাবে কাজ করা যা পৃথিবীতে চলাচলকারী সবকিছুর জন্য ভয় এবং আতঙ্কের কারণ হয়; এটি আসলে ঈশ্বর-প্রদত্ত বিধানেরই অনুসরণ।
এমনকি মানব কেন্দ্রিক নৈতিক কাঠামোর (Human centred ethical structure) মধ্যেও, আমাদের পরিবেশের সংরক্ষণ সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। ফসল ফলানো এবং পশুপালনের উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা সভ্যতার দৃষ্টিকোণ থেকে, মরুভূমিকে পতিত ভূমি, অকেজো এলাকা বলে মনে হতে পারে যাকে উৎপাদনশীল করার চেষ্টা মানুষই করতে পারে। একটা সময় ছিল যখন কৃষিজমি দ্বারা বেষ্টিত গ্রামগুলিকে ঢালাও অরণ্যের মধ্যে, মরুভূমির মধ্যে কিংবা রুক্ষ পাহাড়ি ঢালের মধ্যে মনে হতো কৃষির মরূদ্যান। আধুনিক সময়ে আধুনিক হওয়ার মূল্যে আমাদের কাছে থেকে যাওয়া অরণ্যের অবশিষ্টাংশ মানব সভ্যতার কর্মকাণ্ডের সমুদ্রে বিচ্ছিন্ন দ্বীপের মতো। এখানেই অরণ্য, অরণ্যসম্পদের সঙ্গে জুড়ে যায় ‘স্কারসিটি ভ্যালু’ (Scarcity Value) তথা অভাবের নীতি, যার ফলে সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সংক্রান্ত যুক্তির ভিত্তি দৃঢ় হয়। তা মানবকেন্দ্রিক নীতির শর্তাবলির মধ্যেও প্রযোজ্য, দীর্ঘমেয়াদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণে এই যুক্তি আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজস্থানের ‘ট্রি ম্যান’ সুরেন্দ্র আওয়ানা, ‘ট্রি টিচার’ হিম্মতারাম ভম্ভু প্রমুখ মাঝে মাঝে কয়েকজনের উদ্যোগ সামনে আসলেও আসলে একটা গোটা রুক্ষ শূন্য এলাকার ‘কালচার’ পাল্টে দিতে প্রয়োজন ‘কমিউনিটি’র এথিকাল পরিবর্তন।
চিত্র – ‘বাংলা লাইভ.কম’, ‘উইকিপিডিয়া’
আমরা সবাই জানি আমাদের বাগানের গাছপালার জন্য কী ভালো বা কী খারাপ। জল, সূর্যালোক এবং সার ভালো, অতিরিক্ত তাপ বা ঠান্ডা চরম ক্ষতিকর। যে কোনো অরণ্য বা প্রান্তরের গাছপালার ক্ষেত্রেও একই কথা প্রযোজ্য, তাহলে কেন তাদের বিকাশকে নিজেদের ভালো লাগা বলে বিবেচনা করা হবে না! প্রাচীন অরণ্য কেউ লাগায়নি, তাকে সংরক্ষণ করতে হয় না। অথচ আজ আমরা এমন জায়গায় উপনীত হয়েছি যে বনাঞ্চল সংরক্ষণ ও পরিবেশের প্রতি যত্নবান হওয়ার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য এমন সুযোগ তৈরি করে যেতে পারি, এমন একটি সংস্কৃতি তৈরি করে যেতে পারি (বই, চলচ্চিত্রের মাধ্যমে) যা আমাদের সন্তানদের এবং তাদের সন্তানদের কাছে হস্তান্তর করা যেতে পারে। অর্থাৎ অত্যাধুনিক ধূসর পৃথিবীর উল্টোদিকে হস্তান্তর যোগ্য পৃথিবীর বিকল্প রেখে যেতে পারি। রুক্ষ এলাকায় মিলিতভাবে জল সংরক্ষণ করার প্রকল্প যখন এলাকার ‘কমিউনিটি’ নিজের ঘাড়েই নিত, এলাকার পুকুর গুলির রিচার্জ করার ব্যবস্থা থাকত, পুকুরের তলদেশে এক কোণে কুয়ো খুড়ে রাখার ফলে জল কখনও শুকোত না- সেগুলোই ‘এনভায়রনমেন্টাল এথিক্স’। যদি আমরা মনে করি যে কম্পিউটার গেম খেলার চেয়ে
অরণ্যের পথে হেঁটে একটি দিন কাটানো গভীরভাবে ফলপ্রসূ, অথবা যদি মনে করি যে এক সপ্তাহের জন্য ব্যাকপ্যাকে খাবার এবং তাবু বহন করে আদিম প্রকৃতিতে থাকা, হাইকিং করা টেলিভিশন দেখার চেয়ে চরিত্রের বিকাশে আরও বেশি অবদান রাখবে, তাহলে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে পরিবেশ-প্রকৃতির প্রতি সহাঅনুভূতি ও সমানুভূতি রাখতে উৎসাহিত করা উচিত। যদি তারা বিকল্প হিসেবে কম্পিউটার গেম পছন্দ করে, তবে আমরা ব্যর্থ হব। অবশেষে, যদি আমরা বর্তমানে বেঁচেবর্তে বনভূমি অক্ষত রাখি, নদীতীর, সমুদ্রের তটকে বুঝতে পারি, মানুষ ছাড়াও অপরাপর প্রাণীর ন্যূনতম চাহিদাটুকু উপলব্ধি করতে পারি, তাহলে ভবিষ্যৎ প্রজন্ম অন্তত তাদের কম্পিউটার গেম থেকে উঠে এমন একটি পৃথিবী দেখার বিকল্প পাবে যা মানুষের দ্বারা তৈরি করা হয়নি। যদি আমরা ধ্বংসই করি, তাহলে সেই পছন্দ বা ‘চয়েজ’ চিরতরে চলে যাবে।
পর্ব – ২১
পরিবেশ নামের এক বিকল্প সংস্কৃতির কথাকার
পরিবেশ ভাবনা আধুনিক বিশ্বে ও উত্তরাধুনিক একাডেমিক ভাবনায় একটি তাত্ত্বিক পরিসর। কিন্তু সাহিত্যে তার প্রয়োগ সবসময় সুচিন্তিত ‘থিয়োরি’র রকমে ছিল না। সাহিত্যিকের স্বতঃস্ফূর্ততাতেই পরিবেশ ভাবনা সৃষ্টিলগ্ন থেকে সাহিত্যের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকেছে। স্বাধীনতা পরবর্তীতে রাষ্ট্রের নতুন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ, ক্রমবর্ধমান বৈশ্বিক পরিবেশগত মানের অবনমন ভারতীয় সাহিত্যে একটি সচেতন মাত্রা যোগ করে। ফলে বিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধের শেষ থেকেই বাঙালী লেখকদের কাছে আর্থ সামাজিক পরিস্থিতির বিচারে সুস্থ জীবনযাত্রার উপযোগী পরিবেশ মুখ্য আলোচ্য বিষয় হয়ে উঠেছে। শরদিন্দু সাহা এই সময়ের একজন ভিন্ন ধারার লেখক। তাঁর রচনায় ‘পরিবেশ’ বলতে সমুদ্রের গর্জন, সবুজ গাছের পাতার হলদে হয়ে যাওয়ার মর্মর বেদনা, রাস্তা-মাঠ-ময়দানের ধুলো, যন্ত্রদানব আর প্রচন্ড দাবদাহে তেতো বাতাসের উচাটনে ক্লান্ত বিধ্বস্ত প্রাণের কথা আছে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার প্রদত্ত ‘স্বাস্থ্য’ বিষয়ক সংজ্ঞা যেমন শরীরকে ছাড়িয়ে মানসিক সুস্থতার লক্ষণকেও ধারণ করে, তেমনই পরিবেশ অর্থে আক্ষরিক সবুজের বাইরেও ব্যাপকতর পরিবেশ ভাবনা লেখক শরদিন্দু সাহার লেখালেখিতে প্রকাশিত। সর্ব অর্থেই সুস্থ পরিবেশের স্পৃহা সেখানে রয়েছে। তাঁর স্পষ্ট বক্তব্য-
দূষণ ছড়ানোর যাবতীয় আয়োজন সাঙ্গ করে এখন বেচারা তৃতীয় বিশ্বের দিকে নজর পড়েছে…মনে রাখা ভাল, আপাত জয়লাভের কৌশলে ফন্দি ফিকিরে, অতিমাত্রায় আগ্রাসী মনোভাব আর উল্লাসে কেউ কেউ আবার নিজেদের ধ্বংসের বীজ রোপন করছেন না তো হে পরিবেশ সুরক্ষার ছদ্ম কারবারী, বিশ্ববাজারের সামন্ত প্রভুরা। ভুলে গেলে চলবে না, মানুষে মানুষে ভেদাভেদ তৈরী করে, রাজনৈতিক সীমানায় কাজিয়ার ইন্দন যুগিয়ে, অর্থনৈতিক শোষণ চালিয়ে, বিশ্বায়নের নামে এই পরিবেশের ভারসাম্য নষ্টের খেসারত কোন একদিন অনেক মূল্য দিয়ে শোধ করতে হতে পারে, তখন আবার আজকের এই হতভাগ্য দরিদ্র বিশ্বলোকদের করুণার পাত্র হতে লজ্জা হবে না তো!
লেখকের ‘হাওয়া বদলে যায়’ গল্পগ্রন্থে বদলে যাওয়া সময়, পৃথিবী, আধুনিকতা ও উন্নয়নের নতুন সংজ্ঞার কালে রামাশীষ, আলোময়ী, শম্ভুর মায়ের মতো একগুচ্ছ চরিত্রের দেখা পাই। তারা হঠাৎ বদলে যাওয়া দুনিয়ায় পা রাখতে কলজে ছেঁড়ার কষ্ট পায়, তবু তো চেষ্টা চালাতে হয়। তারা কেউ হয়ে যায় ঐতিহ্যের ধারক ও রক্ষক, কেউ উবে যাওয়া পেশার সংগ্রহশালা, কেউ বা প্রকৃতির রূপ পরিবর্তনের প্রাক্কালীন প্রাকৃতিক ইতিহাসের চরিত্র। শম্ভুর মা শুকনো নদীর এপারে অপেক্ষা করে থাকে গাঙ ভাসানো নদীর স্মৃতি আগলে। ‘আলোময়ীর পাঠশালা’ গল্পে দেখব শহরের পুঁজির গন্ধ, ড্রেনের ময়লার অপ্রীতিকর গন্ধ, খারাপ সময়ের সঙ্কটপূর্ণ গন্ধ আলোময়ীকে আচ্ছন্ন ও আক্রান্ত করতে পারে না। সে খারাপ গন্ধকে ভালো গন্ধ দিয়ে তাড়াতে পারে। তার ভালো গন্ধের আশ্লেষ তৈরি হয় পুরনো বাড়ি, অযাচিত আগাছা, মিষ্টি হাওয়ার গন্ধে। পুরনো ইট-কাঠ-পাথরে সে পুরনো সংস্কৃতিকে খুঁজে পায়, তাকে শ্রদ্ধা জানায়, তাতে বাঁচতে চায়। এই পুরনো গন্ধের উত্তরাধিকারকে সে হারাতে চায় না। পুরনোকে একেবারে উৎখাত করে নতুনকে আশ্রয় নিতে হচ্ছে- এটা আলোময়ী মানতে পারেনি। বরং চেয়েছে যে পুরনোর উত্তরাধিকারে ‘নতুন’ আসুক। বিশ্বায়নের নয়া রূপ, নগরায়নের অস্বস্তিকর দিক এবং পুরনো ঐতিহ্য, পুরনো কলকাতার ঘ্রাণ পাশাপাশি চলা রেললাইনের মতোই উঠে এসেছে।
‘মরা গাঙে বান ডেকেছে’ গল্পে মুণ্ডেশ্বরী নদীকে কেন্দ্র করে জনপদ, গ্রাম সংস্কৃতি, আধুনিকতার সংকট, ভোগের নতুন নতুন ক্ষেত্র, শিকড়ের সন্ধানের কথা আছে। পঞ্চাননের সময়ে সেই গাঁয়ের লোকজন জাল কাঁধে নদীর পাড় ধরে সারি সারি দাঁড়াত, ঢোল-কাঁসর বাজত, পদ্মা জাল সেলাই করত। কিন্তু যখন নদীতে ধস হয়, বাড়ি-ঘর নদীগর্ভে যায়, ফসলের চিন্তায় আর উপোসি পরিবারের শুকনো মুখের চিন্তায় ঘুম আসে না। যে নদী তার গর্ভে ফসল, ঘর-বাড়ি ঢুকিয়ে নেয়, সেই নদীই শুকিয়ে গেলে নদীর খাত বরাবর জনপদের পরিবার পার হয়ে যায়। আর গাছগুলো হেসে তাদের আবার ডেকে নেয়। পঞ্চানন মাটি কেটে বাঁধ তেরি করেছিল, তাদের জীবন গাছের হলুদ থেকে সবুজ হওয়া আর সবুজ থেকে হলুদ হওয়ার জীবন। নদীর রুক্ষতায় নদীগর্ভের কাছে আর যখন নদী জলে ভরা থাকে তখন নদীগর্ভের ঊর্ধ্বে ঘর বানাতে হয়। তাপসরা নদীকে নিয়ে যতই দার্শনিক কথা, সুখ খোঁজার কথা, রোমান্টিকতার কথা বলতে চান না কেন, শম্ভুরা জানে এই নদী তাদের কাছে কী। বাঁধ করা আর বাঁধ কাটা, নদী আসে আর নদী যায়- ওর ঘর ছেড়ে নীচে নামে, আবার নীচ থেকে ঘরে চলে যায়; পূর্বপুরুষের গল্পটা শম্ভুর নিজের গল্পই হয়ে যায়। অপূর্ব কেবল তার মনের পরিবর্তন খেয়াল করে। সে ক্রমে বোঝে যে নদী আছে বলেই ব্যবসা, মানুষ, একটি গ্রামের বিশ্বাস-সংস্কৃতি তথা ‘Folk’ গড়ে ওঠে; এমনকি ভেসে যায় ‘মিথ’-এর ভেলাও। আসলে নদী মানে মাটি, জনপদ, গাছ-গাছালি, মেঘ, বৃষ্টি, জল, আলো নিয়ে কোনো স্থানের ভূ-প্রাকৃতিক ও সাংস্কৃতিক সৌন্দর্য। নদীটা অপূর্ব’র কাছে যৌবনবতী নারী, পরে শম্ভুর কাছে তার নিজের মায়ের মতো হয়ে ওঠে।
শরদিন্দু সাহা’র ‘চৈতন্য প্রাঙ্গণ’ আরেকটি গল্পগ্রন্থ, যেখানে সঙ্কটের কাল রয়েছে। তবে সেখানে পরিবেশগত বিপন্নতা ছাড়াও মিশে গেছে মানব সমাজের বিবিধ বিপন্নতার দিকগুলি। নিজেকে যেমন চিনতে পারা যাচ্ছে না, হারিয়ে যাচ্ছে সম্পর্ক নির্ণয়ের সূত্রগুলো, পণ্যায়িত হচ্ছে অনুভূতিও। ‘অচিন অপেরা’য় মেঘ-চন্দনা-পুঁইমাচা সহ এমন দুনিয়ায় যেতে চাওয়ার কথা আছে যা আধুনিক দুনিয়ায় কেউ দেখাতে চায় না বা বলা যায় ওই আধুনিক দুনিয়াটাই বিছিন্ন। গল্পের শিশু চরিত্রটি তার মনকে ছোট হতে দিতে চায় না, ভাবনাগুলোকে মরতে দিতে চায় না- বর্তমান একবিংশ শতকীয় অত্যাধুনিকেরা যা হারিয়ে ফেলেছে। বাচ্চাটি সঙ্কট কালেও তার চৈতন্যকে বদলাতে দেয় না, ঘাসের মঞ্জরি, প্রজাপতিতে, তাজা ফুলের গন্ধে বেঁচে উঠতে চায়। যারা জায়গা দখলের লোভে জোরে দৌঁড়ায়, তাদের ত্যাগ করতে চায়। তারা চৈতন্যের রূপ নয়, বরং ‘ফ্যাশন শো’-এর র্যাম্প ওয়াক দেখতে চায়। চারপাশে যান্ত্রিক আর অযান্ত্রিক সত্তা, উন্নত জীবনযাত্রার ছায়ার পেছনে ছোটা সমাজের কঙ্কালসার ছবি, মারণ রোগের বিষ- তারই মাঝে দাঁড়িয়ে একজন মানুষ (‘গুনাহর পটভূমি’)। সে প্রত্যাখ্যান করতে শিখে নেয় সমাজের আর পাঁচজনের বানানো দূষিত পরিবেশকে।
‘উজানি মঙ্গল’ উপন্যাসের কেন্দ্রীয় চরিত্র আক্কাস আলি, তার স্বভাব ও জীবন-যাপন প্রণালী অদ্ভুত। ‘না-মানুষ’ বস্তুর সঙ্গে সহজেই সে ভাষা আদান-প্রদান করতে পারে, সেটি তার অতীন্দ্রিয় ও স্বাভাবিক স্বত:স্ফূর্ত ক্ষমতা। সে বাস্তবতায় বাস করলেও পরাবাস্তবতায় সহজেই বিচরণ করতে পারে। উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ে এক শকুনির দেখা মেলে, যে সামাজিক বিশ্বাসে অমঙ্গলের প্রতীক। লালিত এই অন্ধ বিশ্বাসকে আঘাত করে লেখকের শকুনি চরিত্রের নবনির্মাণ। শকুনি মানব সমাজের আত্ম হানাহানিতে ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ভয়ে মানুষের জন্য নিদান খোঁজে। ষোল বিঘা, ওলাইচণ্ডীকে রক্ষা করতে সে আক্কাসের সহকারীও বটে। যে জংলা ঘাস জলা ছিল সেগুলো বুজে ছোট ছোট জলায় ভাগ হয়ে হয় ষোল বিঘে জমি। নোংরা আবর্জনা বেড়ে যাচ্ছে সেখানে, যন্ত্র দিয়ে জল বের করে ওলাইচণ্ডীর মাঠ জাগিয়ে তোলা হবে। শকুনের অভিমান ছিল মানুষ জাতির প্রতি, প্রচ্ছন্ন দেমাকও ছিল কেননা আসমান জমিন মিলে তার সংসার। তাকে হুঁশিয়ারি দেওয়ার ক্ষমতা কেবল আক্কাসের আছে, কোনো ভূমি আগ্রাসীদের তথা লোভী মানুষের নেই। শকুনি এরকম লোভীর প্রতিনিধি হিসেবে ভোম্বলকে দেখে, যার শাসনে তটস্থ জীবকুল। ভোম্বলদের বকলমে বাঁকা পথের কারবারিরা এলাকায় খুন-ঝামেলা চালায় ও পারস্পরিকতায় জীবন যাপনের পরিবর্তে অসুস্থ খাদ্য-খাদকের বাস্তুতন্ত্রীয় সম্পর্ক গড়ে তোলে। আক্কাস আলি ভোম্বলকে যন্ত্রদানবের সমার্থক হিসেবে দেখে, সে প্রকৃতিকে নিজের প্রয়োজনে ব্যবহার করে চলে মাত্র ও মাটি কেটে নিয়ে গিয়ে অন্যত্র বসতি নির্মাণ করে তার হর্তা-কর্তা-বিধাতা হয়ে উঠতে চায়। অথচ স্বচ্ছ হয়ে ওঠে আক্কাসের মুখ। ঘৃণার রাজনীতি পুড়িয়ে ফেলতে পারেনি তার সুপ্ত ইচ্ছাকে- প্রকৃতি কেন্দ্রিক বাংলার স্বপ্নকে, প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিকতায় মানুষের বাঁচার স্বপ্নকে। মানুষের আগুপিছু হওয়ার খাবলা খাবলি তাকে বিব্রত করে। আধুনিক গোছানো সমাজ অগোছালো প্রকৃতিকে দূরে ঠেলেছে- তার বিরুদ্ধে আক্কাস বলতে চায়।
শকুনি দম্পতিরা দেখে কারা যেন তাদের বসবাসের জন্য বরাদ্দ খোঁদল বুজিয়ে ফেলেছে। এমনকি ভাগাড়েতে পড়া পশুগুলোর চামড়াও তুলে নিচ্ছে ব্যবসায়িক দরকারে। আক্কাস আলি যখন তার বুঁদ হওয়া খেয়ালে ধরে ফেলতে চায় ষোলো বিঘা আর ওলাইয়ের জীবনচরিতের খেয়ালখুশি তখন শকুনি-মানুষের মিতালি হয়। এলাকার নিষ্পাপ একটি মেয়ে খেলার ছলে চোখ বন্ধ করে গাছে গাছে মিতালির স্বপ্ন দেখে। আক্কাস আলিও সেই বাংলা চায় যেখানে ঘরে ঘরে বাতি জ্বলবে, পাখির ডাক শোনা যাবে, শস্য দানার গন্ধ থাকবে। সে হিসাব খোঁজে কবে মাটির সোঁদা গন্ধ পৃথিবীময় ছড়াবে, আবার নরম আলো উঁকি দেবে বাঁশ বাগানে, জোছনা সুন্দরীর নাচ ছড়িয়ে পড়বে কল কল করা টইটুম্বুর জলে। সে মগডালে পাখির ঝাঁক খেয়াল করে, তাদের রঙবেরঙ পালকের ঐশ্বর্যকে লুকিয়ে রাখতে চায় বিপন্নতার কালের স্পর্শ থেকে। উদ্বাস্তু পাড়াতেও খাদ্য খাদকের সুষ্ঠু বাস্তুতন্ত্র তৈরি করতে চায়। যেন ওলাইচণ্ডী আক্কাস-এর কাছে আর্তি জানায়- “ওরা আমার বুকে জমে যাওয়া নীল জল ঘোলাটে করবে, ভ্রষ্ট করে দেবে আমার গর্ভ, আমার ভ্রূণের করবে অপমান।” আলিও শপথ নেয় নীলকন্ঠ হওয়ার, সে বিষাক্ত হতে দেবে না ক্ষীরোদ সাগর রূপী প্রকৃতিকে। তার মনে হয় শত্রুরা কুমারী প্রকৃতিকে ‘প্রসেসিং’ করে তথা ধর্ষণ করে যে রূপ দিয়েছে তা বেশ্যার রূপ। তাকে পুঁজি বানিয়ে ওরা ব্যবসা ফাঁদবে। মায়ের মতো ওলাইচণ্ডিকে জড়িয়ে ধরলে চরিত্রায়িত ওলাইচণ্ডিও কেঁদে ফেলে আলির বুকে। পৃথিবীর সমস্ত প্রাকৃতিক সম্পদকে পকেটবন্দি করে যারা রাজত্ব কায়েম করার সূত্রে ‘সোশ্যাল হায়ারার্কি’তে অবস্থান করে, ব্যক্তিগত মুনাফায় ফুলে ফেঁপে ওঠে, তাদের অত্যাচার ও আধিপত্যের বিপরীতে বিদ্রোহ তৈরি হয়।
বিপন্নতা ও সংকটকালীন নিরর্থকতায় মানুষও যেন নিজেকে চেনার সূত্রগুলো হারিয়ে ফেলেছে- “সেলাই মেশিনের লোহার চাকতিতে অভ্যস্ত হয়ে নিজেদের দক্ষতা বেচে দেয়।” পৌনপুনিকতার ক্লান্তি, হতাশার ছবিটি বড় সুন্দরভাবে নির্মিত হয়েছে। তারা হয়ে গেছে যেন বন্ধ্যা-নিষ্কর্মা-চুপ। ফলে শকুনিগুলো এতকাল দেখে শুনে বোকা হয়ে থাকলেও এবারে শুরু করেছে চেঁচামেচি। এবার মাঠ কথা বলবে, গাছ কথা বলবে, আজ বাদে কাল তারা আর আলিতে মিলে যেন এক বিকল্প পথের খোঁজ লাগিয়ে দেয়। তিল তিল করে বেঁচে থাকার যে পথ তৈরি আছে বনৌষধির মতো, তার পুনরাবৃত্তি ঘটিয়ে বুঝতে চেয়েছে যে হিংসা ও আধিপত্যের পথ সামনে খোলা রয়েছে তা একমাত্র পথ কিনা। আলিরও ডানা গজায় শকুনির মতো। যখন ষোলো বিঘা আর ওলাইচণ্ডির সবাই যন্ত্রচালিত মৃত তখন আক্কাস আলি দিব্যি বেঁচে থাকে। কারণ তার অবলম্বিত ভাবনায় ও জীবনপথে জাত-বেজাতের বিচার ও বিভাজন আলাদা করে মাথা ব্যথার কারণ হয়ে দাঁড়ায় না। কবরস্থানের বটগাছ, দূরের কৃষ্ণচূড়া অনেককাল চুপচাপ বসে দেখেছে, এবার কথা বলবে। ওদের সঙ্গে আলির রীতিমতো কথা হয়- সংগ্রাম শুরু হলো বলে; চলতি সমসাময়িক ইতিহাসের এক পাল্টা ইতিহাস তারা রচনা করবে। এখন বিপন্নতার কাল, ভূমি শিথিল, বীজ বুনে ভূমিকে শক্ত আর দৃঢ় করতে গেলেও পেতে হবে সেই বীজের উত্তরাধিকার। অনেক সৃষ্টি, ধ্বংস আর পুনরায় সৃষ্টির মধ্য দিয়ে অগোছালো পদযাত্রায় তৈরি হবে পরবর্তী অনুসন্ধানের পুরোহিত। শিল্পী যেমন ভূমির সাজঘরে আলো ফেলে পরীক্ষা করে বীজ বুনতে চেয়ে, তেমনি বীজও তো খুঁজে ফেরে কোথায় সে তার জন্মের বার্তাকে বয়ে এনে রোপণ করবে! যদিও আনচান মোহ আর গতি পরিবর্তনের খেলায় উন্মত্ত পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে মনে হয় মাটির কোলে লুটিয়ে পড়বে বীজ, তবু ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে না। শিল্পী হাল ধরে। শিল্পী হিসেবে মানুষ রূপকল্প নির্মাণ করতে গিয়ে নিজের জমি মজবুত করতে চেয়েছে, স্বার্থের কথা ভেবেছে, শাবল-খন্তা-কোদাল-কাটারি নিয়ে দলে দলে অভিযান চালিয়েছে। উন্নয়নের পথে সেই শিল্পীর দল শুধু সৃষ্টির বদলে উৎপাদনের উন্মাদনায় এমনই বুঁদ হয়ে থেকেছে যে পরিমন্ডলকে বশে আনার দক্ষতা রপ্ত করেছে। ফলে বীজ অভুক্ত থাকে দিনমানে, অশ্রুতে চোখ বোজে, ভূমি ওজন করে নেয় অবশিষ্ট যৌবনের কতটুকু ‘ধারণ ক্ষমতা’ নিঃশেষ করলে তার ধারণ ক্ষমতা লোপ পাবে। কিন্তু দেখা যায় বীজ তার সুস্থির প্রদক্ষিণে জেগে থাকে।
পর্ব – ২২
পরিবেশবাদী ভারতীয় কথাসাহিত্য ধারা
আঠারো ও উনিশ শতক জুড়ে পাশ্চাত্যের সাহিত্যে পরিবেশভাবনা এসেছে কখনও ভ্রমণকাহিনীতে, কখনও বা স্থানীয় প্রাকৃতিক বিবৃতির প্রসঙ্গে। যেমন ১৭৫৯ সালে গিলবার্ট হোয়াইট ‘ন্যাচারাল হিস্ট্রি অফ সেলবোর্নে’ ইংল্যান্ডের একটি গ্রামের গাছ, পাখিদের জীবনচক্র, ঋতুভেদে ও জলবায়ুর প্রভাবে তার পরিবর্তন নিয়ে লেখেন। আবার প্রকৃতিবিদ বার্টরাম তাঁর ভ্রমণকাহিনীতে (বার্টরাম’স ট্রাভেলস’,১৭৯১) গাছ, পাখি ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদের নিখুঁত বিবরণ দেন। জেমস ফেনিমোর কুপার রচিত ‘দ্য পাইওনিয়রস’ (১৮২৩) সম্ভবত প্রথম উপন্যাস যাতে প্রকৃতি প্রাধান্য পায়। লেখক নিউইয়র্কের অটসিগো লেকের বিপর্যস্ত বাস্তুতন্ত্র, টেম্পলটন শহরের প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ ও তার যথাযথ ব্যবহার প্রসঙ্গ ছাড়াও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য, প্রকৃতির চূড়ান্ত বিপজ্জনক দিকগুলিও রক্ষণাবেক্ষণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বলেন। হেনরি ডেভিড থর্যেউ তাঁর ‘ওয়াল্ডেন অর লাইফ ইন দ্য উডস’ (১৮৫৪)-এ দেখান যে বাঁচার উপযোগী যৎকিঞ্চিৎটুকু নিয়েই জীবনধারণ করা যায়, কিন্তু প্রকৃতির সান্নিধ্য আবশ্যকীয় শর্ত। মধ্য ক্যালিফোর্নিয়ার সিয়েরা পর্বতমালার জীববৈচিত্র্য, ইয়োসমাইট উপত্যকার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য নিয়ে জন ম্যুর ১৯১১ সালে লেখেন ‘মাই সামার ইন সিয়েরা’। ১৯৫৭ সালে রচিত ‘অন দি বিচ’ উপন্যাসে নিল শ্যুট পরমাণু যুদ্ধ পরবর্তী তেজস্ক্রিয় মেঘ ও তা থেকে হওয়া বৃষ্টিতে মানুষের অবধারিত মৃত্যু ও পলায়নের প্রসঙ্গ উত্থাপন করেছেন।
রাসায়নিক শিল্পের বিস্তার ও কীটনাশকের ব্যাপক ব্যবহারে পরিবেশের ওপর তার কুপ্রভাব নিয়ে বিংশ শতাব্দীতে র্যাচেল কারসন ‘সাইলেন্ট স্প্রিং’ (১৯৬২) লেখেন। ‘আ ফেবেল ফর টুমরো’ অধ্যায়ে দেখানো হয় আমেরিকার প্রকৃতিলগ্ন জীবনের প্রতিমা-প্রতীকগুলি ছিন্নভিন্ন, সমৃদ্ধ খামার, সবুজ ও প্রাণীরা ব্যাধিতে আক্রান্ত। ডেল স্মিথ রচিত ‘হোয়াট দ্য ওরাংওটাং টোল্ড এলিস’ (২০১১) এবং জে.ও ক্যালহানের ‘দ্য স্পিরিট অফ দ্য গ্রেট ওক’ উপন্যাস একবিংশ শতাব্দীতে পরিবেশ বিপন্নতায় লুপ্তপ্রায় প্রাণী ও বৃক্ষ প্রজাতি নিয়ে সচেতনতাকে সূচিত করে। মার্সেল থিরোর ‘ফার নর্থ’ উপন্যাসে (২০১০) সাইবেরিয়ান নন্দনকাননের ধ্বংস ও তাপমাত্রা বৃদ্ধিতে বায়ুর ঘনত্ব কমে যাওয়ার মত পরিবেশগত সমস্যাগুলি এসেছে। ‘ফ্লাইট বিহেভিয়ারে’ (২০১২) বারবারা কিংসলভার বিশ্ব-উষ্ণায়নের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরল প্রজাতির প্রজাপতিদের আবাসস্থল বদল এবং ঝাঁকে ঝাঁকে মৃত্যুর সংবাদ দেন। যুদ্ধবিধ্বস্ত, খরাবিধ্বস্ত দুনিয়ায় জলের অভাব, তার সংরক্ষণকে কেন্দ্র করে রচিত ‘মেমরি অফ ওয়াটার’ (২০১৪)। প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও জীববৈচিত্র্যের সমাহারে পূর্ণ নাইজেরিয়ান ডেল্টা প্রাকৃতিক তেলেরও ভান্ডার। ফলে তেলের খনি আবিষ্কার ও তার পণ্যায়ন সমুদ্রের জলকে, ডেল্টার ইকোসিস্টেমকে কিভাবে নষ্ট করে, তার আখ্যান ‘অয়েল অন ওয়াটার’ (২০১৪)। উক্ত শতকের গোড়া থেকেই আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে নানা ভাবে পরিবেশমূলক চিন্তাভাবনা শুরু হয়েছিল জোনাথান স্কিনারের ইকোপোয়েটিকস পত্রিকায় (২০০১-০৫) কাব্যচর্চার মাধ্যমে। ক্রমে পরিবেশকেন্দ্রিক সাহিত্যচর্চা বিভিন্ন দেশে ছড়িয়ে পড়ে।
গত ত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে ভারতীয় সাহিত্যের ‘ইকো টেক্সট’গুলি আলাদা করে জায়গা করে নিয়েছে। হিন্দি ও অসমিয়া সাহিত্যে পঞ্চাশের দশক থেকেই পরিবেশবাদী সাহিত্য রচনা শুরু হলেও ভারতে প্রাতিষ্ঠানিভাবে তা শুরু হয় ১৯৮০তে নির্মল সালভামনির ‘তামিল ইকো পোয়েটিক্সে’র মাধ্যমে (thinai/thinnai), ১৯৯৬ সালে তিনটি বুকলেট প্রকাশ করে তিনি ‘ইকোলিটারেচার’ চর্চা শুরু করেন। ২০০৫ সাল থেকে ‘অরগ্যানাইজেশন ফর দি স্টাডি অফ লিটারেচার এন্ড এনভায়রনমেন্ট (OSLE) প্রতিষ্ঠানটি ভারতীয় পরিসরে পরিবেশবাদী সভা, সেমিনারের আয়োজন ও লেখাপত্র প্রকাশ করতে থাকে। ক্রমে ভারতীয় পরিসরে বিবিধ ভাষার সাহিত্যে তার জোয়ার ছড়িয়ে পড়ে। বোড়ো লেখক নীলকমল ব্রহ্মের (১৯৪৪-১৯৯৯) ‘ভোঁতা তলোয়ার’ গল্পে অরণ্যসম্পদ ও প্রাণীরক্ষার দায়িত্বে থাকা বনমন্ত্রীকে খুশি করতে তারই খাবার পাতে শিকার করা গর্ভবতী হরিণের মাংস পরিবেশনের কথা পাই। পরিবেশ সঙ্কটের সঙ্গে বোড়োদের নিজস্ব অস্তিত্ব ও সংস্কৃতির সঙ্কট একত্রিত হয়ে এই গল্প আমাদের শেখায় পশুপাখি, গাছপালা, ঝড়-জঙ্গল, নুড়িপাথর ইত্যাদি সবকিছুই একসময়ে শেষ হবে ধরে নিয়ে আগে থেকেই তার ভোগলীলায় মেতে ওঠার জীবনচর্যা কখনোই কাঙ্খিত নয়। হিন্দি গল্পকার রামকুমারের ‘চেরী গাছ’ গল্পে ঠিকেদারেরা যখন একটি চেরী গাছকে ব্যবসায়িক প্রয়োজনে লাগায় তখন গাছের শূন্য শাখা কাঁপিয়ে নিঃশ্বাস নেওয়া যন্ত্রণায় সঙ্গ দিতে দেখা যায় একটি মেয়েকে, যে গাছ থেকে ফুল ফল না ছেঁড়ার শিক্ষায় বিশ্বাস করে) কৈলাস বনবাসীর (১৯৬৫) ‘এই সময়টা পাখিদের জন্য’ গল্পে (বহুপণ্যের বাজারে একজন ধানের ছড়া বিক্রেতা (নারী) কথককে জানায় যে ছড়াটি কিনলে পাখিরা ধান খেতে আসবে আর ক্রেতার পুণ্য হবে। পণ্যায়ন ও বিজ্ঞাপনের ভিড়ে নিমেষেই মাঙ্গলিক একটি ছবি নির্মিত হয় ও নারীটি প্রকৃতির প্রতিনিধি হয়ে ওঠে। পরমুহূর্তে একদল তোলাবাজদের বাহুবলে তার মত মাটির হাঁড়ি ইত্যাদি পসার নিয়ে বসা অন্য নারীদেরও পিষ্ট হতে দেখে কখকের মনে হয় এই সময়ে পাখিদের জন্য কেউ ভাবছেনা, তারা ভয়ে লুকিয়ে পড়ছে। সিন্ধী গল্পকার ঈশ্বর ভারতীর (১৯৪২) ‘পাখিরা’ গল্পে পাখিদের বাসা বানানোর কথা, সে বসতি তৈরিতে মানুষের সাহায্য করার প্রয়োজনীয়তা ও পশুপাখিদের প্রতি দয়া-মায়ার মত সুকুমার বৃত্তিকে জীবনচর্যার অন্তর্ভুক্ত করার কথা বলা আছে।
ইন্দ্রা বাসওয়ানীর (১৯৩৬) ‘শুধুই জল’ গল্পে মহানগরের জনবিস্ফোরণ, তাদের চাহিদা মেটাতে গিয়ে জলস্তরের ওপর বাড়তি চাপ ও অর্থের বিনিময়ে এই অমূল্য প্রাকৃতিক সম্পদের মালিকানা এক শ্রেণির মুষ্টিবদ্ধ হওয়ায় ঘরে ঘরে জলবন্টনে অসমতার কথা পাই। হিন্দি লেখক ফণীশ্বরনাথ রেণুর ‘পরতি পরিকথা’ (১৯৫৭) উপন্যাসে কোশী নদীর বন্যাকে সম্বল করে পতিত অনুর্বর গ্রামের উর্বরায়ণ ও বনায়নের প্রকল্প গ্রহণের মাধ্যমে সেই জমি গ্রামের গরীব মানুষদের মধ্যে বন্টন করার প্রসঙ্গ আছে। কেন্দ্রীয় চরিত্র জিতেন এহেন উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে গ্রামের বাস্তুতন্ত্র রক্ষার পাশাপাশি প্রকৃতিনির্ভর মানুষের উন্নতি নিশ্চিত করতে চেয়েছে, পরিবেশ ও উন্নয়ন যে পরস্পরবিরোধী না সেটা প্রমাণ করতে পেরেছে। রামদর্শ মিশ্রের ‘সুখতা হুয়া তালাব’ (২০১৬) উপন্যাসে দীঘি-পুকুরের ওপর নির্ভর করে থাকা গ্রামের ‘ইকোসিস্টেম’ ভেঙে পড়ার কথা আছে ভারতে জল সংরক্ষণের প্রাচীন ঐতিহ্যবাহী কৌশলগুলির অন্যতম স্থানীয় পুকুর শুকিয়ে যাওয়ার ফলে। গ্রামের আঞ্চলিক জল সমস্যার পাশাপাশি আগামী ভবিষ্যতে মহানগরীর জন্যেও যে জলসঙ্কট একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হয়ে উঠবে, সে সতর্ক বার্তাও এই আখ্যান দেয়) অসমিয়া লেখক মহিম বড়ুয়ার ‘এখন নদীর মৃত্যু’ গল্পে নওগাঁর মধ্য দিয়ে প্রবাহিত কলঙ্গ নদীর বক্ষে স্বার্থান্বেষী মানুষদের জন্য বাঁধ নির্মাণে নদীর ক্ষতি হওয়ার প্রসঙ্গ আছে। অপূর্ব কুমার শর্মার ‘বাঘে তাপুর রাতি গল্পে বাঘ সংরক্ষণের প্রয়োজনীয়তা, সচেতনতা প্রসঙ্গের পাশাপাশি প্রাণীবৈচিত্র্য বিলুপ্তিতে মানুষের ভূমিকা নিয়ে বলা হয়েছো গোবিন কুমার খাউন্ডের ‘রুময়াং’ (২০১৬) উপন্যাসে ভারতের ‘বনমানুষ’ খ্যাত যাদব পায়েং এর কথা আছে, যিনি কয়েক দশক ধরে ব্রহ্মপুত্র নদীর বালুকাময় তীরে গাছ লাগিয়ে তার যত্ন করে প্রায় একটি সংরক্ষিত অরণ্য গড়ে তোলে।
অনুরাধা শর্মা পূজারীর ‘ইয়াত এখন অরণ্য আছিল’ (২০১৬) উপন্যাসটি গুয়াহাটির আমচাং রিজার্ভ ফরেস্ট উচ্ছেদের পটভূমিতে লেখা, এখানে মানুষ, প্রকৃতি ও নগর জীবনের দ্বন্দ্বের কথা আছে। এছাড়া প্রভাত গোস্বামীর ‘শুকুলা হাতির খোঁজ’ (২০১২) উপন্যাসে হাতি ও অসমের খিলঞ্জীয়া জনগোষ্ঠীর বর্তমান সঙ্কটাপন্ন পরিস্থিতি ফুটে উঠেছে। আধুনিক সভ্যতায় হাতি-মানুষ সম্পর্কে সংঘাতের মাঝে তাদের সহাবস্থানের দৃষ্টান্ত খাঁড়া করে হাতি সংরক্ষণের দায়িত্ব নেওয়ার প্রয়োজনীয়তার কথা বলা আছে। পংকজ গোবিন্দের ‘চরাই চুবুরি’ (২০১৬) অরণ্য সংরক্ষণ ও ইকোট্যুরিজম নিয়ে লেখা। ইন্দ্র সিনহার ‘এনিমেলস পিউপল’ (২০০৭ সাল) উপন্যাস ১৯৮৪ সালে ভূপালের গ্যাস দুর্ঘটনা ও পরিবেশে তার ভয়ানক প্রভাবকে কেন্দ্র করে লেখা। বিদেশী পুঁজিতে নির্মিত কীটনাশক তৈরির কারখানা (ইউনিয়ন কার্বাইড ইন্ডিয়া লিমিটেড) থেকে নির্গত ক্ষতিকর গ্যাস পরবর্তী কয়েক প্রজন্ম পর্যন্তও মানবশরীরে তার প্রভাবের চিহ্ন রেখেছিল। আখ্যানের কথক উল্লেখিত দুর্ঘটনায় কোনোক্রমে বেঁচে গেলেও বিষাক্ত পরিবেশের শিকার হয়, মেরুদণ্ড বেঁকে গিয়ে তার শরীরের সাধারণ স্বাভাবিক গঠনটি চারপায়ে চলা পশুর মত হয়। প্রকৃতি ও তার খেয়ালখুশিকে প্রযুক্তি কিভাবে হাতের মুঠোয় নেওয়ার চেষ্টা চালাচ্ছে, তারই দলিল বন্দনা শিবার ‘স্টোলেন হার্ভেস্ট’ (২০০০সাল) উপন্যাস।
যে বীজ, ফসল, গাছ, জীববৈচিত্র্যের দায়িত্ব প্রকৃতির নিজের হাতে ও কিছুটা চাষী, অরণ্যচারী গোষ্ঠীর হাতে রক্ষিত হত, পুঁজিবাদ এবং কর্পোরেট মস্তিষ্ক সেসব চুরি করতে উদ্যত। সে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং এর মাধ্যমে বীজের পেটেন্ট প্রাপ্ত, ফলনশীলতা বৃদ্ধি করা ও সংরক্ষণের নামে প্রযুক্ত মাত্রাতিরিক্ত কীটনাশক, রাসায়নিক পদার্থ খাদ্যচক্রে প্রবেশ করে পৃথিবীব্যাপী সব পরিবেশের সব ধরনের জীবজন্তুর উপর তীব্র প্রতিক্রিয়া ঘটাচ্ছে। অরণ্যের বৈচিত্র্য, তার মাটি- জল- বায়ুর স্বাস্থ্য সংরক্ষণের বিরুদ্ধে কাঁচামালের জন্য গাছ কেটে পাইন, ইউক্যালিপটাস জাতীয় গাছ রোপণে বনমহোৎসব পালন তার বিনোদন যাপন। গত একশো বছরে প্রকৃতির সঙ্গে পারস্পরিকতাহীনতায় জলের মত প্রাকৃতিক সম্পদের অভাব ও বিপন্নতা তামিল লেখক চো ধরমনের (১৯৯২সাল) ‘সুল’ উপন্যাসে এসেছে। জল ও জলাশয়ের সংরক্ষণ, সঞ্চিত জলভান্ডারের যথাযথ ব্যবহারের দিকে নজর দেওয়া এ উপন্যাসের বিষয়। লক্ষ্মী কান্নানের (২০১১সাল) ‘মুনিয়াক্কা’ গল্পে সন্তানপরিত্যক্ত বিধবা এক নারী চরিত্রকে পাই, যে মালিকের বাগানের গাছগুলোকে শোভাবর্ধক সৌন্দর্য্যমাত্র মনে করেনা, বরং তারা সন্তানের প্রতিমূর্তি হয়ে ওঠে। মালিকের দেওয়া ঘরের বদলে বাগানে কুঁড়ে ঘর তৈরি করে থাকে যাতে রাতের অন্ধকারে প্রকৃতির কালোর সঙ্গে মিলিত হওয়া যায়, গাছগুলোর মাথা হাওয়ায় উড়তে শুরু করলে তাদের জীবন্ত সত্তা বলে মনে হয় মুনিয়াক্কার। ‘নন্দনবন’ গল্পের বৃদ্ধ চরিত্রটি ঘন স্বাস্থ্যকর গাছপালা ও বিচিত্র ফুলের সামঞ্জস্যে তার বাগানকে নন্দন বনের মত সাজিয়ে তোলেন। সেখানে আসা চড়াই, কোকিল, ক্যানারি পাখির যত্ন ও ভরনপোষণও তিনি করে থাকেন। প্রকৃতির সঙ্গে নিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ এই বৃদ্ধের মৃত্যু হলে সন্তানেরা যখন সম্পত্তি নিয়ে ভাগবাটোয়ারাতে ব্যস্ত থাকে তখন ঐ পাখিরাই তার মৃতদেহ বহন করে নিয়ে যায় এবং লিলি, সালভিয়া, হিবিস্কাস ফুলেরা তার মৃত্যুর শোকসঙ্গীতে গলা মিলিয়ে স্বার্থপর সন্তানদের নীতিগত আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়।
বলা যায়, আজকের সময়ে এসে সচেতনভাবে নির্মিত পরিবেশবাদী কথাসাহিত্যের একটি বিস্তৃত ক্ষেত্র তৈরি হয়েছে। পরিবেশভাবনাকে কেন্দ্রে রেখে প্রকৃতি, সমাজ ও ব্যক্তি মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের সমগ্রতা নিয়ে বাংলায় এই ধরনের গল্পোপন্যাস রচনা শুরু হয়েছে গত ত্রিশ বছর ধরে। পরিবেশগত ভাবনাচিন্তার মূল কিছু প্রবণতায় নিম্নলিখিত উপবিভাগে ভাগ করা যায়-
- পরিবেশের বহুমাত্রিক দূষণ, প্রজাতির বিলুপ্তি ও বাস্তুতন্ত্রীয় ভারসাম্য বিনষ্টির ভয়াবহ বর্ণনা পাই—ক. কিন্নর রায়ের (১৯৫৬—) ‘অনন্তের পাখি’, ‘মেঘচোর’ (২০০৬); স্ব
খ. স্বপ্নময় চক্রবর্তীর (১৯৫১—) ‘শনি’, ‘ফুল ছোঁয়ানো’;
গ. অমিতাভ সমাজপতির ‘জলঙ্গি’ (২০১২);
ঘ. অমর মিত্রের ‘কলসপুর যাইনি’ (২০২০), ‘বিভূতিবাবুর দেশ’ (২০১১) ;
ঙ. অশোক তাঁতীর ‘ফুলেরা যেভাবে ফোটে’ (২০১০);
চ. জয়া মিত্রের (১৯৫০—) ‘দুই উদয়ের গল্প’;
ছ. সুকান্তি দত্তের ‘লেবুপাতার ঘ্রাণ’ (১৯৯৮);
জ. গৌর কারকের ‘ময়ূরের ডিম’;
ঝ. শুভংকর গুহর (১৯৫৬—) ‘ঋতুবদলের মরশুমে’, ‘পাখিরঙের বিশ্রামখানা’র (২০২০) মতো গল্পে। শত রোগের জীবাণু দেহে ধারণ করে সুকান্তি দত্তের (১৯৬৫—) ‘বিষমানব’ বিদ্রূপ করে তৃতীয় বিশ্বের পরিবেশ দূষণ, সচেতনতা-স্বাস্থ্যবিধি ও পরিচ্ছন্নতা নিয়ে আয়োজিত শৌখিন পরিবেশ সভাকে।
- প্রাকৃতিক সম্পদ ধ্বংস ও অপচয়ের বিরোধিতায় ভোগের চরিত্র পরিবর্তনের প্রয়াস পরিলক্ষিত হয় ক. কৃষ্ণেন্দু মুখোপাধ্যায়ের ‘তেষ্টা’ (২০১৯);
খ. অরিন্দম বসুর ‘শীতকাল আসবেনা’;
গ. সুকান্তি দত্তের ‘অযৌক্তিক আগাছা’ (২০০৮);
ঘ. শেখর বসুর ‘গাছ-মানুষ’ (১৯৮৬) গল্পে।
- প্রতিবেশ সংরক্ষণে বিকল্প ব্যবস্থা অনুসন্ধানের সুর আছে
ক. অরিন্দম বসুর (১৯৬৭—) ‘পাখি সব’;
খ. চিরঞ্জয় চক্রবর্তীর ‘জটায়ু’ (২০১৯) গল্পে।
গ. সুকান্ত গঙ্গোপাধ্যায়ের (১৯৬৭—) ‘পবিত্র বাগান’ গল্পে বটানির প্রফেসর সরস্বতী নদীর পলি পড়া উর্বর জমিতে কীটনাশক বা রাসায়নিক সারহীন ঔষধি গাছ ফলাতে গিয়ে দাবি করেন, যথার্থ অর্থে মানবসভ্যতার উন্নয়ন নতুন করে তার নার্সারি থেকেই শুরু হবে।
ঘ. সোহারাব হোসেনের ‘হ্যাঁ মানুষ অথবা কাকতাড়ুয়া’ গল্পের (২০০৫) প্রধান চরিত্র ধন্বন্তরি কবিরাজ হতে গিয়ে ‘বাংলার গাছ’ হয়ে ওঠে। এ ধরনের জীবনদর্শনগত উত্তরণ পরিবেশবাদের আদর্শ প্রভাবিত।
- উদ্ভিদ বা প্রাণীর সংরক্ষণে প্রকৃতির নিজস্ব অধিকারের দাবিতে
ক. প্রতিভা সরকারের ‘প্রেম’ (২০২০)
খ. মাহবুব লীনেনের ‘বনমজুর’ (২০২১) গল্পদুটি সমৃদ্ধ।
প্রাণী সংরক্ষণ আইনের ফাঁক গলে হাতি, রয়্যাল বেঙ্গল টাইগারের শিকার আর ‘বডি পার্টস’ পাচার, ক্রমাগত হরিণেরও চোরাশিকারে বাঘেদের সঙ্কটমুখী ‘সার্ভাইভাল রেট’ প্রসঙ্গের পাশাপাশি ‘প্রেম’ গল্পে পারুলের মতো চরিত্রেরা শেখায় আলোয়-বাতাসে-অরণ্যে-শস্যে সকলের সমান অধিকারের স্বীকৃতি।
- প্রকৃতিলগ্ন সংস্কৃতি, নৈতিকতা, মূল্যবোধ পুনরুদ্ধারের সুর প্রধান হয়ে ওঠে
ক. মন্দাক্রান্তা সেনের (১৯৭২—) ‘মালী’;
খ. বরুণ মাইতির ‘অ’ (২০১৯);
গ. অসীম ত্রিবেদীর ‘সিদ্ধান্ত’;
ঘ. অনিন্দিতা মন্ডলের ‘হেরে যাওয়ার গল্পে’ (২০২১)।
- পুঁজিবাদী উন্নয়নের স্বার্থে প্রাকৃতিক উপাদানে সমৃদ্ধ এলাকার জলবায়ু-উদ্ভিদ-পশুপাখির জীবনকে নষ্ট না করে তাকে সামাজিক, অর্থনৈতিকভাবে কেন্দ্রীকৃত করা এবং মানুষকে তার প্রতিবেশের সঙ্গে মিথষ্ক্রিয়ায় বাস করতে প্রভাবিত করার পরিকাঠামো রয়েছে
ক. সমরেশ মজুমদারের ‘হে বৃক্ষনাথ’ (২০১৬);
খ. সীমা রায়ের ‘গাছটা’ (২০১৬),
গ. তিলোত্তমা মজুমদারের ‘বিকেলের আলো’ (জন্ম ১৯৬৬),
ঘ. সমরেশ মজুমদারের ‘জলের প্রাণ’ (২০১৮) গল্পে।
- নিসর্গ-নারীবাদী ভাবনা প্রভাবিত গল্পগুলির মধ্যে
ক. রাধা ভটের ‘অন্নের ব্যবস্থা’,
খ. সরোজ দরবারের ‘কি ভুলেছি কেন ভুলেছি’,
গ. জয়া মিত্র’র ‘উন্নয়ন ও ঘরের লক্ষ্মী’,
ঘ. হর্ষ দত্ত’র ‘শিবানীতলার নদীজীবন’,
ঙ. ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের ‘তাতারসি’,
চ. সাধন চট্টোপাধ্যায় ‘ভাদ্রের গোধূলি-লগন’ গল্পগুলি।
এছাড়া গৌর বৈরাগীর ‘জবরদখল’, সুবীর মজুমদারের ‘স্বজনে’র মত গল্পে প্রাকৃতিক উপাদানের গুরুত্ব পুঁজির নিরিখে নয়, বরং বাস্তুতন্ত্রীয় ভারসাম্য সংরক্ষণের ভূমিকায় নির্ধারিত। প্রতিভাস ম্যাগাজিন
পর্ব – ২৩
পরিবেশবাদী বাংলা উপন্যাস
জিম ডোয়ার্যে’র বই ‘where the wild books are: A field quide to Eco-fiction’ (২০১০) বইতে বলেন যে ‘ইকোফিকশনে’ না-মানব পরিবেশ কেবল একটি ‘ফ্রেমিং ডিভাইস’ বা পটভূমি হিসেবে উপস্থিত না হয়ে বরং মানব ইতিহাসকে প্রাকৃতিক ইতিহাসের সাথে জড়িত করবে। শুধুমাত্র মানব ইতিহাসকে তথা মানবকেন্দ্রিকতাকে কোনো গুরুত্ব দেওয়ার বদলে ‘ইকো-টেক্সট’গুলির বরং একটি নৈতিক দিক থাকবে- পরিবেশের প্রতি মানুষের দায়বদ্ধতার অঙ্গীকার। আর পরিবেশগত বোধটি ক্রিয়াশীল থাকবে প্রক্রিয়া হিসেবে।
মাইক ভ্যাসি যে কোনো ধারায় (রোমান্স, অ্যাডভেঞ্চার, রহস্য বন ও বন্যদের জীবন্ত করে তোলার উপায় হিসেবে ‘ইকো-ফিকশন’কে ভাবেন। ডিমে ডোয়ার্যের মতে তিনি প্রথম ইকো-ফিকশন শব্দটি শুনেছিলেন ওয়াশিংটন স্কয়ার প্রেস প্রকাশিত ‘ইকো-ফিকশন অ্যানথোলজি’ থেকে (১৯৭১)। এখানে শুরুতেই বলা হয়েছে-
“পৃথিবী একটি ইকো-সিস্টেম। এটি সামূহিক স্মৃতিকে ধারণ করে। ফলে এর মধ্যে যেকোনো ঘটনাকেই যত অ-তাৎপর্যপূর্ণ মনে হোক না কেন, কোনো না কোনো ভাবে কোনো না কোনো সময়ে তা ওই বাস্তুতন্ত্রে অবস্থিত বাকি সবকিছুর অস্তিত্বকে প্রভাবিত করে।”
ইকো-টেক্সটগুলি ইকো-সিস্টেমে অবস্থানকারী মানুষের ভূমিকা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে যে সে পরিবেশের সতর্কতামূলক বার্তাকে ক্রমাগত গুরুত্ব না দিয়ে নিজের উৎস ধ্বংসের লীলায় নিজেই মেতে থাকবে কিনা, সভ্যতাকে কসাইখানার দিকে প্রসারিত করবে কিনা।
বাংলার বিজ্ঞানভাবুক মধুসূদন গুপ্ত (কলিকাতা ফিবার হাসপাতালের ডাক্তার), আচার্য জগদীশচন্দ্র বসুর পরিবেশ সচেতনতার নির্দেশও আমরা যখন গ্রহণ করিনি, তখন কলম ধরেছেন প্রোথিত যশা লেখক-লেখিকারা। আমাদের বেঁচেবর্তে থাকা চরাচরের প্রতি গভীর দায়িত্ববোধ সাহিত্যের একটি নতুন প্রকরণ হিসেবে ‘পরিবেশবাদী কথাসাহিত্য’কে প্রতিষ্ঠা করে ফেলে। প্রকৃতি-মানুষ বিরোধ পর্বে এসে পৌঁছতে বাঙালির পরিবেশচর্চাগত অভ্যাসের যে বিপুল বদল ঘটেছে, বাংলা কথাসাহিত্যে পরিবেশভাবনা বিবর্তনের রূপরেখায় তার প্রতিফলন স্পষ্ট। পরিবেশবাদী বাংলা উপন্যাসগুলি গত ত্রিশ বছরের কিছু বেশি সময় ধরে আলাদা জায়গা তৈরি করে নিয়েছে।
১৯৭২ সালে স্টকহোমে পরিবেশ সমস্যা নিয়ে প্রথম বিশ্ব সম্মেলন হয়। বিশ্ব পরিবেশ সম্মেলনের দু’বছরের মাথায় ১৯৭৪ সালে প্রকাশিত হয় বাঙালি লেখিকা লীলা মজুমদারের ‘বাতাসবাড়ি’ উপন্যাস। জনবিস্ফোরণপিষ্ট ভবিষ্যতের পৃথিবীতে থাকা-খাওয়ার অভাব, নিঃশেষ হয়ে আসা প্রাকৃতিক খনিজ সম্পদ, জলের অভাব ইত্যাদির অভাবপূরণে বাতাসবাড়ির নকশা তৈরি করেন লেখিকা লীলা মজুমদার। সেখানে সৌরশক্তির যন্ত্র তৈরির কারখানা বানিয়ে পরিবেশকে দূষণমুক্ত করার ব্যবস্থা যেমন আছে, তেমনি আছে পর্যাপ্ত সবজির চাষ। স্বভাবতই পরিবেশবান্ধব এমন বাতাসবাড়িতে বৃষ্টির অভাবও মিটে যায়। পরবর্তী ১৯৮৯ সালের পরিবেশ সম্মেলনটি হয় নেদারল্যান্ডস-এ। এই সম্মেলনে জলবায়ু পরিবর্তন এবং বায়ুমণ্ডলীয় দূষণ নিয়ে আলোচনা করা হয়েছিল। সেখানে পরিবেশ সমস্যার ঘোষণাপত্রে পেশ করা হয় ছাব্বিশটি নীতির কথা, যার মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষা করা এবং নবায়নযোগ্য উৎস উৎপাদন করার নীতি। লীলা মজুমদারের ‘হাওয়ার দাঁড়ি’ উপন্যাসে (১৯৮৯) বিজ্ঞানসম্মত এই নীতির প্রতিফলন পাই। শীত-বৃষ্টি-গরমহীন এলাকার গাছ মরে যাওয়া, পাহাড় ধসে যাওয়া, ঝরণা লুকোনোর মত সমস্যা সমাধানে পন্ডিত অঙ্ক কষে জানায়- দিনরাত কয়লা তোলা, নলে করে গ্যাস চালান দেওয়া, সব খেয়ে শেষ করে ফেলার কারণে প্রকৃতি আর মানুষের স্বাভাবিক সহাবস্থানের মূলে উপস্থিত নিয়মনিষ্ঠা ফুরিয়ে গেছে। মানুষের অত্যাচার যখন পৃথিবীর অক্ষদন্ডের কৌণিক অবস্থান পাল্টে দিয়েছে তখন উল্টোদিকে বর্জ্যটুকুও নষ্ট না করে তা পুঁতে রেখে জৈব সার তৈরির মাধ্যমে পরিবেশের স্বাস্থ্যবিধান করা ও শস্য ফলানোর শিক্ষাদান আছে। প্রাকৃতিকভাবে দূষণ অপসারিত করতে পরিবেশের সক্ষমতা বাড়ানোর শিক্ষা দেন তিনি।
আবার হুগলী নদী সন্নিহিত কাঁঠালবেড়ে গ্রামের আটশো বিঘে জমি অধিগ্রহণ করে তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রের পত্তনকে ঘিরে সৃষ্ট দূষণের কথা আছে অমর মিত্রের ‘কৃষ্ণগহ্বর’ উপন্যাসে (১৯৯৮)। লরি লরি ছাই ফেলে জমি উঁচু করে ‘ডেভলপ’ করা হয়, চিমনিতে কাজ করতে থাকা শ্রমিকদের বেওয়ারিশ মৃত্যু হয়, নাম ছড়িয়ে পড়ে- মানুষখেকো চিমনি। ডেভলপমেন্টের কুফল সম্পর্কে সচেতন যারা, তারা দেখেছিল মাটি কেটে নেওয়ার ফলে তৈরি বড় গর্ত, গাড়ি আসার সঙ্গে সঙ্গে সাপ ব্যাঙ ইঁদুর এমনকি বাস্তুসাপের পলায়ন, ছাই হয়ে যাওয়া নদীর জল, ইলিশের না আসা তথা গোটা গ্রামেরই ধসে যাওয়া বাস্তুতন্ত্র। অমর মিত্র দেখান, বিদ্যুৎ আর ‘ডেভলপমেন্ট’-এর জোয়ারে গ্রামের কেবল অর্থনেতিক কাঠামোই পাল্টে যাচ্ছেনা, তার চেনা জীবনপ্রবাহও বদলে যায়। শিল্পায়ন ও নগরায়ণে গ্রাম আক্রান্ত হচ্ছে। সুকান্তি দত্তের ‘যুধানকথা’য় (২০০১) ইটভাটার দূষণ ও পুকুর বুজিয়ে গুদামঘর বানানোর বিরুদ্ধে লড়াই করে আহত পরিবেশ সচেতন নাগরিক যুধান বারবার পৌঁছে যায় দূষিত কালো জলের বিলে, যেখানে বাদামি ডানা শুকপাখির বলা পুরাণকথায় ফুটে ওঠে লোভ, ক্ষমতা, রাজনীতির আগ্রাসনে পরিবেশ বিপন্নতার আখ্যান। যুধান দেখে তার শৈশবের শুঁটি নদী শুকিয়ে নালার মত হয়েছে, কমলাদিঘির পাড় ও মাঠ বিক্রি হয়ে প্লটে প্লটে ভাগ হয়ে গেছে, ঐতিহ্যবাহী সিংহীবাগান আর নেই, নদী পুড়ে গিয়ে জলপিপি-শালিকের ঝাঁক আর গাছের পাতায়ও আগুন ধরে গেছে। তবু এই ধ্বংসলীলার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ শেষপর্যন্ত চালিয়ে যায় যুধান, সোনালি শস্যভরা ক্ষেতের ভেতর শরীর ডুবিয়ে হাঁটতে হাঁটতে এক মহাবৃক্ষের সামনে পৌঁছে সে সমগ্র আধুনিক মানব প্রজাতির প্রতিনিধি হিসেবে ক্ষমা চাইতে চায়।
‘মধুবনের বন্ধু’তে (২০০২) চোরাকাঠ পাচারকারীদের হাত থেকে জঙ্গল রক্ষার কাহিনি শুনিয়েছেন লেখক ভগীরথ মিশ্র, বলেছেন পবন কাঠুরিয়ার কাঠ কাটার ফলে পাতলা হয়ে যাওয়া জঙ্গল ঘনত্ব আর পরিবেশে তার প্রভাব সম্পর্কে। স্বকৃত জলবায়ু পরিবর্তনের দৃষ্টান্তে পবন নিজের সংশোধন ঘটায় এবং জঙ্গলের বাস্তুতন্ত্র সংরক্ষণে ব্রতী হয়৷ আকর খনন ও ফসিল জাতীয় জ্বালানির কারণে পাইরাইটের মধ্যে থাকা আর্সেনিক রূপের সঙ্গে অক্সিজেনের ক্রিয়া-বিক্রিয়ায় তৈরি হয় মারণ বিষ। সাধন চট্টোপাধ্যায় রচিত ‘জলতিমির’ পানীয় জলে সেই আর্সেনিক দূষণের আখ্যান। রবিদাসপাড়ার বাসিন্দা অন্নপূর্ণার মৃত্যুর উৎস খুঁজতে খুঁজতে আমরা জানতে পারি পাড়ার কলের জলে বহুদিন ধরে হাল্কা ফ্যান মত মিশে থাকার সূত্রে গ্রামের মধ্যে পরিছন্নতা ও স্বাস্থ্য বিষয়ে কিছুটা সচেতন অন্নপূর্ণাই কেবল বুঝতে পেরেছিল পেট ছাড়া, শিলঠোকা কালচে দাগের তাৎপর্য। বিজ্ঞানমঞ্চের প্রতিনিধিত্বে জলদূষণের সচেতনতামূলক কর্মসূচি ও কালিয়দমনের মিথের আশ্রয়ে আর্সেনিক দমনের প্রসঙ্গ এসেছে। কার্যত সাধন চট্টোপাধ্যায় জনস্বাস্থ্যসচেতনতার প্রথম বাংলা উপন্যাসটি লিখলেন। তাঁর আরেকটি উপন্যাস ‘শেষ রাতের শেয়ালে’ হারিয়ে যাওয়া সোনাই নদী পুনরুদ্ধারকল্পে গঠিত সোনাই রক্ষা কমিটি বুঝতে পারে নদীটাকে সংঘবদ্ধ ভাবে চুরি করা হয়েছে, তার বুক থেকে মাটি তুলে রাস্তাঘাট বানিয়ে ঘিঞ্জি জনবসতির তলায় চাপা দেওয়া হয়েছে। গ্রিনবেঞ্চে সোনাইকে খোঁজার অধিকার জারি রাখার আবেদনে তারা পরিবেশ সংরক্ষণে সচেতনতা গড়ে তুলতে চায়, সোনাইয়ের সন্তান পুকুরগুলোকে বাঁচানোর দাবি তোলে।
‘সবুজ রঙের শহর’ উপন্যাসে (২০০৯) সিন্থেটিক সবুজের মাঝে নগরায়ণ প্রকল্প স্থান পেয়েছে। কৃত্রিম গাছ, ফুল, জোনাকি, নীলজল ও সমুদ্র গর্জনের ব্যবস্থাপনায় পূর্বে এবং ভবিষ্যতে বহু গ্রাম, চাষের জমি, আমকাঁঠালের বাগান অধিগ্রহণ করে বেড়ে যাওয়ার পরিকল্পনায় সবুজ শহর অথরিটি প্রকৃতিলগ্নতায় যাপিত জীবনের সমস্ত স্মৃতি মুছে ফেলতে বদ্ধপরিকর। পরিবর্তে সবুজ শহর দিতে চায় প্রযুক্তির কল্যাণে যা খুশি যখন খুশি পাওয়ার গ্যারান্টি। কিন্নর রায়ের ‘প্রকৃতিপাঠ’ উপন্যাস শূন্য দশক থেকে সরাসরি পরিবেশবাদী কথাসাহিত্যের চর্চার পরিসর বিস্তৃত করে দেয়। পরিবেশবাদী পত্রিকা, পরিবেশবাদী লেখকগোষ্ঠী ও আন্দোলনের কথা এসেছে। প্রধান চরিত্র সতীপ্রসন্ন মানুষ আর পরিবেশকে অনেকখানি সংস্কারমুক্ত করার ভূমিকায় পরিবেশদূষণ মূলক কার্যকলাপ, পুকুর বোজানো, বহুতলের প্রাচুর্যে নেমে যাওয়া জলের স্তর, পরিযায়ী পাখিদের কমতি, ধোঁয়াশার আকাশ, ঐতিহাসিক বাড়ি ভেঙে মাল্টি স্টোরড বিল্ডিং ওঠা ইত্যাদিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে সুস্থ পরিবেশ-বোধ গড়তে চান। সমীরের মত কেউ কেউ যারা যতদিন সম্ভব ‘ইকোলজিক্যাল ব্যালান্স’ রক্ষার কথা ভাবছিল, সতীপ্রসন্ন তাদের সঙ্গে মিলিতভাবে এলাকার গরীব গৃহস্থদের একমাত্র অবলম্বন পুকুর বুজিয়ে বাড়ি তৈরির বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলেন; তিনি বুঝতে পারেন যে ‘পরিবেশ’ (পত্রিকা) করা তাঁর বৃথা যায়নি। ‘মেঘপাতাল’ উপন্যাসে বিহারের দলমা থেকে খাদ্যের অভাবে নেমে আসা হাতির দল খেদানোকে কেন্দ্র করে প্রজাতিটির সংখ্যা হ্রাস, হাতির সঙ্গে জড়িত উপযোগবাদ, পশ্চিমবঙ্গে কেবল উত্তরবঙ্গ ও মেদিনীপুরে কোনোক্রমে টিকে থাকা জঙ্গল, শৌখিন বনসৃজন, আত্মরক্ষার্থে বিপন্ন হাতিদের গৃহীত পন্থার কথা আছো তথাকথিত হস্তিবিশারদও যখন হাতি শিকারের দলে থাকে তখন সাবুর মত এক-দু’জন কোনো এক অদৃশ্য যোগাযোগে বুঝতে পারে অবলা পশুদের স্বার্থের কথা। লেখক দেখান যে আধুনিক প্রযুক্তিধন্য সভ্যতা অরণ্য নির্বিচারে ধ্বংস করতে পারলেও হাতিদের অস্তিত্ব নিশেষ করতে পারেনি, তবু অস্তিত্বের বিপদ সংকেত ঝুলতে থাকে হাতিসহ পাইথন, লেপার্ড, পাখি, প্রজাপতিদের সামনে।
আবুল বাশারের ‘শেষ রূপকথা’ উপন্যাসে লাইসেন্সহীন কেমিক্যাল কারখানা আর তা থেকে ছড়ানো ভয়ানক রাসায়নিক দূষণের কথা আছে। কোনোরকম সেফটি ভালভ, উপযুক্ত ড্রেনেজ সিস্টেমহীন ‘দি মেডিলিঙ্ক ইন্ডিয়া ইন্টারন্যাশনাল’ কারখানা হেভি ওয়েট কেমিক্যালের বর্জ্যে পুকুরের জলে টক্সিক লেভেল ছাড়িয়ে যায়, বিষাক্ত পুকুরের জল আর ঘাস খেয়ে পার্শ্ববর্তী খাটালের গাইগুলোর বাঁট ফেটে রক্তদুধের আমদানি হতে থাকে, শুভেন্দুর চুল অকালে পাকে, মূত্রদ্বারে ঘা হয়, বাড়ির আমগাছটা পর্যন্ত মরে যায়, প্রতিবেশী বাড়ির ছোট মেয়েটি অন্ধ হয়ে যায় (মাইওপিয়াতে), এবং কারখানার দারোয়ানের বুকে যক্ষ্মা বাসা বাঁধে। ক্রমে এলাকার সমস্ত জল আর বায়ু সন্দেহজনক হয়ে ওঠে। ডাক্তার সীতানাথ দূষণ প্রতিরোধে প্রগতি মঞ্চের ভূমিকা প্রচার করেন, আবার ‘স্কুল অফ এনভায়রনমেণ্টাল স্টাডিজ’-এর সদস্য অমরেন্দ্র বসু পরিবেশ দূষণে দায়ী যে কোনো শিল্প সংগঠন বন্ধ করে দিতে উদ্যত। লেখক ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের অজস্র লাইসেন্সহীন কেমিক্যাল কারখানা থেকে ছড়িয়ে পড়া দূষণের কথা আর সেই দূষণ রোধ করতে গেলে বহু মানুষের বেকারত্বের কাহিনি জ্ঞাপন করেছেন।
মণীন্দ্র গুপ্তর ‘নুড়ি বাঁদর’ (২০১৬)-এর গল্প স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের গল্প, এতে প্রাণীদের নিগূঢ় জটিল অন্তরঙ্গতা খুঁজে দেখা আছে। বরফ, মাটি, পাথরের চাঁই গুমগুম শব্দে বলে ওঠে- “আমাদের প্রাণ নেই, ইন্দ্রিয় নেই, তবু আমরাও কিছু কিছু বুঝি।” তাদের শান্তিতে থাকতে না দিলে তারাও শান্তিতে থাকতে দেবে না মানুষকে। অরণ্যের নুড়িকে লেখক প্রাচীন সঞ্জীবনী জলধারায় বাঁদরে পরিণত করান, যে মানুষের সঙ্গে পারস্পরিকতায় সভ্যতার বাহক হতে চেয়েছিল, কিন্তু অবিলম্বে সে বোঝে মানুষের সঙ্গে অংশীদারী কারবার তাদের মত পশু-পাখিদের চলবেনা। প্রকৃতির সঙ্গে নিয়মানুবর্তিতায় থাকার পরম্পরাবাহিত অভিজ্ঞতা, জ্ঞান আমরা হারিয়েছি কিন্তু তবু আধশুকনো পুকুর, ক্ষেত, কাদরের ঐতিহ্য হারিয়ে ফেলতে যে নেই, তেমন সুরই শোনায় জয়া মিত্রর ‘সূর্যের নিজের গ্রাম’ (২০২১) উপন্যাস। পরিশেষে নাম করা যায় শেখর মুখোপাধ্যায়ের ‘অঝোর মৌসুমি’র (২০২১)। জাতীয় উন্নয়নের মাপকাঠি হিসেবে সীমাহীন তাপবিদ্যুৎ উৎপাদনে সংশ্লিষ্ট এলাকার বাস্তুতন্ত্রীয় সাম্যাবস্থাই কেবল বিঘ্নিত হয়না, এমনকি উন্নয়ন এবং পরিবেশের আন্তসম্পর্ক বিষয়ক জিজ্ঞাসাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। পর্যালোচিত হয় পরিবেশ ও অর্থব্যবস্থার আর্থ-সামাজিক ইতিহাস। পুঁজিবাদী পিতৃতান্ত্রিক সমাজ আর তার নির্দেশিত উন্নয়ন ভাবনার একটি বিকল্প হিসেবে ‘Subsistence perspective’ অর্থাৎ বেঁচে থাকতে যতটুকু দরকার, ততটুকুই আয় বা উৎপাদন করার প্রয়োজনীয়তার দিকে লেখক আমাদের নজর টানেন।
তথাকথিত উন্নয়ন ও ক্রমাগত নগরায়ণ যখন ‘বিশ্ব উষ্ণায়ন’ শব্দটিকে অভিধানের পৃষ্ঠা থেকে দৈনন্দিন জীবনে নিয়ে এল, তখনও মানুষ সচেতনতামূলক কোনো নীতি তেমনভাবে গ্রহণ করেনি। পরিবেশের হঠাৎ বা দীর্ঘস্থায়ী বিপর্যয়ের কারণে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিসমষ্টির স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ব্যাহত হলে, ঘরবাড়ি হারাতে বাধ্য হলে তাদের বলা হয় পরিবেশ জনিত উদ্বাস্তু বা ‘প্রব্রজণকারী’। ‘এনভায়রনমেন্টাল এমার্জেন্সি মাইগ্রেণ্টস’, ‘এনভায়রনমেন্টাল ফোর্সড মাইগ্রেণ্টস’, ‘এনভায়রনমেন্টাল ইনডিউসড মাইগ্রেণ্টস’ (Environmental emergency migrants, Environmental forced migrants, Environmental induced economic migrants) ভেদে এরা সাময়িক বা চিরস্থায়ী ভাবে নিজ ভূমি থেকে উৎখাত হয়। কারণ- দীর্ঘস্থায়ী খরা, জলসংকট, অতিবৃষ্টি, জমির উর্বরা শক্তি হ্রাসে খাদ্য সংকট বা তীব্র তাপ প্রবাহ। অমিতাভ ঘোষের ‘বন্দুক দ্বীপে’র বিষয়বস্তু বর্তমান সময়ের দুটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা- জলবায়ু পরিবর্তন ও পরিযায়ী মানুষ। জানব এদের কথাও। প্রতিভাস ম্যাগাজিন
